আমার এই লেখার বিষয় কেবল কবি জীবনানন্দ দাশ নন। কবিজাযা লাবণ্য দাশের ভূমিকাও এ লেখায় প্রধান। কবির দাম্পত্যজীবনের কয়েকটি অন্তরঙ্গ চিত্রে যেমন স্বামী ও পিতা জীবনানন্দ দাশের ব্যক্তিজীবনটি উদ্ভাসিত হয়ে উঠতে দেখি, তেমনি সমুজ্জ্বল হয়ে থাকে কবির এক পরম আপনজনের চিত্র।
লম্বা ছিপছিপে উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ একটি মেয়ে। মুখের গড়ন লম্বা ধাচের। উজ্জ্বল চোখ, তীক্ষু নাক, পাতলা ঠোট। বয়স সতের-আঠার। ঢাকায় হষ্টেলে থেকে পড়ত। নাম লাবণ্য। ছোটবেলাতেই বাবা-মাকে হারিয়েছে। মানুষ হয়েছে জ্যাঠামশাই-এর কাছে।
তখনকার কালের ঢাকার কলেজের মেয়ে যেমন হত, ঠিক তেমন। বিপ্লবী দলের সঙ্গে গোপন সংযোগ, শরীরচর্চা, আবার নাচ গান অভিনয়ে ঝোক । মা-বাপ নেই বলে খুব স্পর্শকাতর। সেই লাবণ্যকে হঠাৎ একদিন জ্যাঠামশাই বাড়িতে ডেকে নিয়ে এলেন। হস্টেল থেকে বাড়িতে আসতে এক মাঠ কাদা ভাঙতে হয়। পরনে নকশাপাড় তাতের সাধারণ শাড়ি। আসতেই জ্যাঠামশাই বললেন, বাড়িতে অতিথি এসেছেন চা জলখাবার এনে দাও। সেই কাদামাখানো শাড়ি পরেই লাবণ্য লুচি মিষ্টি চা নিয়ে এলেন বাইরের ঘরে। অতিথির সংখ্যা মাত্র একজন। শ্যামবর্ণ, অতিসাধারণ ধুতিপাঞ্জাবি পরা নতমুখী একটি আটাশ-উনত্রিশ বছরের যুবক।
জ্যাঠামশাই পরিচয় করিয়ে দিলেন। ইনি দিল্লী থেকে এসেছেন। ওখানকার রামযশ কলেজে পড়ান। ইংরেজির অধ্যাপক। আর এ আমার ভাইঝি লাবণ্য। অধ্যাপক জীবনানন্দ দাশ চোখ তুলে নমস্কার করলেন।
জীবনানন্দ দাশ চোখ তুলে নমস্কার করলেন। সেদিন দুপুরে জ্যাঠামশাই লাবণ্যকে বললেন দিল্লী থেকে যে ছেলেটি এসেছিলেন, তিনি তাকে দেখতেই এসেছিলেন। এবং যাবার সময় মনোনীত করে গেছেন। লাবণ্যের কিন্তু তখন বিয়ে করতে একটুও ইচ্ছে নেই। সে সময়ে কারই বা থাকে। বিশেষ করে সবে তখন কলেজে ঢুকেছে, সবে মুক্তির স্বাদ, সবে রাজনীতির রহস্যময় আস্বাদ–তখন সব এত নতুন এত বৈচিত্র্যময.... জ্যাঠামশাই লাবণ্যকে জীবনের বাস্তব দিকগুলির কথাও ভাবতে বললেন সেদিন। বাবা নেই, মা নেই। কেবল তিনিই সম্বল। আর জীবনানন্দ কথা দিয়েছিলেন বিয়ের পরও লাবণ্য পড়বেন। তাছাড়া যখন জ্যাঠামশাই বলছিলেন–‘মেয়েটা মা-বাপ মরা একটু জেদি একটু আদুরে, ওকে তুমি ভালো করে দেখো”—তখন ছেলেটির শান্তচোখে একটা আশ্বাসের ছায়া তিনি স্পষ্ট দেখেছেন । বিশেষ করে ছেলেটির শান্ত প্রকৃতিটা তাকে সবচেয়ে বেশি আকৃষ্ট করেছিল।
লাবণ্য মত দিলেন। সে বছরটা ১৯৩০ সাল। সে সময়টা বৈশাখ ।
ঢুকে জীবনে প্রথম একটি শাড়ি কিনল। আশীর্বাদের শাড়ি। সন্ধ্যায় আশীৰ্বাদ হল। লাবণ্য হিন্দু কুলীন বাড়ির মেয়ে। মানুষ গিরিডিতে। তার বিশেষ হিদুয়ানির সংস্কার ছিল না। জ্যাঠামশাই ব্রাহ্ম ছিলেন। কিন্তু ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের মর্যাদা দিতেন বলেই তিনি লাবণ্যকে জিজ্ঞেস করে নিলেন, বিয়ে কোন মতে হবে। ব্রাহ্ম বিবাহে লাবণ্যের আপত্তি হয় নি।
বিয়ের সময়ে জীবনানন্দর সঙ্গে এসেছিলেন বুদ্ধদেব বসু আর অজিত দত্ত। বিয়ের অনেক করণীয় স্মৃতির সঙ্গে স্বামীর একটি বন্ধুর স্মৃতিও কেন যেন গেঁথে গিযেছিল তার মনে বুদ্ধদেব ছোটখাটো বুদ্ধিদীপ্ত উজ্জ্বল একটি যুবক তখন। স্বামী পরিচয় করিয়ে দিয়ে বলেছিলেন : বিশ্ববিদ্যালয়ের রত্ন, পণ্ডিত ব্যক্তি। কিন্তু লাবণ্যর চোখে সুন্দর লেগেছিল তার প্রাণচাঞ্চল্য, আকর্ষণীয় কথা বলার ভঙ্গি, সহজ সাবলীল আচরণ। লাবণ্য দাশ বললেন;– সাধারণত ওঁর বন্ধুদের সামনে খুব একটা বেরোতাম না। কিন্তু বিয়ের দিনটি থেকেই বুদ্ধদেববাবুকে আমি আমার স্বামীর বন্ধু, আমাদের বড় সুহৃদ বলে জেনেছি। তিনি এলেই তার কাছে এসে বসেছি। তার পাণ্ডিত্য, কবিপ্রতিভা নামযশ কিছুই আমাদের আর তার মধ্যে কোনো আড়াল সৃষ্টি করে নি। বিয়ের দিনে দেখা সেই বৃদ্ধিদীপ্ত মানুষটি—আমার তরুণ স্বামীর তরুণ সঙ্গীটি আমার কাছে ঐভাবেই মুদ্রিত হয়ে গেছেন। বিয়ের পর বরিশালে গেলেন বর-বধূ। মস্ত সংসার। অনেকখানি ছড়ানো, মেলা জায়গা নিয়ে বড় বড় ঘর। কিন্তু মাটির ভিত। খড়ের আস্তর। শহর থেকে গিয়ে লাবণ্যর খানিকটা অবাক লেগেছিল। ঢুকতেই ইতস্তত করছিলেন ঘরে। পরে সেই বড় বড় ঠাণ্ড ঘর, আম, জাম, বট, অশথের, হিজলের ছড়ানো বড় বড় বাগান পুকুরের স্নিগ্ধতা লাবণ্য অনুভব করেছিলেন।
তরুণ স্বামী কিন্তু কোনোদিন গৌরব করেও বলেন নি তিনি কবিতা-টবিতা লেখেন। তার করা পালক বলে একটি কাব্যগ্রন্থও আছে। কিন্তু সবসময়ে তিনি বই পড়তেন। বই-ই ছিল তার আশ্রয়। ছোট ছোট অক্ষরে কী যেন লিখতেন মাঝে মাঝে। বাংলায়। লাবণ্য এলে লুকোতেন। আর স্বামী যা লুকোবেন তাই-ই যদি কেড়ে নিয়ে না দেখবেন তাহলে আঠার বছরের মেযেটির আর জেদ কোথায় রইল ? লাবণ্য দাশ বলছিলেন,—‘অনেকে বলেন, তিনি নিপাট ভালোমানুষ, আত্মভোলা, কোনোদিকে তার দৃষ্টি ছিল না ইত্যাদি। এসব যখন শুনি, বা পড়ি, তখন আমার খানিকটা অদ্ভুত লাগে। কারণ ঐ ছবিতে আমি যেন আমার অচেনা ব্যক্তিত্বহীন একজন সাজানো শৌখিন কবির তৈরি-করা ছবি দেখতে পাই। আমি ঐ ব্যক্তিত্বহীন জীবনানন্দকে সত্যিই চিনি না। আমার স্বামীর ছবি, আমার কাছে সম্পূর্ণ অন্য। তার উদার মন, আর ব্যক্তিত্বের জন্য জীবনে অনেকবার আমি অনেক সমস্যা থেকে উদ্ধার পেয়েছি মনে পড়ে। দু-একটা চিত্র আমি দিই।
‘মনে আছে, একবার বিয়ের ঠিক পরেই বরিশালের গ্রামের প্রতিবেশীদের মধ্যে কেউ কেউ বলেছিলেন, ‘আহা আমন এম. এ. পাস প্রফেসর ছেলে, অথচ বিয়েতে বিশেষ কিছুই পেল না। আমি এসব কথা শুনে খুব কষ্ট পেলাম। আমার স্বভাবই ছিল জেদি। আর সবরকম প্রশ্ৰয়ও পেতাম ওঁর কাছে। একদিন চাপা গলায় বললাম ওঁকে, “বাহ রে আমি কি তোমায সেধে সেধে বিয়ে করেছি। তোমরা যে এত সব কথা শোনাও। তুমিই তো আমায় নিজে দেখেশুনে নিয়ে এসেছ।” কথাটা উনি শুনলেন। তারপর আমার শাশুড়ির কাছে গিয়ে বললেন,—“যারা এসব কথা বলছেন, আমি লাখ টাকা পেলেও তাদের বাড়ির মেয়ে বিয়ে করতাম না। সুতরাং এ নিয়ে চর্চা না হওয়াই ভালো। সুতরাং তার ব্যক্তিত্ব ছিলই এবং কথার উচিত জবাব তিনি চিরকালই দিতে পেরেছেন।
আর একটি ঘটনা মনে পড়ে, তার জীবনের কোথাও দেওয়া-নেওয়া, দেনা-পাওনার কোনো স্বাভাবিক সংস্কারই ছিল না বলে বিয়ের সময় আংটি-বদলে-পাওয়া আমাদের বাড়ির আংটিটি নিয়ে তাকে খুব লজ্জা পেতে দেখেছি। কেবল বলতেন, আচ্ছা, কেন যে ওঁর এত টাকা খরচ করে এই
আংটি করিয়ে দিলেন। শুধু শুধু ভদ্রলোকদের খানিকটা অর্থব্যয়। আমার শাশুড়ি বললেন, ‘বাহ আংটি বদলের সময় লাগবেনা বুঝি। উনি বিব্রত হয়ে বলতেন, ‘তা একটা পেতলের আংটি-টাংটি দিলেই তো হত!’
বিয়ের পর বরিশালে এসে লাবণ্যর পড়া স্থগিত রইল। জীবনানন্দও একটু ইতস্তত করছিলেন কিভাবে স্ত্রীর কলেজে পড়ার কথাটা পড়বেন এই ভেবে। তখন লাবণ্যর এক শ্বশুরমশাই বললেন ঠিক আছে তোমার পরীক্ষা নেব। যদি পাস হও তাহলে পড়ার অনুমতি পাবে।
লাবণ্য দাশ জানান, — ‘একটি খালি ঘরে বাইরে থেকে শিকল তুলে দিয়ে তিনি আমায় কাগজ কলম দিয়ে বললেন, এক ঘণ্টার মধ্যে ইংরেজিতে একটা রচনা লেখো! অন্য মেয়ে হলে হয়তো অভিমান করে লিখতই না। আমি কিন্তু লিখলাম। রচনাটা পড়ে তিনি আমাকে পড়বার অনুমতি দিলেন। আগষ্ট মাসে ভর্তি হলাম। ডিসেম্বরে টেস্ট-এ বসলাম। আই. এ. পরীক্ষার সময় থেকেই ওঁর সহায়তা পেয়েছি। পূর্ণ সহযোগিতা পেলাম বি.এ. পরীক্ষা দেবার সময়। তখন উনি আর কারে কথা শুনলেন না। আমাকে পড়াতে লাগলেন। তখন মঞ্জ হয়েছে। মঞ্জকে ঘুম পাড়িয়ে রাত্রে পড়তাম। বিশেষ করে উনি আমাকে সংস্কৃতটা খুব যত্ন করে পড়িয়েছিলেন। পড়ার সুবিধার জন্য ঘর আমাকে ছেড়ে দিয়েছিলেন। আবার পাছে রাত্রে পড়ায় ফাকি দিয়ে ওঁর কাছে গিয়ে গল্প করি, তাই শিকল তুলে শাসন করে দিয়ে যেতেন। নিজেও সব সময় পড়তেন। বিশেষ করে ইংরেজি বই। অঙ্কেও খুব ভালো ছিলেন। কেবল হাতে ফিগার এঁকেছিলেন বলে পাচ নম্বর কেটেছিল। পচানব্বই পেয়েছিলেন অঙ্কে |
‘যখন আই. এ. পড়ছি তখন বিনয়-বাদল-দীনেশের সময়, তখন হঠাৎ একদিন কলেজ থেকে ফিরে দেখি, বাড়ির সামনে কুড়ি-পঁচিশখানা সাইকেল। পুলিশ এসেছে। একজন আমার পড়ার টেবিলের ওপর চেপে বসে আছে, আর একজন আমার বিছানার ওপর। উনি খুব বিব্রত মুখে দাড়িয়ে আছেন। ওঁর মুখ একেবারে ফ্যাকাশে। আমি স্পষ্ট বুঝলাম ভয়টা নিজের জন্য যত না তত নববধূর জন্য। পুলিশকে বলছেন, – না, না, ওর তো কোনোরকম সন্ত্রাসবাদীদের সঙ্গে যোগাযোগ আছে বলে জানি না!
—আপনি কী জানবেন মশাই! ওরা সব ঢাকার মেয়ে। ওরা এসব কথা মরে গেলেও কাউকে বলবে নাকি ?
—বেশ তো, আপনারা সব সার্চ করে দেখুন! লাবণ্য দাশ বললেন, – “পুলিশ কীভাবে যে ওঁর যত্ন করে গুছিয়ে রাখা পাণ্ডুলিপি ছিড়ে ছড়িয়ে নষ্ট করতে লাগল! বাড়ির সবাই কত বিরক্ত হলেন। নতুন বউএর জন্য এই পুলিশের হাঙ্গামা। কিন্তু উনি স্থির হয়ে দাড়িয়ে সব দেখলেন। একটি কথাও বললেন না।
পুলিশ অনেকক্ষণ ধরে দলের একটি ছেলের নাম বের করবার জন্য আমাকে নানারকম জেরা করতে লাগল। আমি খবর পেয়েছিলাম এসব হবে। তাই সাবধান ছিলাম। তবু অসাবধানবশত কীভাবে জানিনা একটি বই হঠাৎ পুলিশরা বের করে ফেললে। আয়ার্ল্যান্ডের বিপ্লবের ইতিহাস বোধহয় বইখানা। তখন ওঁর মুখের সব রক্ত সরে গেছে। পুলিশ খাতাপত্র খুলে বসেছে একেবারে। তখন পুলিশ এইভাবেই এলোপাতাড়ি অ্যারেস্ট করছিল। হাজার হাজার অ্যারেষ্ট। আমি হঠাৎ বললাম—আচ্ছা, বইটার জন্য আপনারা এত আশ্চর্য হচ্ছেন কেন ?
—কেন হবো না ? —আমার ইন্টারমিডিয়েট হিস্ট্রি আছে তা জানেন ? —হ্যা, কিন্তু তাতে কী হয়েছে ? —বাহ, ওটা তো আমার পাঠ্য! সৌভাগ্যবশত পুলিশ অফিসাররা ছিলেন ম্যাট্রিক-পাস মাত্র। তারা একটু চোখ চাওয়াচাওয়ি করলেন। তাদের মধ্যে যিনি একটু বয়স্ক তিনি বললেন, নাও হে নাও, অনেক তো হয়েছে, এবার নিল লিখে চলে পুলিশ চলে যাবার পর আমার খুড়শ্বশুর রাগের চােটে বইখানা টুকরো করে ছিড়লেন। আর তিনি বিপর্যস্ত পাণ্ডুলিপিগুলোর দিকে তাকিয়ে শুধু বললেন, আচ্ছা, কী হত বলো তো যদি ওরা সত্যিই খোজ নিত বইটা পাঠ্য কিনা!
উনি ছোটবেলা খুব ভালো ফুটবল খেলতেন। ফুল ভালোবাসতেন। গুছানো ঘরদোর ভালোবাসতেন। বেঁচে থাকাটাকে শিল্পের মতো দেখতে চাইতেন। আমি একটু বিলাসী ছিলাম। উনি বলতেন জানো মেযের খুব সুন্দর করে সিদুরটি না পরলে, এবতাটি না দিলে আমার বাপু, ভালো লাগে না। আমি অমনি চট করে দেখে নিতাম আমার সিথিতে দেবের রেখাটি উজ্জ্বল আছে কিনা। আর ভালোবাসতেন রবীন্দ্রনাথের গান। জীবন মরণের সীমানা ছাড়ায়ে গানটি ওঁর প্রিয় ছিল। ওঁর মৃত্যুর পরপর সম্বন্ধে একটা অদ্ভুত আকর্ষণ ছিল। মাঝে মাঝেই ওই কথা বলতেন। বলতেন মৃত্যুর পরে অনেক প্রিয়জনের সঙ্গে দেখা হয়। আর খালি বলতেন, আচ্ছ বলো তো, আমি মারা গেলে তুমি কী করবে ? ওঁর বড় দুঃখ ছিল, ওঁর জেঠিমার নিষ্করুণ বৈধব্য পালন ওঁকে পীড়া দিত। উনি আমাকে বলতেন, তুমি কিন্তু ওসব কিছু করতে পারবে না। ঠিক এইরকমটিই থাকবে। সব সময় শুনতে শুনতে যখন ধৈর্যচ্যুতি ঘটত তখন রেগে-টেগে গিযে ভাবতে হবে না একেবারে!' তখন উনি হেসে চুপ করে যেতেন।
ছেলেমেয়েরা ছিল ওঁর বন্ধু। আর কবিতা শোনার গোপন সঙ্গী। মঞ্জুর কবিতা লেখা ওই ওঁর থেকেই পাওয়া। আর সুচরিতা, আমার ননদ, ওর কাছেও মাঝে মাঝে লেখা পড়তেন। রসগোল্লা খেতে খুব ভালবাসতেন। ছেলে হয়তো রসগোল্লা খাচ্ছে। হঠাৎ সমবয়সীর মতো এসে বলতেন— আধখানা দে না রে! কলকাতায় আসবার পর সুবোধ রায় ছিলেন ওঁর খুব বন্ধু, তার সঙ্গে রাত একটা দেড়টা পর্যন্ত গল্প করতেন। ছোট ছেলে সমরও থাকত সেই নিশীথ আড্ডায় ।
‘এবার বলি সম্পূর্ণ আমাদের দুজনের মধ্যেকার কথা। হয়তো এ কথায় একজন সংবেদনশীল কবিজায়ার ছবি ফুটবে না। নাইবা ফুটল। আমি তো তার বা আমার কারো কোনো মিথ্যা এক ‘Halo' তৈরি করতে পারব না। ওঁর কবিতা ক্রমশ ক্রমশ ধরছি। এখনও অনেকবার অনেকবার পড়তে হবে। আমিও ওঁর একজন পাঠিকা। বিয়ের পর থেকে অনেকদিন আমার কাছে রবীন্দ্রনাথই ছিলেন কবি। আমার কবি। যখনই কোনো বাংলা লেখা নিয়ে গেছি দেখাতে, উনি বলেছেন, correct করবার কিছু নেই। লিখতে তুমি জানো। ধাচ আছে নিজস্ব। রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে কোথায় কী বলেছেন আমি জানি না। তবে আমায় বলেছেন, চাদ বা সূর্যকে রাহু গ্রাস করে একটু একটু করে। একবারে মারে না। আর সেই তখনও মাঝখানে কালো কাচ ফেলে তবেই চাওয়া যায তার দিকে। রবীন্দ্রনাথকে যে আমরা দেখি সেও আমাদের সেইভাবে দেখা ।
‘তার সংসারে তিনি আমাকে অধীন করেছিলেন অবাধ স্বাধীনতা দিযে। বরিশালেই বলতেন যখন নিজের সংসার হবে তোমাকে আমি স্বাধীনতা দেব সম্পূর্ণ অবাধে। তা তিনি দিযেছিলেন। তাছাড়া আমার মধ্যে যে আদরে আদরে নষ্ট, একটু উদ্ধত ছোট্ট মেযেটি ছিল—তার প্রতিও ছিল তার অবাধ প্রশ্ৰয়। আমার বাপের বাড়ি ছিল না বলে আমার দুঃখটি তিনি বুঝতেন। একবার কোথায় যেন বেড়াতে যাবার কথা হয়েছিল। তিনি বললেন, খুব ভালো করে বেড়ানোটুকু উপভোগ করবে। আমাদের কথা ভেবে চট করে এসো না যেন। কিছুদিন থেকে এসো!
আর কেউ না বুকুক আমি বুঝেছি স্বামী হিসেবে তিনি কতখানি অনুভূতিপ্রবণ ছিলেন। নাহলে এমন কথা বলা কিন্তু সহজ বিষয় না।
‘কখনো পরীক্ষার সময় কলমে কালি ভরি নি। উনি সব ঠিকঠাক করে দিতেন। ক্লাসের খাতা দেখতাম যখন হাতের কাছে ডিকশনারি নিয়ে কখনো বসি নি। জানিই তো উনি আছেন। পাশের ঘর থেকে চেচিয়ে চেচিয়ে শব্দের বানান বা মানে জিজ্ঞেস করে নিতাম। ওঁর বলতে দেরি হলেই, ভয় দেখাতাম,—দাড়াও আসছি! তোমার কবিতা লেখা বের করছি!
উনি অমনি সহাস্যে আমার প্রশ্নগুলির উত্তর দিতেন। নাহলে মৃদুভাবে বলতেন, একসঙ্গে সব
লিখে এনে জিজ্ঞেস করলেই তো হয়!
‘মনে আছে নাটক করলাম আমরা। ঘরে-বাইরে’। আমি সেজেছিলাম মেজ বৌরানী। ওঁকে বললাম—টিকিট রইল, যেয়ো কিন্তু!
‘ভাবো, নাটক শেষ করে, বাড়ির দিকে ফিরছি, রীতিমতো রাতে। কিন্তু ভয় নেই। প্রায় দাপটের সঙ্গে। এসেই বুঝলাম, যান নি। রেগে-টেগে অস্থির, বললাম—“পাচশোবার বললাম যাবে! গেলে না কেন ? একদিন কবিতা লেখা কামাই দিতে পারো না!’ উনি বললেন, ‘আহা রাগ করো কেন ? তুমি করেছ! ভালোই তো হবে। হবে না? চলো খাবার ঠাণ্ড হয়ে যাবে, খাবে চলো।’
‘আমি তখনও রাগ করছি দেখে বললেন, —আচ্ছা আচ্ছা, কাল যাবো। ‘বলো তো, আজ নাটক হয়ে গেল, উনি কাল কোথায় যাবেন ? ‘আমার যত দাপট ছিল ওঁর কাছে। অন্য কিছুতে বকতেন না, শুধু ছেলেমেয়ে ছিল ওঁর প্রাণ, ওদের কিছু বললেই বকতেন।
‘মনে আছে লিখতে যদি চেয়ারে বসলেন তো আর জ্ঞান নেই। কিছুতেই গেঞ্জি ছাড়বেন না। আর আমি ওঁর গেঞ্জি কাচবই। তখন একটা বড় কাচি নিয়ে আসতাম। বলতাম, ‘কাটি ? পিঠ থেকে কেটে নিই গেঞ্জিটা ?”
‘হেসে খুলে দিতেন। ‘উনি যে চাকরি পেতেন না তা নয়। উনি চাকরি করতে চাইতেন না। বারবার বলতেন, বলো তো, কী নিদারুণ সময়ের অপচয়। বড় ক্ষতি হয়। এভাবে এতটা সময় চলে যাওয়া। আহা, যদি আমার এমন সঞ্চয় থাকত যে এভাবে সময় নষ্ট না করলেও চলত!.... ওঁর এই কথাটি বড় মনে পড়ে! আর একটি ব্যক্তিগত কথা মনে পড়ে, বিবাহিত জীবনের শুরুতে জ্যাঠামশাইকে যে কথাটি দিয়েছিলেন সারাজীবন তিনি তা রেখেছিলেন। আমাকে কোনোদিন কোনো কারণে ক্ষুন্ন করেন নি।
সাক্ষাৎকার : কবিতা সিংহ
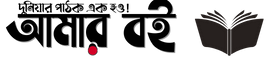


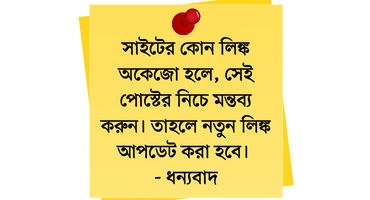







![[ছোট্টগল্প] সেক্সবয় - তসলিমা নাসরিন](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEizCNalHzbcL_TRO47frupqVrYhkJmfl_OaBixQzVrIC9gZtXtGiggWI52u_yo8X-cwdAfVwBlwyTJSaFM9F2lp5Qn4Kq0vWMi5DWKhVvP7UN-MkOFsO-kl7tIV3Xu874EhlsSm4r8fbNgR/w72-h72-p-k-no-nu/sboyt.png)








