
রং তুলির সত্যজিৎ
দেবাশীষ দেব
মুখ বন্ধ
১৯৬০ সালে সিনেমা জগৎ পত্রিকাতে সত্যজিৎ রায়কে নিয়ে লেখা একটি প্রবন্ধে খুবই অর্থপূর্ণ অথচ স্পষ্ট এই মন্তব্যটি করেছিলেন পূর্ণেন্দু পত্রী। বােঝা যায় একাধারে কবি, চিত্রশিল্পী, এবং পরবর্তীকালের একজন সফল চিত্রপরিচালক পত্রীমশাইয়ের আসল উদ্দেশ্য ছিল সত্যজিৎ চর্চার একটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ দিক সম্বন্ধে পাঠককে যথাসম্ভব সচেতন করে তোলা। একজন সম্পূর্ণ পেশাদার আর্টিস্ট হিসেবে কর্মজীবন শুরু করে একটানা বহু বছর যথেষ্ট সম্মানে কাটালেও সিনেমা তৈরি শুরু করার পর প্ৰায় রাতারাতি বিশ্বজোড়া সাফল্য এসে সত্যজিতের ছবি আঁকার জগৎটাকে যেন ক্রমশ আড়ালে ঠেলে দিয়েছিল। এর ফলে সিনেমার পাশে তার রং তুলিতে করা সমস্ত কাজ যে আপাতদৃষ্টিতে নেহাৎই অকিঞ্চিৎকর হয়ে উঠতে পারে অনেক আগে থেকেই এই রকম একটা আশঙ্কা প্ৰকাশ করেছিলেন পত্রীমশাই।
পত্রীমশাইয়ের আশঙ্কা যে একেবারেই অমূলক ছিল না তা ভবিষ্যতে প্রমাণিত হয়েছে। একের পর এক শিল্পগুণে ভরা অতি উচ্চমানের সব সিনেমা মানুষকে চিত্রপরিচালক সত্যজিতের প্রতি বিশেষ ভাবে আকৃষ্ট করে তুলবে। এতে আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই। কিন্তু এর পিছনে আর্টিস্ট সত্যজিতের যে কত বড় ভূমিকা রয়েছে তা নিয়ে আজও যেন অদ্ভূত এক উদাসীনতা চােখে পড়ে।
স্কুলে থাকতেই বাছাই করা বিদেশি সিনেমা দেখার অভ্যাস ছিল সত্যজিতের, বড় হয়ে সে সব নিয়ে ধীরে ধীরে গভীর চর্চাও শুরু করে দেন। তিনি। বিশেষ করে ফিল্মমেকিং-এর ব্যাপারটা তার কাছে একসময় রীতিমতো গবেষণার বিষয় হয়ে দাড়ায়। এর ফলে সিনেমার মধ্যে লুকিয়ে থাকা যাবতীয় সম্ভাবনা সত্যজিতের শিল্পচেতনাকে এতটাই অনুপ্রাণিত করে তুলেছিল যে শেষ পর্যন্ত আর্টিস্টের নিরাপদ চাকরি ছেড়ে দিয়ে তিনি অনিবাৰ্যভাবে সিনেমাকেই বেছে নিয়েছিলেন প্রধান কর্মক্ষেত্র হিসেবে। সেই সঙ্গে এটাও বলা যেতে পারে, জীবনের শেষ দিন অবধি একমাত্র সিনেমাই যেন তাঁর শিল্পসত্তাকে সৃষ্টির আনন্দে ভরিয়ে রেখেছিল।
অথচ শুধু আর্টিস্ট সত্যজিৎকে নিয়ে যদি আলোচনা করা হয় তা হলে তার প্রতিভার এমন একটা দিক সম্পর্কে জানা যাবে যেটা কিছু কম চমকপ্ৰদ নয়। একজন গ্রাফিক ডিজাইনার হিসেবে তার করা বিজ্ঞাপনের নকশা থেকে আরম্ভ করে বই বা সঙ্গে পাল্লা দিয়ে যে রীতিমতো আন্তর্জাতিক মানের হয়ে উঠেছিল। সে ব্যাপারে কোনও সন্দেহ নেই।
শিল্পী সত্যজিৎকে নিয়ে বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় অল্পবিস্তর লেখালিখি হয়েছে, তার কাজের কিছু নমুনা নিয়ে দু-একটি অ্যালবাম প্রকাশনা বা মাঝে মধ্যে প্রদর্শনীও হয়েছে, তবে এই কর্মকাণ্ডের কোনওটিই শিল্পী সত্যজিতের ধারাবাহিক সম্পূর্ণ পরিচয় ধরে রাখার চেষ্টা করেনি।
আসলে ছবি আঁকা বা ডিজাইন সংক্রান্ত যাবতীয় কাজ তিনি যে পরিস্থিতির মধ্যেই করে থাকুন না কেন এটা মনে রাখতে হবে তা ছিল সত্যজিতের সম্পূর্ণ আলাদা একটা শিল্পীসত্তা। পৃথিবীর অন্যতম সেরা চিত্রপরিচালক, আবার ছবি আঁকাতেও দিব্যি পারদশী ছিলেন, এই ধরনের একটা চলতি ধারণাকে প্রশ্রয় দিতে গিয়ে বিষয়টির প্ৰতি চিরকাল যথেষ্ট অবিচার করা হয়েছে। অথচ তাঁর সারা জীবনের প্রায় প্রতিটি শিল্প-সৃষ্টির মধ্যেই পাওয়া যায় গভীর নিষ্ঠা আর আত্মপ্রত্যয়ের ছোঁয়া। খুব সামান্য একটা কাজের মধ্যেও যে তিনি কতখানি ভাবনা চিন্তার প্রয়োগ ঘটিয়েছিলেন দেখে আশ্চর্য হতে হয়। এ নিয়ে পূর্ণাঙ্গ গবেষণায় উদ্যোগী হননি কেউ। তাই পত্রীমশাইয়ের কথার রেশ টেনেই বলা যায়, সত্যজিতের মৃত্যুর প্রায় দেড় যুগ পরেও তাকে জানা সে অর্থে অসম্পূর্ণই থেকে গিয়েছে।
অবশ্য এটাও ঠিক, গ্রাফিক ডিজাইনের যে অসংখ্য কাজ সত্যজিৎ প্রায় পঞ্চাশ বছর ধরে করে গিয়েছেন, সেগুলির মূল আর্ট ওয়ার্ক তো দূরের কথা, ছাপা হওয়া কপিও অনেক ক্ষেত্রে উদ্ধার করা অসম্ভব। ফলে সব একত্র করে একটা পুরোদস্তুর সংগ্ৰহ কোনওদিন তৈরি করা যাবে কি না সে ব্যাপারে যথেষ্ট সন্দেহ আছে।
তবু যা রয়েছে আর যা এখনও উদ্ধারযোগ্য তারই মধ্য থেকে প্রাসঙ্গিক কিছু কাজ বেছে নিয়ে চার পর্বে শিল্পী সত্যজিতের এই আলোচনা সাজানো হয়েছে। আশা করি এর ভিতর দিয়ে তার কাজের ধারা ও বিবর্তনের একটা চেহারা পাঠকের কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠবে।
“যে জিনিসটা ছেলেবয়স থেকে বেশ ভালোই পারতাম সেটা হল ছবি আঁকা।” এটা জানিয়েছিলেন সত্যজিৎ রায় তাঁর আত্মকথা “যখন ছোট ছিলাম”-এ (সন্দেশ, মে ১৯৮১)। বোঝা যায় এই ক্ষমতা তিনি পেয়েছিলেন বংশের ধারা অনুযায়ী। কারণ তার দাদু উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী ও বাবা সুকুমার রায় দু’জনেই একাধারে পেন্টার এবং ইলাষ্ট্রেটর হিসেবে বিশেষ পারদশী। শুধু তাই নয়, পরে যে সমস্ত ক্ষেত্রে সত্যজিৎ—প্রতিভার চূড়ান্ত বিকাশ ঘটতে দেখা গিয়েছে, তার মধ্যে একমাত্র ছবি আঁকাটাই তিনি শিখেছিলেন প্রথাগত তালিমের মধ্য দিয়ে। প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে ইকনমিক্সে গ্র্যাজুয়েট হওয়ার পর ১৯৪০-এর মাঝামাঝি শান্তিনিকেতনের কলাভবনে ভর্তি হয়েছিলেন সত্যজিৎ, একরকম তার মায়ের ইচ্ছেতেই। কারণ ফাইন আর্ট নিয়ে কাজ করার উৎসাহ তাঁর কোনওদিনই ছিল না। কমার্শিয়াল আটেই যাওয়া মোটামুটি ঠিক করে রেখেছিলেন তিনি, কিন্তু সেটা আবার কলাভবনে শেখানো হয় না। কিন্তু ওখানে গিয়ে ভারতবর্ষের শিল্পকলার ঐতিহ্যকে ভালভাবে জেনে এসে পরে কাজে লাগানো যাবে এই চিন্তাটাইছিল সত্যজিতের মনে । এ ব্যাপারে শান্তিনিকেতন তাকে মোটেই হতাশ করেনি। কলাভবনে নন্দলাল বসু এবং বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায়ের যে শুধু আরও পাকাপোক্ত হয়ে গিয়েছিল তাই নয়, সেই সঙ্গে তৈরি হয়েছিল আর্ট সম্পর্কে সম্পূর্ণ নতুন এক ধরনের উপলব্ধি।
অবশ্য কলাভবনের চার বছরের কোর্স শেষ না করে আড়াই বছরের মাথায় সত্যজিৎ ফিরে আসেন কলকাতায়। কারণ তার মনে হয়েছিল প্রয়োজনীয় যা কিছু তা ইতিমধ্যেই শেখা হয়ে গিয়েছে। এবং এই আড়াই বছর যে তাঁর জীবনে কতখানি মূল্যবান সে বিষয়ে তিনি নিজেই লিখেছেন, “শিল্পকলার ক্ষেত্রে পশ্চিমী ঐতিহ্যের যে প্রভাব, এতদিন আমার চেতনাকে তা-ই পুরোপুরি অধিকার করে রেখেছিল। মুগ্ধ হয়ে দেখেছি রেমব্রান্ট আর দা ভিঞ্চির শিল্পকলা। এবারে প্রাচ্য পৃথিবীর শিল্পকলার ঐশ্বৰ্যময় জগতের দরজাটা আমার চােখের সামনে খুলে গেল। চিনে ল্যান্ডস্কেপ, জাপানি কাঠখোদাই আর ভারতীয় মিনিয়েচার হঠাৎ ধাক্কা মেরে জাগিয়ে দিল আমার চেতনাকে৷ প্ৰাচীন শিল্পৈশ্বর্যের জন্যে ভারতবর্ষের যে-সব জায়গার খুব খ্যাতি, তিনজন বন্ধুর সঙ্গে সেই সময়েই আমি সেখানে যাই। অজন্তা, ইলোরা আর খাজুরাহাে দেখে আমার চােখ খুলে যায়।” (অপুর পাঁচালি, আনন্দ পাবলিশার্স, ১৯৯৫, পৃ. ১৭-১৮)
সেই সঙ্গে এটাও মনে রাখতে হবে নন্দলাল-এর কাজের স্টাইল এবং বৈচিত্ৰ্য কী দারুণ ভাবে অনুপ্রাণিত করেছিল সত্যজিৎকে, পরে যার প্রভাব বিশেষ ভাবে চোখে পড়ে তার বহু ইলাষ্ট্রেশনে। কলাভবনে অন্যান্যের মধ্যে রামকিঙ্কর আর বিনোদবিহারীর মতো শিল্পী পেন্টিং কিংবা ভাস্কর্যে যে সব পরীক্ষানিরীক্ষা করতেন তা যে অনেক সময় আধুনিক ওয়েস্টার্ন আর্ট-এর খুব কাছাকাছি চলে গিয়েও বিশেষ এক ধরনের ভারতীয়তা বজায় রাখত সেটাও তিনি লক্ষ করেছিলেন। এ ছাড়া ছবি আঁকার পাশাপাশি চর্চা করার সুযোগ এসেছিল ক্যালিগ্রাফি নিয়েও— এ ব্যাপারে আগে থেকেই যথেষ্ট উৎসাহ ছিল তার। আরও বড় কথা হল, শান্তিনিকেতনের খোলামেলা পরিবেশে সত্যজিতের মতো শহুরে মানুষের কাছে গ্রাম বাংলার স্বাভাবিক সৌন্দৰ্য অনেক বেশি স্পষ্টভাবে ধরা দিয়েছিল, জীবনে সেই প্রথম তিনি শেখেন কী ভাবে প্রকৃতিকে দেখতে হয়।
১৯৪২ সালের ডিসেম্বর মাসে শান্তিনিকেতনের পাটচুকিয়ে কলকাতায় ফিরে এসে পছন্দমতো একটা চাকরি পেতে কয়েক মাস অপেক্ষা করতে হয়েছিল সত্যজিৎকে। অবশেষে ১৯৪৩ সালের জুন মাসে বিজ্ঞাপন সংস্থা ডি. জে. কিমার-এ তিনি যোগ দেন জুনিয়র আর্টিস্ট হিসেবে। বাজার চলতি হরেকরকম পণ্যসামগ্ৰীীর প্রচার ও বিক্রির জন্য যে ধরনের ছবি বা ডিজাইনের প্রয়োজন হয় প্রধানত সেই সব আঁকার কথা ভেবেই কর্মজীবন শুরু করেছিলেন সত্যজিৎ। তবে গোড়ার দিকে কলাভবনের যাবতীয় শিক্ষাকে সম্ভবত সব থেকে সার্থকভাবে কাজে লাগাবার সুযোগ এসেছিল সিগনেট প্রেস থেকে প্রকাশিত বিভিন্ন বই-এর প্রচ্ছদ আর ইলাষ্ট্রেশন করতে গিয়ে। ১৯৪৩ সালেই কিমার-এর ম্যানেজার দিলীপকুমার গুপ্ত যিনি সবার কাছে পরিচিত ছিলেন ডি. কে.” নামে, তিনিই শুরু করেন এই প্রকাশনা সংস্থা। প্রতিষ্ঠানটির সঙ্গে সত্যজিৎ যে শুধু একজন কমার্শিয়াল আর্টিস্ট হিসেবে যুক্ত ছিলেন। তাই নয়, বরং বলা যায় ডি. কে.-র সঙ্গে একজোট হয়ে রীতিমতো বিপ্লব ঘটিয়ে ফেলেছিলেন বাংলা বই-এর গেট-আপ, ডিজাইন আর ছাপার ক্ষেত্রে। ডি. কে.-র স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে সত্যজিৎ নিজেই লিখেছেন– “বাংলা বই-এর অঙ্গসীেষ্ঠবে সিগনেট যে সম্পূর্ণ নতুন ধারার প্রবর্তন করেছিল তাতে কোনো সন্দেহ নেই। এর মূলে ছিল “ডি. কে.’-র গভীর জ্ঞান, অক্লান্ত পরিশ্রম এবং একরোখা পারফেকশনিজম।” (“কাজের মানুষ ডি.কে.',বিভিাব, দিলীপকুমার গুপ্ত সংখ্যা, ১৯৭৯, পৃষ্ঠা ২০)।
এই সিগনেট প্রেস থেকে প্রকাশিত বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পথের পাঁচালী উপন্যাসের সংক্ষিপ্ত সংস্করণ আম আঁটির ভেপুর জন্য অনেক অলংকরণ করেন। সত্যজিৎ। বলা যায় এই কাজের সূত্র ধরেই ‘‘পথের পাঁচালী” নিয়ে জীবনের প্রথম সিনেমাটি করার কথা মাথায় আসে তার। শুটিং শুরুর আগে এই সিনেমার চিত্ৰনাট্য হিসেবে যে ভাবে তিনি কালি-কলম দিয়ে বিভিন্ন দৃশ্যের স্কেচ একে সাজিয়েছিলেন তা আজও সিনেমার ইতিহাসে এক বিরল দৃষ্টান্ত হয়ে আছে।
১৯৫৫ সালে মুক্তি পাওয়া ‘‘পথের পাঁচালী”-র অভাবনীয় সাফল্য যেমন সত্যজিৎকে রাতারাতি পৃথিবীর প্রথম সারির ফিল্মমেকার হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করে জগৎ থেকে। সিনেমা নিয়ে পুরোপুরি ব্যস্ত হয়ে পড়ার পরেই তিনি ছেড়ে দেন বিজ্ঞাপন কোম্পানির চাকরি। সিগনেট প্রেস বা অন্যান্য ক্ষেত্রেও যেন অনেকটাই কমে যায় আগের সেই উদ্যম। তবে এই সিনেমার প্রয়োজনেই কিন্তু গ্রাফিক সংক্রান্ত নানা ধরনের কাজ প্রথম থেকেই নিজের হাতে করতে শুরু করেছিলেন সত্যজিৎ। পোস্টার, লোগো, বুকলেট কিংবা টাইটেল কার্ড আঁকা থেকে শুরু করে সাজপোশাক এমনকী সেট পরিকল্পনা করতে গিয়েও রীতিমতো কাজে লেগেছিল তার ছবি আঁকার অভিজ্ঞতা।
তবে এরই মধ্যে তাকে হঠাৎ ভীষণভাবে জড়িয়ে পড়তে হল একেবারে অন্য রকম এক কাজের সঙ্গে। ঘনিষ্ঠ বন্ধু সুভাষ মুখোপাধ্যায়কে নিয়ে তিনি ১৯৬১ সাল থেকে নতুনভাবে নিয়মিত বের করতে শুরু করলেন বন্ধ হয়ে যাওয়া ছোটদের মাসিক পত্রিকা সন্দেশ । আর এই সন্দেশ-কে কেন্দ্র করেই সিনেমার বাইরে সত্যজিতের গোটা কাজের জগৎটা যেন সম্পূর্ণ নতুন একটা দিকে মোড় নিল। ছোট ছোট পাঠকদের কথা ভেবে প্ৰবল উৎসাহে তিনি পত্রিকাটির প্রতিটি সংখ্যার জন্য প্রচ্ছদ থেকে শুরু করে ইলাষ্ট্রেশন, লোগো, কমিক স্ট্রিপ, লেটারিং ইত্যাদি নানারকম আঁকার কাজে ফিরে এলেন। সেই সঙ্গে সম্পাদনার দায়িত্ব যেন ভীষণভাবে উস্কে দিয়েছিল তাঁর লুকিয়ে থাকা সাহিত্যের প্রতিভাকেও। তার উপর নিজের লেখার ইলাষ্ট্রেশন নিজেকেই করতে হত সত্যজিৎকে। পরে সেগুলো বই আকারে ছাপতে গিয়ে প্রচ্ছদ আঁকার দায়িত্বটাও যোগ হল। তা ছাড়া বহু অনুরোধ রাখতে র্তাকে মাঝে মাঝেই বিভিন্ন ধরনের ডিজাইনের কাজও করে যেতে হয়েছে দীর্ঘ দিন ধরে। অবশ্য এই সত্যজিৎকে তখন আর ঠিক পেশাদার আর্টিস্ট বলা যাবে না। যা কিছু আঁকছিলেন সবই যেন নিজস্ব একটা তাগিদ থেকে সৃষ্টির একটা বিকল্প রাস্তা খোঁজা। হয়তো সেই কারণেই সত্যজিতের কাছে এর বিশেষ কোনও মূল্য ছিল না। এমনকী প্রথম জীবনে রীতিমতো পেশাদারি উদ্যোগ নিয়ে করা কাজগুলিকেও সেভাবে গুরুত্ব দেননি তিনি। এই উদাসীনতা স্পষ্ট তাঁর একটি লেখায়, [১৯৯০-এ দিল্লিতে অনুষ্ঠিত তাঁর গ্রাফিক আর্ট-এর প্রদর্শনীর ক্যাটালগ-এর ভূমিকা]— “Since I consider myself primarily to be a filmmaker and secondarily to be a writer of stories for young people, I have never taken my graphic Work seriously and I certainly never considered it worthy of being exposed to the public.” হয়তো এই মনোভাবের কারণেই শিল্পকলার বিভিন্ন ধারা সম্পর্কে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি অথবা বিশ্লেষণ নিয়ে কদাচিৎ তিনি আলোচনা করেছেন।
দেবাশীষ দেব
মুখ বন্ধ
“তিনি যে চিত্রকর তা আজও সাধারণ্যে যথেষ্ট অজ্ঞাত। অথচ চিত্রকর সত্যজিৎকে না জেনে শুধু চলচ্চিত্রকার সত্যজিৎকে জানা র্তাকে সম্পূর্ণ জানা নয়।”
১৯৬০ সালে সিনেমা জগৎ পত্রিকাতে সত্যজিৎ রায়কে নিয়ে লেখা একটি প্রবন্ধে খুবই অর্থপূর্ণ অথচ স্পষ্ট এই মন্তব্যটি করেছিলেন পূর্ণেন্দু পত্রী। বােঝা যায় একাধারে কবি, চিত্রশিল্পী, এবং পরবর্তীকালের একজন সফল চিত্রপরিচালক পত্রীমশাইয়ের আসল উদ্দেশ্য ছিল সত্যজিৎ চর্চার একটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ দিক সম্বন্ধে পাঠককে যথাসম্ভব সচেতন করে তোলা। একজন সম্পূর্ণ পেশাদার আর্টিস্ট হিসেবে কর্মজীবন শুরু করে একটানা বহু বছর যথেষ্ট সম্মানে কাটালেও সিনেমা তৈরি শুরু করার পর প্ৰায় রাতারাতি বিশ্বজোড়া সাফল্য এসে সত্যজিতের ছবি আঁকার জগৎটাকে যেন ক্রমশ আড়ালে ঠেলে দিয়েছিল। এর ফলে সিনেমার পাশে তার রং তুলিতে করা সমস্ত কাজ যে আপাতদৃষ্টিতে নেহাৎই অকিঞ্চিৎকর হয়ে উঠতে পারে অনেক আগে থেকেই এই রকম একটা আশঙ্কা প্ৰকাশ করেছিলেন পত্রীমশাই।
পত্রীমশাইয়ের আশঙ্কা যে একেবারেই অমূলক ছিল না তা ভবিষ্যতে প্রমাণিত হয়েছে। একের পর এক শিল্পগুণে ভরা অতি উচ্চমানের সব সিনেমা মানুষকে চিত্রপরিচালক সত্যজিতের প্রতি বিশেষ ভাবে আকৃষ্ট করে তুলবে। এতে আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই। কিন্তু এর পিছনে আর্টিস্ট সত্যজিতের যে কত বড় ভূমিকা রয়েছে তা নিয়ে আজও যেন অদ্ভূত এক উদাসীনতা চােখে পড়ে।
স্কুলে থাকতেই বাছাই করা বিদেশি সিনেমা দেখার অভ্যাস ছিল সত্যজিতের, বড় হয়ে সে সব নিয়ে ধীরে ধীরে গভীর চর্চাও শুরু করে দেন। তিনি। বিশেষ করে ফিল্মমেকিং-এর ব্যাপারটা তার কাছে একসময় রীতিমতো গবেষণার বিষয় হয়ে দাড়ায়। এর ফলে সিনেমার মধ্যে লুকিয়ে থাকা যাবতীয় সম্ভাবনা সত্যজিতের শিল্পচেতনাকে এতটাই অনুপ্রাণিত করে তুলেছিল যে শেষ পর্যন্ত আর্টিস্টের নিরাপদ চাকরি ছেড়ে দিয়ে তিনি অনিবাৰ্যভাবে সিনেমাকেই বেছে নিয়েছিলেন প্রধান কর্মক্ষেত্র হিসেবে। সেই সঙ্গে এটাও বলা যেতে পারে, জীবনের শেষ দিন অবধি একমাত্র সিনেমাই যেন তাঁর শিল্পসত্তাকে সৃষ্টির আনন্দে ভরিয়ে রেখেছিল।
অথচ শুধু আর্টিস্ট সত্যজিৎকে নিয়ে যদি আলোচনা করা হয় তা হলে তার প্রতিভার এমন একটা দিক সম্পর্কে জানা যাবে যেটা কিছু কম চমকপ্ৰদ নয়। একজন গ্রাফিক ডিজাইনার হিসেবে তার করা বিজ্ঞাপনের নকশা থেকে আরম্ভ করে বই বা সঙ্গে পাল্লা দিয়ে যে রীতিমতো আন্তর্জাতিক মানের হয়ে উঠেছিল। সে ব্যাপারে কোনও সন্দেহ নেই।
শিল্পী সত্যজিৎকে নিয়ে বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় অল্পবিস্তর লেখালিখি হয়েছে, তার কাজের কিছু নমুনা নিয়ে দু-একটি অ্যালবাম প্রকাশনা বা মাঝে মধ্যে প্রদর্শনীও হয়েছে, তবে এই কর্মকাণ্ডের কোনওটিই শিল্পী সত্যজিতের ধারাবাহিক সম্পূর্ণ পরিচয় ধরে রাখার চেষ্টা করেনি।
আসলে ছবি আঁকা বা ডিজাইন সংক্রান্ত যাবতীয় কাজ তিনি যে পরিস্থিতির মধ্যেই করে থাকুন না কেন এটা মনে রাখতে হবে তা ছিল সত্যজিতের সম্পূর্ণ আলাদা একটা শিল্পীসত্তা। পৃথিবীর অন্যতম সেরা চিত্রপরিচালক, আবার ছবি আঁকাতেও দিব্যি পারদশী ছিলেন, এই ধরনের একটা চলতি ধারণাকে প্রশ্রয় দিতে গিয়ে বিষয়টির প্ৰতি চিরকাল যথেষ্ট অবিচার করা হয়েছে। অথচ তাঁর সারা জীবনের প্রায় প্রতিটি শিল্প-সৃষ্টির মধ্যেই পাওয়া যায় গভীর নিষ্ঠা আর আত্মপ্রত্যয়ের ছোঁয়া। খুব সামান্য একটা কাজের মধ্যেও যে তিনি কতখানি ভাবনা চিন্তার প্রয়োগ ঘটিয়েছিলেন দেখে আশ্চর্য হতে হয়। এ নিয়ে পূর্ণাঙ্গ গবেষণায় উদ্যোগী হননি কেউ। তাই পত্রীমশাইয়ের কথার রেশ টেনেই বলা যায়, সত্যজিতের মৃত্যুর প্রায় দেড় যুগ পরেও তাকে জানা সে অর্থে অসম্পূর্ণই থেকে গিয়েছে।
অবশ্য এটাও ঠিক, গ্রাফিক ডিজাইনের যে অসংখ্য কাজ সত্যজিৎ প্রায় পঞ্চাশ বছর ধরে করে গিয়েছেন, সেগুলির মূল আর্ট ওয়ার্ক তো দূরের কথা, ছাপা হওয়া কপিও অনেক ক্ষেত্রে উদ্ধার করা অসম্ভব। ফলে সব একত্র করে একটা পুরোদস্তুর সংগ্ৰহ কোনওদিন তৈরি করা যাবে কি না সে ব্যাপারে যথেষ্ট সন্দেহ আছে।
তবু যা রয়েছে আর যা এখনও উদ্ধারযোগ্য তারই মধ্য থেকে প্রাসঙ্গিক কিছু কাজ বেছে নিয়ে চার পর্বে শিল্পী সত্যজিতের এই আলোচনা সাজানো হয়েছে। আশা করি এর ভিতর দিয়ে তার কাজের ধারা ও বিবর্তনের একটা চেহারা পাঠকের কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠবে।
“যে জিনিসটা ছেলেবয়স থেকে বেশ ভালোই পারতাম সেটা হল ছবি আঁকা।” এটা জানিয়েছিলেন সত্যজিৎ রায় তাঁর আত্মকথা “যখন ছোট ছিলাম”-এ (সন্দেশ, মে ১৯৮১)। বোঝা যায় এই ক্ষমতা তিনি পেয়েছিলেন বংশের ধারা অনুযায়ী। কারণ তার দাদু উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী ও বাবা সুকুমার রায় দু’জনেই একাধারে পেন্টার এবং ইলাষ্ট্রেটর হিসেবে বিশেষ পারদশী। শুধু তাই নয়, পরে যে সমস্ত ক্ষেত্রে সত্যজিৎ—প্রতিভার চূড়ান্ত বিকাশ ঘটতে দেখা গিয়েছে, তার মধ্যে একমাত্র ছবি আঁকাটাই তিনি শিখেছিলেন প্রথাগত তালিমের মধ্য দিয়ে। প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে ইকনমিক্সে গ্র্যাজুয়েট হওয়ার পর ১৯৪০-এর মাঝামাঝি শান্তিনিকেতনের কলাভবনে ভর্তি হয়েছিলেন সত্যজিৎ, একরকম তার মায়ের ইচ্ছেতেই। কারণ ফাইন আর্ট নিয়ে কাজ করার উৎসাহ তাঁর কোনওদিনই ছিল না। কমার্শিয়াল আটেই যাওয়া মোটামুটি ঠিক করে রেখেছিলেন তিনি, কিন্তু সেটা আবার কলাভবনে শেখানো হয় না। কিন্তু ওখানে গিয়ে ভারতবর্ষের শিল্পকলার ঐতিহ্যকে ভালভাবে জেনে এসে পরে কাজে লাগানো যাবে এই চিন্তাটাইছিল সত্যজিতের মনে । এ ব্যাপারে শান্তিনিকেতন তাকে মোটেই হতাশ করেনি। কলাভবনে নন্দলাল বসু এবং বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায়ের যে শুধু আরও পাকাপোক্ত হয়ে গিয়েছিল তাই নয়, সেই সঙ্গে তৈরি হয়েছিল আর্ট সম্পর্কে সম্পূর্ণ নতুন এক ধরনের উপলব্ধি।
অবশ্য কলাভবনের চার বছরের কোর্স শেষ না করে আড়াই বছরের মাথায় সত্যজিৎ ফিরে আসেন কলকাতায়। কারণ তার মনে হয়েছিল প্রয়োজনীয় যা কিছু তা ইতিমধ্যেই শেখা হয়ে গিয়েছে। এবং এই আড়াই বছর যে তাঁর জীবনে কতখানি মূল্যবান সে বিষয়ে তিনি নিজেই লিখেছেন, “শিল্পকলার ক্ষেত্রে পশ্চিমী ঐতিহ্যের যে প্রভাব, এতদিন আমার চেতনাকে তা-ই পুরোপুরি অধিকার করে রেখেছিল। মুগ্ধ হয়ে দেখেছি রেমব্রান্ট আর দা ভিঞ্চির শিল্পকলা। এবারে প্রাচ্য পৃথিবীর শিল্পকলার ঐশ্বৰ্যময় জগতের দরজাটা আমার চােখের সামনে খুলে গেল। চিনে ল্যান্ডস্কেপ, জাপানি কাঠখোদাই আর ভারতীয় মিনিয়েচার হঠাৎ ধাক্কা মেরে জাগিয়ে দিল আমার চেতনাকে৷ প্ৰাচীন শিল্পৈশ্বর্যের জন্যে ভারতবর্ষের যে-সব জায়গার খুব খ্যাতি, তিনজন বন্ধুর সঙ্গে সেই সময়েই আমি সেখানে যাই। অজন্তা, ইলোরা আর খাজুরাহাে দেখে আমার চােখ খুলে যায়।” (অপুর পাঁচালি, আনন্দ পাবলিশার্স, ১৯৯৫, পৃ. ১৭-১৮)
সেই সঙ্গে এটাও মনে রাখতে হবে নন্দলাল-এর কাজের স্টাইল এবং বৈচিত্ৰ্য কী দারুণ ভাবে অনুপ্রাণিত করেছিল সত্যজিৎকে, পরে যার প্রভাব বিশেষ ভাবে চোখে পড়ে তার বহু ইলাষ্ট্রেশনে। কলাভবনে অন্যান্যের মধ্যে রামকিঙ্কর আর বিনোদবিহারীর মতো শিল্পী পেন্টিং কিংবা ভাস্কর্যে যে সব পরীক্ষানিরীক্ষা করতেন তা যে অনেক সময় আধুনিক ওয়েস্টার্ন আর্ট-এর খুব কাছাকাছি চলে গিয়েও বিশেষ এক ধরনের ভারতীয়তা বজায় রাখত সেটাও তিনি লক্ষ করেছিলেন। এ ছাড়া ছবি আঁকার পাশাপাশি চর্চা করার সুযোগ এসেছিল ক্যালিগ্রাফি নিয়েও— এ ব্যাপারে আগে থেকেই যথেষ্ট উৎসাহ ছিল তার। আরও বড় কথা হল, শান্তিনিকেতনের খোলামেলা পরিবেশে সত্যজিতের মতো শহুরে মানুষের কাছে গ্রাম বাংলার স্বাভাবিক সৌন্দৰ্য অনেক বেশি স্পষ্টভাবে ধরা দিয়েছিল, জীবনে সেই প্রথম তিনি শেখেন কী ভাবে প্রকৃতিকে দেখতে হয়।
১৯৪২ সালের ডিসেম্বর মাসে শান্তিনিকেতনের পাটচুকিয়ে কলকাতায় ফিরে এসে পছন্দমতো একটা চাকরি পেতে কয়েক মাস অপেক্ষা করতে হয়েছিল সত্যজিৎকে। অবশেষে ১৯৪৩ সালের জুন মাসে বিজ্ঞাপন সংস্থা ডি. জে. কিমার-এ তিনি যোগ দেন জুনিয়র আর্টিস্ট হিসেবে। বাজার চলতি হরেকরকম পণ্যসামগ্ৰীীর প্রচার ও বিক্রির জন্য যে ধরনের ছবি বা ডিজাইনের প্রয়োজন হয় প্রধানত সেই সব আঁকার কথা ভেবেই কর্মজীবন শুরু করেছিলেন সত্যজিৎ। তবে গোড়ার দিকে কলাভবনের যাবতীয় শিক্ষাকে সম্ভবত সব থেকে সার্থকভাবে কাজে লাগাবার সুযোগ এসেছিল সিগনেট প্রেস থেকে প্রকাশিত বিভিন্ন বই-এর প্রচ্ছদ আর ইলাষ্ট্রেশন করতে গিয়ে। ১৯৪৩ সালেই কিমার-এর ম্যানেজার দিলীপকুমার গুপ্ত যিনি সবার কাছে পরিচিত ছিলেন ডি. কে.” নামে, তিনিই শুরু করেন এই প্রকাশনা সংস্থা। প্রতিষ্ঠানটির সঙ্গে সত্যজিৎ যে শুধু একজন কমার্শিয়াল আর্টিস্ট হিসেবে যুক্ত ছিলেন। তাই নয়, বরং বলা যায় ডি. কে.-র সঙ্গে একজোট হয়ে রীতিমতো বিপ্লব ঘটিয়ে ফেলেছিলেন বাংলা বই-এর গেট-আপ, ডিজাইন আর ছাপার ক্ষেত্রে। ডি. কে.-র স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে সত্যজিৎ নিজেই লিখেছেন– “বাংলা বই-এর অঙ্গসীেষ্ঠবে সিগনেট যে সম্পূর্ণ নতুন ধারার প্রবর্তন করেছিল তাতে কোনো সন্দেহ নেই। এর মূলে ছিল “ডি. কে.’-র গভীর জ্ঞান, অক্লান্ত পরিশ্রম এবং একরোখা পারফেকশনিজম।” (“কাজের মানুষ ডি.কে.',বিভিাব, দিলীপকুমার গুপ্ত সংখ্যা, ১৯৭৯, পৃষ্ঠা ২০)।
এই সিগনেট প্রেস থেকে প্রকাশিত বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পথের পাঁচালী উপন্যাসের সংক্ষিপ্ত সংস্করণ আম আঁটির ভেপুর জন্য অনেক অলংকরণ করেন। সত্যজিৎ। বলা যায় এই কাজের সূত্র ধরেই ‘‘পথের পাঁচালী” নিয়ে জীবনের প্রথম সিনেমাটি করার কথা মাথায় আসে তার। শুটিং শুরুর আগে এই সিনেমার চিত্ৰনাট্য হিসেবে যে ভাবে তিনি কালি-কলম দিয়ে বিভিন্ন দৃশ্যের স্কেচ একে সাজিয়েছিলেন তা আজও সিনেমার ইতিহাসে এক বিরল দৃষ্টান্ত হয়ে আছে।
১৯৫৫ সালে মুক্তি পাওয়া ‘‘পথের পাঁচালী”-র অভাবনীয় সাফল্য যেমন সত্যজিৎকে রাতারাতি পৃথিবীর প্রথম সারির ফিল্মমেকার হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করে জগৎ থেকে। সিনেমা নিয়ে পুরোপুরি ব্যস্ত হয়ে পড়ার পরেই তিনি ছেড়ে দেন বিজ্ঞাপন কোম্পানির চাকরি। সিগনেট প্রেস বা অন্যান্য ক্ষেত্রেও যেন অনেকটাই কমে যায় আগের সেই উদ্যম। তবে এই সিনেমার প্রয়োজনেই কিন্তু গ্রাফিক সংক্রান্ত নানা ধরনের কাজ প্রথম থেকেই নিজের হাতে করতে শুরু করেছিলেন সত্যজিৎ। পোস্টার, লোগো, বুকলেট কিংবা টাইটেল কার্ড আঁকা থেকে শুরু করে সাজপোশাক এমনকী সেট পরিকল্পনা করতে গিয়েও রীতিমতো কাজে লেগেছিল তার ছবি আঁকার অভিজ্ঞতা।
তবে এরই মধ্যে তাকে হঠাৎ ভীষণভাবে জড়িয়ে পড়তে হল একেবারে অন্য রকম এক কাজের সঙ্গে। ঘনিষ্ঠ বন্ধু সুভাষ মুখোপাধ্যায়কে নিয়ে তিনি ১৯৬১ সাল থেকে নতুনভাবে নিয়মিত বের করতে শুরু করলেন বন্ধ হয়ে যাওয়া ছোটদের মাসিক পত্রিকা সন্দেশ । আর এই সন্দেশ-কে কেন্দ্র করেই সিনেমার বাইরে সত্যজিতের গোটা কাজের জগৎটা যেন সম্পূর্ণ নতুন একটা দিকে মোড় নিল। ছোট ছোট পাঠকদের কথা ভেবে প্ৰবল উৎসাহে তিনি পত্রিকাটির প্রতিটি সংখ্যার জন্য প্রচ্ছদ থেকে শুরু করে ইলাষ্ট্রেশন, লোগো, কমিক স্ট্রিপ, লেটারিং ইত্যাদি নানারকম আঁকার কাজে ফিরে এলেন। সেই সঙ্গে সম্পাদনার দায়িত্ব যেন ভীষণভাবে উস্কে দিয়েছিল তাঁর লুকিয়ে থাকা সাহিত্যের প্রতিভাকেও। তার উপর নিজের লেখার ইলাষ্ট্রেশন নিজেকেই করতে হত সত্যজিৎকে। পরে সেগুলো বই আকারে ছাপতে গিয়ে প্রচ্ছদ আঁকার দায়িত্বটাও যোগ হল। তা ছাড়া বহু অনুরোধ রাখতে র্তাকে মাঝে মাঝেই বিভিন্ন ধরনের ডিজাইনের কাজও করে যেতে হয়েছে দীর্ঘ দিন ধরে। অবশ্য এই সত্যজিৎকে তখন আর ঠিক পেশাদার আর্টিস্ট বলা যাবে না। যা কিছু আঁকছিলেন সবই যেন নিজস্ব একটা তাগিদ থেকে সৃষ্টির একটা বিকল্প রাস্তা খোঁজা। হয়তো সেই কারণেই সত্যজিতের কাছে এর বিশেষ কোনও মূল্য ছিল না। এমনকী প্রথম জীবনে রীতিমতো পেশাদারি উদ্যোগ নিয়ে করা কাজগুলিকেও সেভাবে গুরুত্ব দেননি তিনি। এই উদাসীনতা স্পষ্ট তাঁর একটি লেখায়, [১৯৯০-এ দিল্লিতে অনুষ্ঠিত তাঁর গ্রাফিক আর্ট-এর প্রদর্শনীর ক্যাটালগ-এর ভূমিকা]— “Since I consider myself primarily to be a filmmaker and secondarily to be a writer of stories for young people, I have never taken my graphic Work seriously and I certainly never considered it worthy of being exposed to the public.” হয়তো এই মনোভাবের কারণেই শিল্পকলার বিভিন্ন ধারা সম্পর্কে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি অথবা বিশ্লেষণ নিয়ে কদাচিৎ তিনি আলোচনা করেছেন।
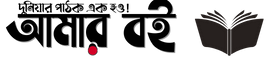

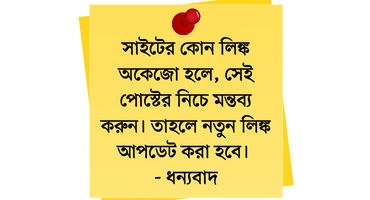







![[ছোট্টগল্প] সেক্সবয় - তসলিমা নাসরিন](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEizCNalHzbcL_TRO47frupqVrYhkJmfl_OaBixQzVrIC9gZtXtGiggWI52u_yo8X-cwdAfVwBlwyTJSaFM9F2lp5Qn4Kq0vWMi5DWKhVvP7UN-MkOFsO-kl7tIV3Xu874EhlsSm4r8fbNgR/w72-h72-p-k-no-nu/sboyt.png)








