
বাংলা সাহিত্য ও বাঙালি মধ্যবিত্ত - সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী
আলোচনার বিষয় আধুনিক বাংলা সাহিত্য, যে-সাহিত্য শিক্ষিত মধ্যবিত্ত বাঙালি সৃষ্টি করেছে, তার নিজের প্রয়োজনে ও আগ্রহে। ওই শ্রেণীর সঙ্গে এই সাহিত্যের সম্পর্ক তাই অত্যন্ত নিবিড়। মধ্যবিত্তের জীবনে নানা আকাক্সক্ষা থাকে, থাকে স্বপ্ন এবং সেই সঙ্গে সংকট, সাহিত্যে যার প্রতিফলন ঘটেছে। মধ্যবিত্তের সঙ্গে জনগণের দূরত্ব ও নৈকট্য এবং ওই শেণীর ভেতরকার দ্বন্দ্বও এই সাহিত্যে আছে। নর-নারীর সম্পর্ক তো বটেই, হিন্দু-মুসলমান সম্পর্কটিও এক সময়ে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। বাঙালি মধ্যবিত্ত সবচেয়ে অধিক গুরুত্ব দিয়েছে শিক্ষাকে, তার পরে সাহিত্যকে। শিক্ষাকে গুরুত্বপূর্ণ মনে করা সাহিত্যের মর্যাদা বাড়িয়েছে।
আলোচনা শুরু হয়েছে ১৭৭৮-এর একটি ঘটনার উল্লেখ দিয়ে; যেটি হল একজন ইংরেজের হাতে বাংলা ভাষার প্রথম ব্যাকরণ গ্রন্থের রচনা। এ ঘটনা এ কথাটা বলছে যে, দেশের নতুন শাসকেরা বাংলা ভাষা সম্পর্কে জানতে চাচ্ছে এবং বলছে এ কথাও যে, তাদের এ জ্ঞান-অণ্বেষনটা উদ্দেশ্যহীন নয়, উদ্দেশ্য রয়েছে, আর সেটা হল নিজেদের কর্তৃত্বকে আরও বিস্তৃত ও গভীর করা। অস্ত্রের সাহায্যে তো শাসন করবেই, ঠিক করেছে অধীনদের আরও অধীন করার জন্য জ্ঞানেরও দরকার পড়বে। ওই বিদেশী শাসনের নানা ধরনের প্রভাব আমরা বাংলা সাহিত্যে প্রত্যক্ষ করি। প্রভাব বিশেষ রূপে কার্যকর হয়েছে ইংরেজি-শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মধ্য দিয়েই। এই মধ্যবিত্ত শ্রেণীই আধুনিক বাংলা সাহিত্যের একাধারে স্রষ্টা ও পাঠক, এবং শ্রেণীটি নিজে যে গড়ে উঠেছে তাও ইংরেজদের আনুকূল্য লাভের ভেতর দিয়েই। শাসক ইংরেজ যে বাংলা ভাষার ব্যাকরণ তৈরি করে দিয়েছে এটা ঠিক নয়, তবে আধুনিক বাংলা সাহিত্যের সামাজিক ব্যাকরণ তৈরিকে তারা যে প্রভাবিত করেছে তাতে কোনো সন্দেহ নেই।
সামাজিক ওই ব্যাকরণের একটি উপাদান হচ্ছে জাতীয়তাবাদ। বাঙালির জন্য পরাধীনতা নতুন অভিজ্ঞতা নয়, কিন্তু ইংরেজ শাসনামলে পরাধীনতার ফলে যে জাতীয়তাবাদী স্পৃহা জেগেছিল তেমনটি আগে কখনও ঘটেনি। অন্য বিজেতারা এখানে এসে স্থায়ীভাবে রয়ে গেছে, কিন্তু ইংরেজরা যে বসবাসের জন্য আসেনি, বাণিজ্যের জন্যই এসেছে এটা ছিল স্পষ্ট। বাণিজ্যের স্বার্থে তারা সাম্রাজ্য গড়েছে। কেবল সৈন্য দিয়ে শাসন করেনি, ভাষা দিয়েও ওই কাজ করেছে। বাঙালি মধ্যবিত্ত ইংরেজদের আনুকূল্য পেয়েছে আবার তার হাতে অপমানিতও হয়েছে; সে বুঝে নিয়েছে যে ইংরেজরা এখানে বসতি স্থাপন করেব না ঠিকই, কিন্তু আবার চলেও যে যাবে তাও নয়; তাছাড়া চলে যাক এটা যে মধ্যবিত্তরা শ্রেণীগতভাবে চেয়েছে এমনও নয়, তাদের স্বার্থ ইংরেজ শাসনকে সমর্থন করেছে। কাজেই ইংরেজ-বিরোধিতা আর ইংরেজ-সমর্থন পরস্পরবিরোধী এ দুই কাজ একসঙ্গেই চলেছে।
স্বাধীনতার জন্য জাতীয়তাবাদী সংগ্রামের আবশ্যকতার বোধটা ইংরেজ বিরোধিতারই ফলশ্র“তি। বাংলা ভাষা চর্চার মধ্যে জাতীয়তাবাদী অনুপ্রেরণা ছিল বৈকি, যারা ওই অনুপ্রেরণাটা বোধ করেনি তারা তাঁবেদারিকে স্বাধীনতা বলে গণ্য করেছে। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনক ঘটনা হল এই যে, সাহিত্যের ক্ষেত্রে ওই জাতীয়তাবাদ ইংরেজকে শত্র“ বলে সরাসরি চিহ্নিত করেনি ভয়ে। ভয় ছিল স্বার্থহানির; ভয় ছিল ইংরেজদের কোপানলে পতনের। ভীত জাতীয়তাবাদের ভুল ধারাটাকে দেখা গেল সামনে না এগিয়ে পিছু হটে গিয়ে আশ্রয় নিচ্ছে ধর্মের কাছে, পরিণত হচ্ছে ধর্মীয় পুনর্জাগরণবাদে। ওই পুনর্জাগরণবাদের পক্ষে অস্বাভাবিক হয়নি সাম্প্রদায়িকতাকে পুষ্ট করা। সাম্প্রদায়িকতার সৃষ্টিতে ইংরেজের সুবিধাবাদী উস্কানি যে ছিল তাতে সন্দেহ নেই, কিন্তু তার মূলটা যে ছিল অর্থনৈতিক, তা অনস্বীকার্য। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে হিন্দু মধ্যবিত্ত এগিয়ে ছিল, মুসলমান মধ্যবিত্ত কিছুটা বিলম্বে এসেছে, এসে পেশা ও রাজনীতিতে নিজের জন্য জায়গা চেয়েছে। জায়গা নিয়ে এই বিরোধটাই হচ্ছে সাম্প্রদায়িকতার মূল উৎস। ধর্ম কাজ করেছে পরিচয়ের চিহ্ন ও উত্তেজক সহকারী হিসেবে।
ভাষা সবসময়ই ইহজাগতিক, সাহিত্যেরও হওয়ার কথা সেরকমই, কিন্তু আধুনিক বাংলা সাহিত্যে ধর্ম প্রবেশ করেছে, এমনকি কার্যকরও থেকেছে, আর ভাষাও যে সাম্প্রদায়িকতার প্রভাব এড়াতে পেরেছে তা নয়।
জাতীয়তাবাদ অত্যন্ত স্পর্শকাতররূপে শত্র“সচেতন। শত্র“র উপস্থিতি না থাকলে সে জোর পায় না, এগোতে পারে না। হিন্দু মধ্যবিত্ত নিজেকে কেবল বাঙালি ভাবেনি, হিন্দুও ভেবেছে এবং এজন্যই অনেক সময় ইংরেজের চেয়েও মুসলমানকে সে বড় শত্র“ হিসেবে দেখেছে। আÍপরিচয়ের প্রশ্নেও ওই মধ্যবিত্তকে ধর্মের কাছে যেতে হচ্ছিল, বিধর্মী ইংরেজের বিপরীতে দাঁড়িয়ে সে যে তার ধর্মীয় পরিচয়কেই উচ্চে তুলে ধরবে এতে কোনো অস্বাভাবিকতা ছিল না। ধর্ম পুরাতন বন্ধু, নির্ভরযোগ্য আশ্রয়দাতা; তার কাছে গিয়ে নিরাপদে ইংরেজ-বিরোধিতাও সম্ভবপর, কেননা বিরোধিতাটা তখন আর রাজনৈতিক থাকবে না, রূপ নেবে ধর্মীয় এবং ধর্মের ব্যাপারে ইংরেজের তেমন কোনো মাথাব্যথা ছিল না, সে এসেছে ব্যবসা-বাণিজ্য করতে, ধর্ম নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করাটা তার ব্যবসার জন্য উপকারী নয়, বরঞ্চ ক্ষতিকর।
মধ্যবিত্তের এ ধর্মাশ্রয়িতা বাঙালির জন্য রাজনৈতিকভাবে অত্যন্ত ক্ষতিকর হয়েছে, কেননা তা সাম্রাজ্যবাদকে পুষ্ট করেছে এবং শেষ পর্যন্ত দেশকে দুই রাষ্ট্রে ভাগ করে ছেড়েছে। ধর্মাশ্রয়িতা সাহিত্যের জন্যও ইতিবাচক ফল বহন করে আনেনি। কেননা সাহিত্যচর্চার ক্ষেত্রে সে পৃষ্ঠপোষকতা দিয়েছে ভাববাদককে এবং সমর্থন করেছে সাম্প্রদায়িকতাকে।
সাহিত্যের সামাজিক ব্যাকরণে এ সত্য ও উল্লেখযোগ্য নিয়ামক যে, বাঙালি মধ্যবিত্ত সাহিত্যচর্চাকে অত্যন্ত উচ্চমূল্য দিয়ে এসেছে। এর একটা সহজ কারণ এই যে, আÍপ্রকাশের অন্য মাধ্যমগুলো তার পক্ষে আয়ত্ত করা সহজ হয়নি। স্থাপত্য ও ভাস্কর্যের উপকরণ এদেশে সীমিত। চিত্রকলাকে রক্ষা করা কঠিন। নৃত্যের ব্যাপারে সামাজিক ও ধর্মীয় বিধিনিষেধ ছিল। তুলনায় বই লেখা সহজ এবং বাঙালি তা লিখলেও। তাছাড়া সাহিত্য তার জন্য কেবল যে আÍপ্রকাশের মাধ্যম ছিল তা নয়, ছিল চিত্তবিনোদনের সুস্থ উপায় এবং ছিল অন্য বাঙালির এবং বহির্বিশ্বের সঙ্গে যোগাযোগের ক্ষেত্র। নিজের চারপাশে যা দেখেছে এবং বাইরের বিশ্ব থেকে যা সংগ্রহ করেছে তা সে ব্যবহার করেছে সাহিত্য রচনায়।
বাঙালির আÍপরিচয়ের ক্ষেত্রে একটা সমস্যা ছিল উত্তর ভারতের সঙ্গে তার সম্পর্ক। উত্তর ভারত বাঙালিকে হিন্দু কিংবা মুসলমান হতে সাহায্য করেছে, বাঙালি হতে পরামর্শ দেয়নি। অথচ ভাষা বাঙালিকে জানিয়ে দিয়েছে যে, বাঙালিরা উত্তর ভারতের সম্প্রসারণ নয়, তারা স্বতন্ত্র। স্বাতন্ত্র্যের এ বোধকে লালন করা বাঙালির জন্য স্বাভাবিক ছিল, আধুনিক বাংলা সাহিত্যে ওই লালন-পালনটা রয়েছেও, কিন্তু সর্বভারতীয় উৎপাতটা যে এখানে-সেখানে দেখা যায়নি তা নয়। বলা বাহুল্য, সর্বভারতীয়তার এই বোধটাও ইংরেজি শাসনেরই ফল, তার আগে ভারতবর্ষে বহু অঞ্চল ছিল, অখণ্ড ভারত বলে কিছু ছিল না।
ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির অনেক দানের মধ্যে একটি হল কলকাতা শহর। ছোটখাটো লন্ডন একটি; প্রবাসে স্বদেশবাসের আয়োজনÑ ইংরেজের জন্য। মধ্যবিত্ত বাঙালির পক্ষে সেখানে সুযোগ সন্ধান খুবই সম্ভবপর। ওই শহরে নানা হট্টগোল, যার মধ্যে মাথা ঠিক রাখাটা সহজ ছিল না; মাথা যারা ঠিক রেখেছিলেন তাদের অনেককেই দেখা গেছে চর্চা করছেন বাংলা সাহিত্যের। বিচ্যুতির সম্ভাব্য পথ তখন একটি নয়, ছিল দুটি। একটি পুঁজিবাদের অপরটি সামন্তবাদের। ইংরেজরা ছিল পুঁজিবাদের প্রতিনিধি। অন্যদিকে দেশের ভেতর কার্যকর ছিল সামন্তবাদী পিছুটান। একদিকে উগ্র ইয়াং বেঙ্গল, অন্যদিকে সামন্তবাদী বাবুয়ানা; ওই বাবুয়ানাও আবার ইংরেজের সৃষ্ট জমিদারি ব্যবস্থার ওপর পা রেখেই দাঁড়িয়েছিল। মাইকেল মধুসূদন দত্তের সঙ্গে ইয়াঙ বেঙ্গলের মিল ছিল; কিন্তু তিনি ছিলেন অত্যন্ত মেধাবান, তাই সাহেব হওয়ার জন্য ধর্ম ছেড়ে ছিলেন ঠিকই, কিন্তু ভাষা ছাড়তে পারেননি। ইংরেজ ভাষার কবি হবেন ভেবেছিলেন, কিন্তু মেধার স্বাভাবিক তাড়না বাঙালি সাহিত্যিকই হলেন। পয়ারের একঘেয়েমি ও বন্ধনের জায়গায় তিনি নিয়ে এলেন অমিত্রক্ষরের বৈচিত্র্য ও মুক্তি। বাংলা সাহিত্যের প্রথম সার্থক নাটক তিনিই লেখেন; রামের পরিবর্তে রাবণকে নায়ক করলেন তিনি তার মহাকাব্যের, এবং প্রহসন লিখে ব্যঙ্গ করলেন যেমন উচ্ছৃঙ্খল আধুনিকতাকে তেমনি সামন্তবাদী শোষণকে। মহাকাব্য ও নাটকে তিনি পিতৃত্বের পতন দেখিয়েছেন। ওই পতনের কারণ হচ্ছে পিতার ব্যর্থতা। পিতা পারেনি সন্তানকে রক্ষা করতে, পিতা ব্যর্থ হয়েছে জাতীয় স্বাধীনতা রক্ষায়। কিন্তু মধুসূদন আরও একটি কাজ করেছেন, কাব্যের ভাষাকে তিনি সংস্কৃতবহুল করেছেন। বীররসের সৃষ্টি করবেন এই আকাক্সক্ষা ছিল তার, কিন্তু সে-বীরত্ব তার সংস্কৃতিতে ছিল অনুপস্থিত, তাই যা সৃষ্টি করেছেন তা বীররস নয়, করুণ রস।
ওদিকে জাতীয়তাবাদের আর্তহƒদয় ক্রন্দন শুরু করেছিল। সেই ক্রন্দনটি মধুসূদনের কাব্যে যেমন আছে, তেমনি রয়েছে রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এবং নবীন চন্দ্র সেনের মহাকাব্যিক উদ্যোগেও। কিন্তু ওই ক্রন্দন সরাসরি ইংরেজ-বিরোধিতায় পরিণত হবে এমন সম্ভাবনা ছিল না, বরঞ্চ ক্ষেত্রবিশেষে তা মুসলমান-বিরোধিতায় পরিণত হয়েছে।
বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় অনেক দিক দিয়েই অসামান্য। মধুসূদনের মতো তিনিও ইংরেজিতেই লেখা শুরু করেছিলেন, কিন্তু মনীষার অনুপ্রেরণায় অচিরেই চলে এসেছেন বাংলা ভাষার কাছে। আধুনিক বাংলা গদ্য রচনা যদিও রামমোহন রায়ই শুরু করেছিলেন, কিন্তু সে-গদ্য সাহিত্যিক প্রাণবন্ততা পায় ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের হাতে। বঙ্কিমচন্দ্র এই গদ্যকেই আরও বৈচিত্র্যপূর্ণ ও কল্পনাসমৃদ্ধ করে তুলেছেন, তার উপন্যাসের সাহায্যে। মাইকেলের মতো বঙ্কিমচন্দ্রও নায়ক খুঁজেছিলেন, কিন্তু সে নায়কের খোঁজে তিনি পুরাণের কাছে যাননি, গেছেন ইতিহাসের কাছে এবং বিশেষভাবে সমসাময়িক জমিদারদের বাড়িতে। রবীন্দ্রনাথের বাইরে সাহিত্যের ক্ষেত্রে বঙ্কিমচন্দ্রই সবচেয়ে প্রভাবশালী লেখক। তার উপন্যাসে ঘটনাক্রম রোমাঞ্চকর; কিন্তু ঘটনার রোমাঞ্চে নয়, বঙ্কিমচন্দ্রের মূল আগ্রহ ছিল চরিত্র সৃষ্টিতে। বহু স্মরণীয় নায়ক-নায়িকা রেখে গেছেন তিনি আমাদের জন্য। তার নায়িকারা অত্যন্ত জীবন্ত ও তেজস্বিনী; কিন্তু তার নিজের স্বাভাবিক পক্ষপাত নায়কের প্রতিই। এ নায়ককে তিনি কলকাতায় পাননি, কলকাতার মানুষেরা তখনও দ্বিমাত্রিক, গভীরতার তৃতীয় মাত্রা তখনও তারা অর্জন করেনি; বঙ্কিমের নায়কেরা তাই থাকে কলকাতার বাইরে।
মীর মশাররফ হোসেনের রচনাও তাৎপর্যপূর্ণ। দুই কারণে। একটি কারণ, সাহিত্যিক অন্যটি সাংস্কৃতিক। বঙ্কিমচন্দ্র মশাররফের গদ্যরীতির প্রশংসা করেছিলেন সেখানে তথাকথিত মুসলমানিত্বের অভাব দেখে। বোঝা যায়, হিন্দু-মুসলমানের একটি সাহিত্যিক ব্যবধান ততদিনে দাঁড়িয়ে গেছে। ভদ্র-অভদ্র, সাধু-চলিতের পার্থক্যের সঙ্গে এ একটি নতুন মাত্রার যোগ বটে। আপাতদৃষ্টিতে এ ব্যবধানটা শ্রেণীগত নয়, কেননা এটা একটি খাড়াখাড়ি বিভাজন, সম্প্রদায়ের ভিত্তিতে। কিন্তু এর পেছনেও শ্রেণী রয়েছে, রয়েছে মধ্যবিত্ত শ্রেণীরই হিন্দু-মুসলমান দুই অংশের বিরোধ। মশাররফ হোসেন অসাম্প্রদায়িক ছিলেন, কিন্তু তবু তিনি তার সম্প্রদায়ের মানুষ বৈকি, তিনি তার প্রধান রচনা ‘বিষাদ সিন্ধু’র জন্য যে-কাহিনীটি বেছে নিয়েছেন সেটি তার সম্প্রদায়ের মানুষের কাছে খুবই পরিচিত। ‘বিষাদ সিন্ধু’ মোটেই ধর্মগ্রন্থ নয়, যদিও মুসলমান সম্প্রদায়ের অনেকের কাছে এ-গ্রন্থ এক সময়ে প্রায় ধর্মগ্রন্থতুল্য মর্যাদা পেয়েছে। ওই রচনাটি আবার উপন্যাসও নয়, যদিও চরিত্র সৃষ্টিতে মশাররফের দক্ষতা একজন ঔপন্যাসিকের মতোই।
মশাররফ হোসেন অত্যন্ত ইহজাগতিক ছিলেন, যে জন্য ‘বিষাদ সিন্ধু’তে দুর্বৃত্ত এজিদ নৈতিকতার প্রতীক নয়, একজন মানুষ বটে। একাধিক বিবেচনায় মশাররফ অমধ্যবিত্তসুলভ ছিলেন। তার মধ্যে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর আÍসচেতনতা ছিল না, যে জন্য তিনি ওজম্বী হতে ভয় পাননি। তিনি বিষয়মুখী হতে চান, আÍমুখিতা ভুলে। রোমাঞ্চকর ঘটনা পছন্দ করেন এবং তার ওজাস্বিতা কখনও কখনও প্রগলভ হয়ে উঠতে চায়। সর্বোপরি, তিনি ‘জমিদারদর্পণ’ লিখে প্রজার ওপর জমিদারের নিপীড়নের ছবি ফুটিয়ে তুলতে চেয়েছেন। দীনবন্ধু মিত্র ‘নীলদর্পণ’ লিখেছেন, সেই দর্পণে বিদেশী সাহেবদের চেহারা-ছবি ধরা পড়েছে, কিন্তু দেশী জমিদাররদের প্রজাপীড়নের ছবি দীনবন্ধুও দেননি। তাৎপর্যপূর্ণভাবে বঙ্কিমচন্দ্র ‘জমিদারদর্পণে’র ভাষার প্রশংসা করেছেন ঠিকই, কিন্তু বইটির বহুল প্রচার চাননি; পাছে প্রজাবিদ্রোহে ইন্ধন জোগানো হয়। সংস্কৃতিতে ধর্মের চেয়ে শ্রেণী যে অধিক শক্তিশালী বঙ্কিমচন্দ্রের এই দ্বিমুখিতা তারই প্রমাণ বটে। তবে ধর্মের শক্তিও যে কম যায় না তার নিদর্শন অন্যত্র যেমন রয়েছে, তেমনি মশাররফের নিজের ক্ষেত্রেও পাওয়া যায় বৈকি। শেষ বয়সে বঙ্কিমচন্দ্রের মতোই মশাররফও ধর্মের কাছেই চলে গেলেন, একদা তিনি ‘গো-জীবন’ লিখে গো হত্যার বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়েছিলেন, তিনিই শেষ পর্যন্ত লিখেছেন শিল্পসৌন্দর্যে-খর্ব ‘মওলুদ শরীফ’। মশাররফ যে উপন্যাস লিখবেন না সেটা নির্দিষ্ট হয়ে গেছে তার সংস্কৃতির কারণেই। সেখানে নায়ক নেই; তার নিজের শিক্ষাদীক্ষাও মফস্বলের; শহরে গেছেন, কিন্তু গ্রামেই কেটেছে তার কর্মজীবন।
কায়কোবাদও মুসলিম মধ্যবিত্ত শ্রেণীরই সদস্য, তবে মশাররফের তুলনায় অনেক বেশি আÍসচেতন তিনি। কলকাতা থেকে দূরে তার অবস্থান, দীনবন্ধু মিত্র ডাক বিভাগের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা ছিলেন, কায়কোবাদ কাজ নিয়েছিলেন নিজের গ্রামে, পোস্ট মাস্টারের। পার্থক্যটা উপেক্ষার নয় এবং সাহিত্য সৃষ্টিতে তা উপেক্ষিত থাকেনি। সাহিত্যচর্চায় তার আকাক্সক্ষাটি ছিল গভীর। কিন্তু আর্থ-সামাজিক অন্তরায়ের কারণে শিক্ষাগত প্রস্তুতি ও সাংস্কৃতিক মূলধন ছিল সীমিত। তার পক্ষে খণ্ড কবিতা লেখা স্বাভাবিক হতো। কিন্তু অহমিকা বোধের তাড়নাতেই হয়তো বা তিনি লিখতে চেয়েছিলেন মহাকাব্য, যেখানে সাফল্য লাভ হিন্দু মধ্যবিত্তের জন্যই কঠিন ছিল, তার পক্ষে সহজ হবে কি করে? কায়কোবাদ সাম্প্রদায়িক ছিলেন না, অবশ্যই নয়। কিন্তু ঐতিহাসিকভাবে তার মধ্যে মুসলিম স্বাতন্ত্র্যের সেই অনুভবটি কার্যকর ছিল, যা পাকিস্তান দাবির বুদ্ধিবৃত্তিক ধারাটি তৈরি করেছে।
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জগৎটা আলাদা। পারিবারিক অবস্থানে ও পরিচয়ে তিনি জমিদার ঠিকই। কিন্তু আকাক্সক্ষা ও রুচিতে মধ্যবিত্ত, যে-রুচি সমৃদ্ধকরণে তার নিজের ভূমিকা ছিল খুবই গুরুত্বপূর্ণ। মধ্যবিত্তের সেই অংশের প্রতিনিধি তিনি যাদের মেরুদণ্ড বেশ খানিকটা শক্ত। রবীন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ভারতবর্ষের প্রথম তিন জন আইসিএসের একজন। বংশানুক্রমে তারা কলকাতার লোক। জীবিকার জন্য রবীন্দ্রনাথকে চাকরির দরখাস্ত লিখতে হয়নি; ওদিকে জীবনের প্রথম ১২ বছর শিক্ষা যা পেয়েছেন তার সবটাই এসেছে মাতৃভাষার মাধ্যমে এবং প্রায় কিশোর বয়সেই বিলেত গেছেন ব্যারিস্টার হওয়ার জন্য। বিলেত গিয়ে ব্যারিস্টার হয়ে ফেরেননি, ফিরেছেন সঙ্গে করে নিয়ে-যাওয়া লেখক হওয়ার আগ্রহটিকে। আরও প্রাণবন্ত করে।
নায়ক গৌরমোহনের খোঁজে রবীন্দ্রনাথকে কল্পিত ইতিহাসের দ্বারস্থ হতে হয়নি। নায়ককে পাওয়া গেছে কলকাতা শহরেই। এ নায়ক কলকাতার মুৎসুদ্দীর নয়, প্রতিনিধি নয় গড়পরতা শিক্ষিত মধ্যবিত্তের। গৌরমোহনের সঙ্গে বিবেকানন্দের মিল রয়েছে এ যেমন সত্য, তেমনি সত্য এটাও যে, গৌরমোহনের যে-পরিণতি সেটা বিবেকানন্দের ক্ষেত্রে অপ্রত্যাশিত। তবে এটা তো খুবই পরিষ্কার যে, বঙ্কিমচন্দ্র যে জাতীয়তাবাদকে উৎসাহিত করেছেন, রবীন্দ্রনাথ তাকে পরিহাসের বস্তু করে তুলেছেন তার ‘গোরা’ উপন্যাসে। তার সময়ে সমাজে পরিবর্তন এসেছে, রাষ্ট্র সম্পর্কেও বিভিন্ন চিন্তা দানাবেঁধে উঠেছে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ রাষ্ট্রকে অত্যন্ত মূল্যবান প্রতিষ্ঠান বলে মনে করেন না, যদিও রাষ্ট্রের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করেন। তার কাছে সমাজ বড় এবং সমাজকে অগ্রসর করে নিয়ে যাওয়ার জন্য তিনি নেতা চান। কিন্তু সে-নেতা উগ্র, অন্ধ বা বিচ্ছিন্ন নয়, তাকে হতে হবে একজন সামাজিক ব্যক্তিত্ব। রবীন্দ্রনাথ ধর্মে বিশ্বাস করেন, কিন্তু তার সে-ধর্ম ব্যক্তিগত, এবং ধর্মের সঙ্গে রাজনীতিকে মিশিয়ে ফেলার যে-আগ্রহ রাজনীতিক গান্ধীর মধ্যেও ছিল, সাহিত্যিক রবীন্দ্রনাথ তা থেকে নিজেকে দূরে রেখেছিলেন।
রবীন্দ্রনাথের প্রিয় নায়িকা কুমুর সাধ্য কী সমাজকে অস্বীকার করে? সে মুক্তি চায়, কিন্তু পায় না। তাকে গ্রাস করে নিতে চায় উঠতি মুৎসুদ্দী বুর্জোয়া শ্রেণীর স্থূল প্রতিনিধি ‘মহারাজ’ মধুসূদন; কুমুর সামাজিক ও নৈতিক নির্ভরতা তার ভ্রাতা বিপ্রদাসের ওপর। কিন্তু বিপ্রদাসের তো তেমন শক্তি নেই যে ভগ্নি কুমুকে রক্ষা করে। বিপ্রদাসের অর্থনৈতিক নির্ভরশীলতা পৈতৃক জমিদারির ওপর। সেই জমিদারির এখন কোনো তেজ নেই, তাকে অকাল বার্ধক্যে পেয়েছে। বিপ্রদাস ঋণগ্রস্ত, ঋণ করেছে আবার মহাজন মধুসূদনের কাছেই। ওদিকে বিপ্রদাসের আপন ভাই বিলেত গেছে ব্যারিস্টারি পড়বে বলে; সেখানে সে পড়াশোনা কতটা করছে জানা না-গেলেও টাকা যে ওড়াচ্ছে দু’হাতে তাতে কোনো সন্দেহ নেই; যে-অর্থের জোগান বিপ্রদাসকেই দিতে হয়। কুমু তাই বন্দি বাইরে থেকে; আবার ভেতর থেকেও মুক্ত নয় সে, তার রয়েছে নানা সংস্কার ও পিছুটান। কুমু মুক্ত হতে পারে যে সমাজবিন্যাসে তা গড়ে ওঠার আভাস রবীন্দ্রনাথের কালে পাওয়া যায়নি। এখনও যে পাওয়া যাচ্ছে তা নয়। কুমুর বন্দিত্বের তাই কোনো প্রতিকার নেই।
শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ছিলেন পেশাদার ও অত্যন্ত জনপ্রিয় লেখক, কিন্তু তাই বলে তার রচনাতে শিল্পমূল্যের যে কোনো ঘাটতি ছিল তা নয়; তিনি অসামান্য কথাশিল্পী, তার গল্পবলার দক্ষতা ও চরিত্রসৃষ্টির ক্ষমতা প্রায় তুলনাহীন। বাংলা সাহিত্যের তিনি প্রধান ঔপন্যাসিক। তার ভেতর রয়েছে একটি মাতৃহƒদয়। যে-হƒদয় নারীর সমস্যা নিয়ে বিশেষভাবে চিন্তিত। ব্যক্তিকে দেখার ব্যাপারে তার ভেতর কাজ করে বুর্জোয়া কৌতূহল। কিন্তু তিনি আবার জাতীয়তাবাদীও, এ জাতীয়তাবাদ অবশ্য তাকে সামন্তবাদবিরোধী করেনি, বরঞ্চ তার সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধিতার অন্তরে সামন্তবাদের সঙ্গে আপসকামিতাকে বপন করে দিয়েছে। সামন্তবাদ দেশী, তাই সে ভালো, এ ধরনের একটি মনোভাব তার চিন্তায় সংরক্ষিত রয়ে গেছে। শরৎ চন্দ্রের উপন্যাসে জমিদারদের কেউ কেউ প্রজার ওপর অত্যাচার করে, কিন্তু তাই বলে জমিদার মাত্রেই যে খারাপ এমন নয়, তাদের ভেতরও ভালোমন্দ রয়েছে। সামন্তবাদী সংস্কৃতির বিশেষ বৈশিষ্ট্য হচ্ছে ভক্তি, আনুগত্য ও ঐতিহ্যপ্রীতিÑ এদের তিনি জরুরি বলে মনে করেন।
আরও দু’জন বড় মাপের ঔপন্যাসিক নিয়ে এ-বইতে আলোচনা আছে। এদের একজন হলেন বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, অন্যজন মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়। উভয়েরই বিশেষ আগ্রহ গ্রামের জীবনে। বিভূতিভূষণ পশ্চিমবঙ্গের গ্রামকে দেখেছেন, মানিক দেখেছেন পূর্ববঙ্গের গ্রামকে। বিভূতিভূষণের ভেতর একজন কবি আছেন, যে-কবিকে ভাবালু বলতে আগ্রহ জন্মে, কিন্তু যিনি আবার অত্যন্ত বাস্তববাদী, অর্থনীতির প্রকৃত শক্তিটাকে তিনি জানেন এবং চেনেন, দুঃখকে দুঃখ হিসেবেই তিনি উপস্থিত করেন। তার আগ্রহের একটি বিশেষ এলাকা কিশোর-কিশোরীরা। সামান্য বস্তু অসামান্য হয়ে ওঠে তার বাক্যশক্তির স্পর্শ পেয়ে। বিভূতিভূষণের চরিত্ররা দরিদ্র, কিন্তু তারা আবার ব্রাহ্মণ, যে জন্য বিচ্ছিন্ন এবং আÍমর্যাদাজ্ঞানসম্পন্ন। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাসে গরিব মানুষেরা সত্যি সত্যি গরিব, তাদের দুঃখটা অনেকাংশেই ব্যক্তিগত; পদ্মাপাড়ের জেলেদের তিনি যে-ভাবে সাহিত্যে নিয়ে এসেছেন তেমনভাবে তার আগে কেউ আনেননি। তার বাস্তববাদিতা নির্মোহ, ভাবালুতাবিহীন এবং বিশেষভাবে সে-কারণেই অসামান্য।
পূর্ববঙ্গের পল্লীর কথা জসীমউদ্দীনের কবিতাতেও রয়েছে। তিনি বাস্তববাদী। কিন্তু তার জগৎটা স্থির, যে জন্য দেখি তিনি যে নতুন নতুন বিষয়বস্তু খুঁজে নেবেন তেমনটা ঘটছে না। বর্তমানকে তিনি ইতিহাসের পরিপ্রেক্ষিতে স্থাপন করেন না। তার বর্তমানে রাষ্ট্র প্রায় অনুপস্থিত। জসীমউদ্দীনের আবেগটা পদ্মাপাড়ের মানুষের আবেগের মতোই প্রবল, ভাষা একাধারে কবিত্বময় ও ওজস্বী; ওই ওজস্বিতাটাও পূর্ববঙ্গীয়। জসীমউদ্দীনের প্রায় সমসাময়িক হয়েও কাজী নজরুল ইসলাম ও জীবনানন্দ দাশ তার থেকে অনেক দূরে। জীবনানন্দের কবিতাতেও পূর্ববঙ্গ আছে, কিন্তু সে-পূর্ববঙ্গে স্থির হয়েও স্থির নয়, শান্ত নদীটির মতো চলমান। সেখানে আকাশে ছায়া পড়ে, যে-আকাশ খবর রাখে আধুনিককালের। তিনি সমুদ্রের কথা ভাবেন, দ্বীপ তাকে ডাকে, তিনি নাবিককে ভোলেন না। জীবনানন্দের ভেতরও বিষণœতাটা এসেছে, সেটি কেবল যে ব্যক্তিগত তা নয়, সমসাময়িক ইতিহাসেরও। প্রকৃতিপ্রেমিক হয়েও জীবনানন্দ আধুনিক, কেননা তার আছে ইতিহাস-চেতনা ও সংশয়। তার কবিতায় চিত্রকল্পের যে প্রাচুর্য ও গৌরব তেমনটি অন্য কোনো বাঙালি কবির লেখায় আমরা পাই না। নজরুলের কবিতাতেও অবশ্য চিত্রকল্পের কোনো অভাব নেই। তিন উচ্চকণ্ঠ, তার সময়ের কবিদের মতো মধ্যবিত্তসুলভ মৃদুভাষণ তার জীবনে ছিল না, তার সাহিত্যেও নেই। নজরুল প্রকৃতিকে নিয়ে লিখেছেন, কিন্তু তিনি প্রকৃতির কবি নন। চলমান বিশ্বের খবর তার লেখায় রয়েছে, কিন্তু তিনি আবার সংশয়হীনভাবে তার দেশের। শ্রেণীচ্যুতির অসাধারণ ক্ষমতা নজরুলের ছিল। কৌতুকবোধও তার অসামান্য। সর্বোপরি সাহিত্যে তিনি হিন্দু-মুসলিম পুরাণকে একত্র করে দিয়েছিলেন, অন্য কারো পক্ষেই যা করা সম্ভব হয়নি। বাংলা কাব্যে রবীন্দ্রনাথের পরেই তার স্থান; রবীন্দ্রনাথের গানের মতো তার লেখা গানও স্বতন্ত্র, এবং বৈচিত্র্যেও অতুলনীয়।
নজরুল ও জীবনানন্দের জন্ম একই বছরে, দু’জনেই রোমান্টিক। বিশ্বযুদ্ধের পর পুঁজিবাদের পক্ষে আর সম্ভ্রম বা ভদ্রতা কোনোটা রক্ষা করাই সম্ভব হয়নি, সে বেশ উন্মোচিত হয়ে পড়েছে। পুঁজিবাদ রূপ নিয়েছে ফ্যাসিবাদের। নজরুল ও জীবনানন্দের কবিতায় ফ্যাসিবাদের প্রতি ধিক্কার রয়েছে, যে-ধিক্কারটা বৃদ্ধদেব বসুর কবিতায় আমরা পাই না। তাই বলে বুদ্ধদেব যে পুরোপুরি রাজনীতিমুক্ত তা নয়, রাজনীতির ছাপ তার গদ্য রচনায় পাওয়া যাবে বৈকি এবং সে-রাজনীতি অবশ্যই বাম ধারার নয়। তিনি পুরোপুরি শিক্ষিত মধ্যবিত্তের প্রতিনিধি। সাহিত্য-সমালোচনায় তিনি সৃষ্টিশীলতা এনেছেন, এবং সাহিত্যরুচির পরিবর্ধনে তার অবদান সামান্য নয়। বুদ্ধদেবও রোমান্টিক, কিন্তু সে-রোমান্টিকতায় জীবনানন্দের সংশয়, কিংবা নজরুলের উচ্চকণ্ঠ নেই।
মোটকথা মধ্যবিত্তই এ সাহিত্য সৃষ্টি করেছে তার নিজের প্রয়োজনে; এ সাহিত্যের মধ্যে ওই শ্রেণীর অভিজ্ঞতা, আকাক্সক্ষা, পক্ষপাত, প্রবণতা, চিন্তা সবকিছুই স্বাভাবিক ও সুন্দরভাবে প্রতিফলিত হয়েছে এবং বড় একটা সত্য এই যে ওই সাহিত্য দ্বারা, সে নিজেও প্রভাবিত হয়েছে বৈকি।
আলোচনার বিষয় আধুনিক বাংলা সাহিত্য, যে-সাহিত্য শিক্ষিত মধ্যবিত্ত বাঙালি সৃষ্টি করেছে, তার নিজের প্রয়োজনে ও আগ্রহে। ওই শ্রেণীর সঙ্গে এই সাহিত্যের সম্পর্ক তাই অত্যন্ত নিবিড়। মধ্যবিত্তের জীবনে নানা আকাক্সক্ষা থাকে, থাকে স্বপ্ন এবং সেই সঙ্গে সংকট, সাহিত্যে যার প্রতিফলন ঘটেছে। মধ্যবিত্তের সঙ্গে জনগণের দূরত্ব ও নৈকট্য এবং ওই শেণীর ভেতরকার দ্বন্দ্বও এই সাহিত্যে আছে। নর-নারীর সম্পর্ক তো বটেই, হিন্দু-মুসলমান সম্পর্কটিও এক সময়ে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। বাঙালি মধ্যবিত্ত সবচেয়ে অধিক গুরুত্ব দিয়েছে শিক্ষাকে, তার পরে সাহিত্যকে। শিক্ষাকে গুরুত্বপূর্ণ মনে করা সাহিত্যের মর্যাদা বাড়িয়েছে।
আলোচনা শুরু হয়েছে ১৭৭৮-এর একটি ঘটনার উল্লেখ দিয়ে; যেটি হল একজন ইংরেজের হাতে বাংলা ভাষার প্রথম ব্যাকরণ গ্রন্থের রচনা। এ ঘটনা এ কথাটা বলছে যে, দেশের নতুন শাসকেরা বাংলা ভাষা সম্পর্কে জানতে চাচ্ছে এবং বলছে এ কথাও যে, তাদের এ জ্ঞান-অণ্বেষনটা উদ্দেশ্যহীন নয়, উদ্দেশ্য রয়েছে, আর সেটা হল নিজেদের কর্তৃত্বকে আরও বিস্তৃত ও গভীর করা। অস্ত্রের সাহায্যে তো শাসন করবেই, ঠিক করেছে অধীনদের আরও অধীন করার জন্য জ্ঞানেরও দরকার পড়বে। ওই বিদেশী শাসনের নানা ধরনের প্রভাব আমরা বাংলা সাহিত্যে প্রত্যক্ষ করি। প্রভাব বিশেষ রূপে কার্যকর হয়েছে ইংরেজি-শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মধ্য দিয়েই। এই মধ্যবিত্ত শ্রেণীই আধুনিক বাংলা সাহিত্যের একাধারে স্রষ্টা ও পাঠক, এবং শ্রেণীটি নিজে যে গড়ে উঠেছে তাও ইংরেজদের আনুকূল্য লাভের ভেতর দিয়েই। শাসক ইংরেজ যে বাংলা ভাষার ব্যাকরণ তৈরি করে দিয়েছে এটা ঠিক নয়, তবে আধুনিক বাংলা সাহিত্যের সামাজিক ব্যাকরণ তৈরিকে তারা যে প্রভাবিত করেছে তাতে কোনো সন্দেহ নেই।
সামাজিক ওই ব্যাকরণের একটি উপাদান হচ্ছে জাতীয়তাবাদ। বাঙালির জন্য পরাধীনতা নতুন অভিজ্ঞতা নয়, কিন্তু ইংরেজ শাসনামলে পরাধীনতার ফলে যে জাতীয়তাবাদী স্পৃহা জেগেছিল তেমনটি আগে কখনও ঘটেনি। অন্য বিজেতারা এখানে এসে স্থায়ীভাবে রয়ে গেছে, কিন্তু ইংরেজরা যে বসবাসের জন্য আসেনি, বাণিজ্যের জন্যই এসেছে এটা ছিল স্পষ্ট। বাণিজ্যের স্বার্থে তারা সাম্রাজ্য গড়েছে। কেবল সৈন্য দিয়ে শাসন করেনি, ভাষা দিয়েও ওই কাজ করেছে। বাঙালি মধ্যবিত্ত ইংরেজদের আনুকূল্য পেয়েছে আবার তার হাতে অপমানিতও হয়েছে; সে বুঝে নিয়েছে যে ইংরেজরা এখানে বসতি স্থাপন করেব না ঠিকই, কিন্তু আবার চলেও যে যাবে তাও নয়; তাছাড়া চলে যাক এটা যে মধ্যবিত্তরা শ্রেণীগতভাবে চেয়েছে এমনও নয়, তাদের স্বার্থ ইংরেজ শাসনকে সমর্থন করেছে। কাজেই ইংরেজ-বিরোধিতা আর ইংরেজ-সমর্থন পরস্পরবিরোধী এ দুই কাজ একসঙ্গেই চলেছে।
স্বাধীনতার জন্য জাতীয়তাবাদী সংগ্রামের আবশ্যকতার বোধটা ইংরেজ বিরোধিতারই ফলশ্র“তি। বাংলা ভাষা চর্চার মধ্যে জাতীয়তাবাদী অনুপ্রেরণা ছিল বৈকি, যারা ওই অনুপ্রেরণাটা বোধ করেনি তারা তাঁবেদারিকে স্বাধীনতা বলে গণ্য করেছে। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনক ঘটনা হল এই যে, সাহিত্যের ক্ষেত্রে ওই জাতীয়তাবাদ ইংরেজকে শত্র“ বলে সরাসরি চিহ্নিত করেনি ভয়ে। ভয় ছিল স্বার্থহানির; ভয় ছিল ইংরেজদের কোপানলে পতনের। ভীত জাতীয়তাবাদের ভুল ধারাটাকে দেখা গেল সামনে না এগিয়ে পিছু হটে গিয়ে আশ্রয় নিচ্ছে ধর্মের কাছে, পরিণত হচ্ছে ধর্মীয় পুনর্জাগরণবাদে। ওই পুনর্জাগরণবাদের পক্ষে অস্বাভাবিক হয়নি সাম্প্রদায়িকতাকে পুষ্ট করা। সাম্প্রদায়িকতার সৃষ্টিতে ইংরেজের সুবিধাবাদী উস্কানি যে ছিল তাতে সন্দেহ নেই, কিন্তু তার মূলটা যে ছিল অর্থনৈতিক, তা অনস্বীকার্য। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে হিন্দু মধ্যবিত্ত এগিয়ে ছিল, মুসলমান মধ্যবিত্ত কিছুটা বিলম্বে এসেছে, এসে পেশা ও রাজনীতিতে নিজের জন্য জায়গা চেয়েছে। জায়গা নিয়ে এই বিরোধটাই হচ্ছে সাম্প্রদায়িকতার মূল উৎস। ধর্ম কাজ করেছে পরিচয়ের চিহ্ন ও উত্তেজক সহকারী হিসেবে।
ভাষা সবসময়ই ইহজাগতিক, সাহিত্যেরও হওয়ার কথা সেরকমই, কিন্তু আধুনিক বাংলা সাহিত্যে ধর্ম প্রবেশ করেছে, এমনকি কার্যকরও থেকেছে, আর ভাষাও যে সাম্প্রদায়িকতার প্রভাব এড়াতে পেরেছে তা নয়।
জাতীয়তাবাদ অত্যন্ত স্পর্শকাতররূপে শত্র“সচেতন। শত্র“র উপস্থিতি না থাকলে সে জোর পায় না, এগোতে পারে না। হিন্দু মধ্যবিত্ত নিজেকে কেবল বাঙালি ভাবেনি, হিন্দুও ভেবেছে এবং এজন্যই অনেক সময় ইংরেজের চেয়েও মুসলমানকে সে বড় শত্র“ হিসেবে দেখেছে। আÍপরিচয়ের প্রশ্নেও ওই মধ্যবিত্তকে ধর্মের কাছে যেতে হচ্ছিল, বিধর্মী ইংরেজের বিপরীতে দাঁড়িয়ে সে যে তার ধর্মীয় পরিচয়কেই উচ্চে তুলে ধরবে এতে কোনো অস্বাভাবিকতা ছিল না। ধর্ম পুরাতন বন্ধু, নির্ভরযোগ্য আশ্রয়দাতা; তার কাছে গিয়ে নিরাপদে ইংরেজ-বিরোধিতাও সম্ভবপর, কেননা বিরোধিতাটা তখন আর রাজনৈতিক থাকবে না, রূপ নেবে ধর্মীয় এবং ধর্মের ব্যাপারে ইংরেজের তেমন কোনো মাথাব্যথা ছিল না, সে এসেছে ব্যবসা-বাণিজ্য করতে, ধর্ম নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করাটা তার ব্যবসার জন্য উপকারী নয়, বরঞ্চ ক্ষতিকর।
মধ্যবিত্তের এ ধর্মাশ্রয়িতা বাঙালির জন্য রাজনৈতিকভাবে অত্যন্ত ক্ষতিকর হয়েছে, কেননা তা সাম্রাজ্যবাদকে পুষ্ট করেছে এবং শেষ পর্যন্ত দেশকে দুই রাষ্ট্রে ভাগ করে ছেড়েছে। ধর্মাশ্রয়িতা সাহিত্যের জন্যও ইতিবাচক ফল বহন করে আনেনি। কেননা সাহিত্যচর্চার ক্ষেত্রে সে পৃষ্ঠপোষকতা দিয়েছে ভাববাদককে এবং সমর্থন করেছে সাম্প্রদায়িকতাকে।
সাহিত্যের সামাজিক ব্যাকরণে এ সত্য ও উল্লেখযোগ্য নিয়ামক যে, বাঙালি মধ্যবিত্ত সাহিত্যচর্চাকে অত্যন্ত উচ্চমূল্য দিয়ে এসেছে। এর একটা সহজ কারণ এই যে, আÍপ্রকাশের অন্য মাধ্যমগুলো তার পক্ষে আয়ত্ত করা সহজ হয়নি। স্থাপত্য ও ভাস্কর্যের উপকরণ এদেশে সীমিত। চিত্রকলাকে রক্ষা করা কঠিন। নৃত্যের ব্যাপারে সামাজিক ও ধর্মীয় বিধিনিষেধ ছিল। তুলনায় বই লেখা সহজ এবং বাঙালি তা লিখলেও। তাছাড়া সাহিত্য তার জন্য কেবল যে আÍপ্রকাশের মাধ্যম ছিল তা নয়, ছিল চিত্তবিনোদনের সুস্থ উপায় এবং ছিল অন্য বাঙালির এবং বহির্বিশ্বের সঙ্গে যোগাযোগের ক্ষেত্র। নিজের চারপাশে যা দেখেছে এবং বাইরের বিশ্ব থেকে যা সংগ্রহ করেছে তা সে ব্যবহার করেছে সাহিত্য রচনায়।
বাঙালির আÍপরিচয়ের ক্ষেত্রে একটা সমস্যা ছিল উত্তর ভারতের সঙ্গে তার সম্পর্ক। উত্তর ভারত বাঙালিকে হিন্দু কিংবা মুসলমান হতে সাহায্য করেছে, বাঙালি হতে পরামর্শ দেয়নি। অথচ ভাষা বাঙালিকে জানিয়ে দিয়েছে যে, বাঙালিরা উত্তর ভারতের সম্প্রসারণ নয়, তারা স্বতন্ত্র। স্বাতন্ত্র্যের এ বোধকে লালন করা বাঙালির জন্য স্বাভাবিক ছিল, আধুনিক বাংলা সাহিত্যে ওই লালন-পালনটা রয়েছেও, কিন্তু সর্বভারতীয় উৎপাতটা যে এখানে-সেখানে দেখা যায়নি তা নয়। বলা বাহুল্য, সর্বভারতীয়তার এই বোধটাও ইংরেজি শাসনেরই ফল, তার আগে ভারতবর্ষে বহু অঞ্চল ছিল, অখণ্ড ভারত বলে কিছু ছিল না।
ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির অনেক দানের মধ্যে একটি হল কলকাতা শহর। ছোটখাটো লন্ডন একটি; প্রবাসে স্বদেশবাসের আয়োজনÑ ইংরেজের জন্য। মধ্যবিত্ত বাঙালির পক্ষে সেখানে সুযোগ সন্ধান খুবই সম্ভবপর। ওই শহরে নানা হট্টগোল, যার মধ্যে মাথা ঠিক রাখাটা সহজ ছিল না; মাথা যারা ঠিক রেখেছিলেন তাদের অনেককেই দেখা গেছে চর্চা করছেন বাংলা সাহিত্যের। বিচ্যুতির সম্ভাব্য পথ তখন একটি নয়, ছিল দুটি। একটি পুঁজিবাদের অপরটি সামন্তবাদের। ইংরেজরা ছিল পুঁজিবাদের প্রতিনিধি। অন্যদিকে দেশের ভেতর কার্যকর ছিল সামন্তবাদী পিছুটান। একদিকে উগ্র ইয়াং বেঙ্গল, অন্যদিকে সামন্তবাদী বাবুয়ানা; ওই বাবুয়ানাও আবার ইংরেজের সৃষ্ট জমিদারি ব্যবস্থার ওপর পা রেখেই দাঁড়িয়েছিল। মাইকেল মধুসূদন দত্তের সঙ্গে ইয়াঙ বেঙ্গলের মিল ছিল; কিন্তু তিনি ছিলেন অত্যন্ত মেধাবান, তাই সাহেব হওয়ার জন্য ধর্ম ছেড়ে ছিলেন ঠিকই, কিন্তু ভাষা ছাড়তে পারেননি। ইংরেজ ভাষার কবি হবেন ভেবেছিলেন, কিন্তু মেধার স্বাভাবিক তাড়না বাঙালি সাহিত্যিকই হলেন। পয়ারের একঘেয়েমি ও বন্ধনের জায়গায় তিনি নিয়ে এলেন অমিত্রক্ষরের বৈচিত্র্য ও মুক্তি। বাংলা সাহিত্যের প্রথম সার্থক নাটক তিনিই লেখেন; রামের পরিবর্তে রাবণকে নায়ক করলেন তিনি তার মহাকাব্যের, এবং প্রহসন লিখে ব্যঙ্গ করলেন যেমন উচ্ছৃঙ্খল আধুনিকতাকে তেমনি সামন্তবাদী শোষণকে। মহাকাব্য ও নাটকে তিনি পিতৃত্বের পতন দেখিয়েছেন। ওই পতনের কারণ হচ্ছে পিতার ব্যর্থতা। পিতা পারেনি সন্তানকে রক্ষা করতে, পিতা ব্যর্থ হয়েছে জাতীয় স্বাধীনতা রক্ষায়। কিন্তু মধুসূদন আরও একটি কাজ করেছেন, কাব্যের ভাষাকে তিনি সংস্কৃতবহুল করেছেন। বীররসের সৃষ্টি করবেন এই আকাক্সক্ষা ছিল তার, কিন্তু সে-বীরত্ব তার সংস্কৃতিতে ছিল অনুপস্থিত, তাই যা সৃষ্টি করেছেন তা বীররস নয়, করুণ রস।
ওদিকে জাতীয়তাবাদের আর্তহƒদয় ক্রন্দন শুরু করেছিল। সেই ক্রন্দনটি মধুসূদনের কাব্যে যেমন আছে, তেমনি রয়েছে রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এবং নবীন চন্দ্র সেনের মহাকাব্যিক উদ্যোগেও। কিন্তু ওই ক্রন্দন সরাসরি ইংরেজ-বিরোধিতায় পরিণত হবে এমন সম্ভাবনা ছিল না, বরঞ্চ ক্ষেত্রবিশেষে তা মুসলমান-বিরোধিতায় পরিণত হয়েছে।
বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় অনেক দিক দিয়েই অসামান্য। মধুসূদনের মতো তিনিও ইংরেজিতেই লেখা শুরু করেছিলেন, কিন্তু মনীষার অনুপ্রেরণায় অচিরেই চলে এসেছেন বাংলা ভাষার কাছে। আধুনিক বাংলা গদ্য রচনা যদিও রামমোহন রায়ই শুরু করেছিলেন, কিন্তু সে-গদ্য সাহিত্যিক প্রাণবন্ততা পায় ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের হাতে। বঙ্কিমচন্দ্র এই গদ্যকেই আরও বৈচিত্র্যপূর্ণ ও কল্পনাসমৃদ্ধ করে তুলেছেন, তার উপন্যাসের সাহায্যে। মাইকেলের মতো বঙ্কিমচন্দ্রও নায়ক খুঁজেছিলেন, কিন্তু সে নায়কের খোঁজে তিনি পুরাণের কাছে যাননি, গেছেন ইতিহাসের কাছে এবং বিশেষভাবে সমসাময়িক জমিদারদের বাড়িতে। রবীন্দ্রনাথের বাইরে সাহিত্যের ক্ষেত্রে বঙ্কিমচন্দ্রই সবচেয়ে প্রভাবশালী লেখক। তার উপন্যাসে ঘটনাক্রম রোমাঞ্চকর; কিন্তু ঘটনার রোমাঞ্চে নয়, বঙ্কিমচন্দ্রের মূল আগ্রহ ছিল চরিত্র সৃষ্টিতে। বহু স্মরণীয় নায়ক-নায়িকা রেখে গেছেন তিনি আমাদের জন্য। তার নায়িকারা অত্যন্ত জীবন্ত ও তেজস্বিনী; কিন্তু তার নিজের স্বাভাবিক পক্ষপাত নায়কের প্রতিই। এ নায়ককে তিনি কলকাতায় পাননি, কলকাতার মানুষেরা তখনও দ্বিমাত্রিক, গভীরতার তৃতীয় মাত্রা তখনও তারা অর্জন করেনি; বঙ্কিমের নায়কেরা তাই থাকে কলকাতার বাইরে।
মীর মশাররফ হোসেনের রচনাও তাৎপর্যপূর্ণ। দুই কারণে। একটি কারণ, সাহিত্যিক অন্যটি সাংস্কৃতিক। বঙ্কিমচন্দ্র মশাররফের গদ্যরীতির প্রশংসা করেছিলেন সেখানে তথাকথিত মুসলমানিত্বের অভাব দেখে। বোঝা যায়, হিন্দু-মুসলমানের একটি সাহিত্যিক ব্যবধান ততদিনে দাঁড়িয়ে গেছে। ভদ্র-অভদ্র, সাধু-চলিতের পার্থক্যের সঙ্গে এ একটি নতুন মাত্রার যোগ বটে। আপাতদৃষ্টিতে এ ব্যবধানটা শ্রেণীগত নয়, কেননা এটা একটি খাড়াখাড়ি বিভাজন, সম্প্রদায়ের ভিত্তিতে। কিন্তু এর পেছনেও শ্রেণী রয়েছে, রয়েছে মধ্যবিত্ত শ্রেণীরই হিন্দু-মুসলমান দুই অংশের বিরোধ। মশাররফ হোসেন অসাম্প্রদায়িক ছিলেন, কিন্তু তবু তিনি তার সম্প্রদায়ের মানুষ বৈকি, তিনি তার প্রধান রচনা ‘বিষাদ সিন্ধু’র জন্য যে-কাহিনীটি বেছে নিয়েছেন সেটি তার সম্প্রদায়ের মানুষের কাছে খুবই পরিচিত। ‘বিষাদ সিন্ধু’ মোটেই ধর্মগ্রন্থ নয়, যদিও মুসলমান সম্প্রদায়ের অনেকের কাছে এ-গ্রন্থ এক সময়ে প্রায় ধর্মগ্রন্থতুল্য মর্যাদা পেয়েছে। ওই রচনাটি আবার উপন্যাসও নয়, যদিও চরিত্র সৃষ্টিতে মশাররফের দক্ষতা একজন ঔপন্যাসিকের মতোই।
মশাররফ হোসেন অত্যন্ত ইহজাগতিক ছিলেন, যে জন্য ‘বিষাদ সিন্ধু’তে দুর্বৃত্ত এজিদ নৈতিকতার প্রতীক নয়, একজন মানুষ বটে। একাধিক বিবেচনায় মশাররফ অমধ্যবিত্তসুলভ ছিলেন। তার মধ্যে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর আÍসচেতনতা ছিল না, যে জন্য তিনি ওজম্বী হতে ভয় পাননি। তিনি বিষয়মুখী হতে চান, আÍমুখিতা ভুলে। রোমাঞ্চকর ঘটনা পছন্দ করেন এবং তার ওজাস্বিতা কখনও কখনও প্রগলভ হয়ে উঠতে চায়। সর্বোপরি, তিনি ‘জমিদারদর্পণ’ লিখে প্রজার ওপর জমিদারের নিপীড়নের ছবি ফুটিয়ে তুলতে চেয়েছেন। দীনবন্ধু মিত্র ‘নীলদর্পণ’ লিখেছেন, সেই দর্পণে বিদেশী সাহেবদের চেহারা-ছবি ধরা পড়েছে, কিন্তু দেশী জমিদাররদের প্রজাপীড়নের ছবি দীনবন্ধুও দেননি। তাৎপর্যপূর্ণভাবে বঙ্কিমচন্দ্র ‘জমিদারদর্পণে’র ভাষার প্রশংসা করেছেন ঠিকই, কিন্তু বইটির বহুল প্রচার চাননি; পাছে প্রজাবিদ্রোহে ইন্ধন জোগানো হয়। সংস্কৃতিতে ধর্মের চেয়ে শ্রেণী যে অধিক শক্তিশালী বঙ্কিমচন্দ্রের এই দ্বিমুখিতা তারই প্রমাণ বটে। তবে ধর্মের শক্তিও যে কম যায় না তার নিদর্শন অন্যত্র যেমন রয়েছে, তেমনি মশাররফের নিজের ক্ষেত্রেও পাওয়া যায় বৈকি। শেষ বয়সে বঙ্কিমচন্দ্রের মতোই মশাররফও ধর্মের কাছেই চলে গেলেন, একদা তিনি ‘গো-জীবন’ লিখে গো হত্যার বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়েছিলেন, তিনিই শেষ পর্যন্ত লিখেছেন শিল্পসৌন্দর্যে-খর্ব ‘মওলুদ শরীফ’। মশাররফ যে উপন্যাস লিখবেন না সেটা নির্দিষ্ট হয়ে গেছে তার সংস্কৃতির কারণেই। সেখানে নায়ক নেই; তার নিজের শিক্ষাদীক্ষাও মফস্বলের; শহরে গেছেন, কিন্তু গ্রামেই কেটেছে তার কর্মজীবন।
কায়কোবাদও মুসলিম মধ্যবিত্ত শ্রেণীরই সদস্য, তবে মশাররফের তুলনায় অনেক বেশি আÍসচেতন তিনি। কলকাতা থেকে দূরে তার অবস্থান, দীনবন্ধু মিত্র ডাক বিভাগের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা ছিলেন, কায়কোবাদ কাজ নিয়েছিলেন নিজের গ্রামে, পোস্ট মাস্টারের। পার্থক্যটা উপেক্ষার নয় এবং সাহিত্য সৃষ্টিতে তা উপেক্ষিত থাকেনি। সাহিত্যচর্চায় তার আকাক্সক্ষাটি ছিল গভীর। কিন্তু আর্থ-সামাজিক অন্তরায়ের কারণে শিক্ষাগত প্রস্তুতি ও সাংস্কৃতিক মূলধন ছিল সীমিত। তার পক্ষে খণ্ড কবিতা লেখা স্বাভাবিক হতো। কিন্তু অহমিকা বোধের তাড়নাতেই হয়তো বা তিনি লিখতে চেয়েছিলেন মহাকাব্য, যেখানে সাফল্য লাভ হিন্দু মধ্যবিত্তের জন্যই কঠিন ছিল, তার পক্ষে সহজ হবে কি করে? কায়কোবাদ সাম্প্রদায়িক ছিলেন না, অবশ্যই নয়। কিন্তু ঐতিহাসিকভাবে তার মধ্যে মুসলিম স্বাতন্ত্র্যের সেই অনুভবটি কার্যকর ছিল, যা পাকিস্তান দাবির বুদ্ধিবৃত্তিক ধারাটি তৈরি করেছে।
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জগৎটা আলাদা। পারিবারিক অবস্থানে ও পরিচয়ে তিনি জমিদার ঠিকই। কিন্তু আকাক্সক্ষা ও রুচিতে মধ্যবিত্ত, যে-রুচি সমৃদ্ধকরণে তার নিজের ভূমিকা ছিল খুবই গুরুত্বপূর্ণ। মধ্যবিত্তের সেই অংশের প্রতিনিধি তিনি যাদের মেরুদণ্ড বেশ খানিকটা শক্ত। রবীন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ভারতবর্ষের প্রথম তিন জন আইসিএসের একজন। বংশানুক্রমে তারা কলকাতার লোক। জীবিকার জন্য রবীন্দ্রনাথকে চাকরির দরখাস্ত লিখতে হয়নি; ওদিকে জীবনের প্রথম ১২ বছর শিক্ষা যা পেয়েছেন তার সবটাই এসেছে মাতৃভাষার মাধ্যমে এবং প্রায় কিশোর বয়সেই বিলেত গেছেন ব্যারিস্টার হওয়ার জন্য। বিলেত গিয়ে ব্যারিস্টার হয়ে ফেরেননি, ফিরেছেন সঙ্গে করে নিয়ে-যাওয়া লেখক হওয়ার আগ্রহটিকে। আরও প্রাণবন্ত করে।
নায়ক গৌরমোহনের খোঁজে রবীন্দ্রনাথকে কল্পিত ইতিহাসের দ্বারস্থ হতে হয়নি। নায়ককে পাওয়া গেছে কলকাতা শহরেই। এ নায়ক কলকাতার মুৎসুদ্দীর নয়, প্রতিনিধি নয় গড়পরতা শিক্ষিত মধ্যবিত্তের। গৌরমোহনের সঙ্গে বিবেকানন্দের মিল রয়েছে এ যেমন সত্য, তেমনি সত্য এটাও যে, গৌরমোহনের যে-পরিণতি সেটা বিবেকানন্দের ক্ষেত্রে অপ্রত্যাশিত। তবে এটা তো খুবই পরিষ্কার যে, বঙ্কিমচন্দ্র যে জাতীয়তাবাদকে উৎসাহিত করেছেন, রবীন্দ্রনাথ তাকে পরিহাসের বস্তু করে তুলেছেন তার ‘গোরা’ উপন্যাসে। তার সময়ে সমাজে পরিবর্তন এসেছে, রাষ্ট্র সম্পর্কেও বিভিন্ন চিন্তা দানাবেঁধে উঠেছে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ রাষ্ট্রকে অত্যন্ত মূল্যবান প্রতিষ্ঠান বলে মনে করেন না, যদিও রাষ্ট্রের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করেন। তার কাছে সমাজ বড় এবং সমাজকে অগ্রসর করে নিয়ে যাওয়ার জন্য তিনি নেতা চান। কিন্তু সে-নেতা উগ্র, অন্ধ বা বিচ্ছিন্ন নয়, তাকে হতে হবে একজন সামাজিক ব্যক্তিত্ব। রবীন্দ্রনাথ ধর্মে বিশ্বাস করেন, কিন্তু তার সে-ধর্ম ব্যক্তিগত, এবং ধর্মের সঙ্গে রাজনীতিকে মিশিয়ে ফেলার যে-আগ্রহ রাজনীতিক গান্ধীর মধ্যেও ছিল, সাহিত্যিক রবীন্দ্রনাথ তা থেকে নিজেকে দূরে রেখেছিলেন।
রবীন্দ্রনাথের প্রিয় নায়িকা কুমুর সাধ্য কী সমাজকে অস্বীকার করে? সে মুক্তি চায়, কিন্তু পায় না। তাকে গ্রাস করে নিতে চায় উঠতি মুৎসুদ্দী বুর্জোয়া শ্রেণীর স্থূল প্রতিনিধি ‘মহারাজ’ মধুসূদন; কুমুর সামাজিক ও নৈতিক নির্ভরতা তার ভ্রাতা বিপ্রদাসের ওপর। কিন্তু বিপ্রদাসের তো তেমন শক্তি নেই যে ভগ্নি কুমুকে রক্ষা করে। বিপ্রদাসের অর্থনৈতিক নির্ভরশীলতা পৈতৃক জমিদারির ওপর। সেই জমিদারির এখন কোনো তেজ নেই, তাকে অকাল বার্ধক্যে পেয়েছে। বিপ্রদাস ঋণগ্রস্ত, ঋণ করেছে আবার মহাজন মধুসূদনের কাছেই। ওদিকে বিপ্রদাসের আপন ভাই বিলেত গেছে ব্যারিস্টারি পড়বে বলে; সেখানে সে পড়াশোনা কতটা করছে জানা না-গেলেও টাকা যে ওড়াচ্ছে দু’হাতে তাতে কোনো সন্দেহ নেই; যে-অর্থের জোগান বিপ্রদাসকেই দিতে হয়। কুমু তাই বন্দি বাইরে থেকে; আবার ভেতর থেকেও মুক্ত নয় সে, তার রয়েছে নানা সংস্কার ও পিছুটান। কুমু মুক্ত হতে পারে যে সমাজবিন্যাসে তা গড়ে ওঠার আভাস রবীন্দ্রনাথের কালে পাওয়া যায়নি। এখনও যে পাওয়া যাচ্ছে তা নয়। কুমুর বন্দিত্বের তাই কোনো প্রতিকার নেই।
শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ছিলেন পেশাদার ও অত্যন্ত জনপ্রিয় লেখক, কিন্তু তাই বলে তার রচনাতে শিল্পমূল্যের যে কোনো ঘাটতি ছিল তা নয়; তিনি অসামান্য কথাশিল্পী, তার গল্পবলার দক্ষতা ও চরিত্রসৃষ্টির ক্ষমতা প্রায় তুলনাহীন। বাংলা সাহিত্যের তিনি প্রধান ঔপন্যাসিক। তার ভেতর রয়েছে একটি মাতৃহƒদয়। যে-হƒদয় নারীর সমস্যা নিয়ে বিশেষভাবে চিন্তিত। ব্যক্তিকে দেখার ব্যাপারে তার ভেতর কাজ করে বুর্জোয়া কৌতূহল। কিন্তু তিনি আবার জাতীয়তাবাদীও, এ জাতীয়তাবাদ অবশ্য তাকে সামন্তবাদবিরোধী করেনি, বরঞ্চ তার সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধিতার অন্তরে সামন্তবাদের সঙ্গে আপসকামিতাকে বপন করে দিয়েছে। সামন্তবাদ দেশী, তাই সে ভালো, এ ধরনের একটি মনোভাব তার চিন্তায় সংরক্ষিত রয়ে গেছে। শরৎ চন্দ্রের উপন্যাসে জমিদারদের কেউ কেউ প্রজার ওপর অত্যাচার করে, কিন্তু তাই বলে জমিদার মাত্রেই যে খারাপ এমন নয়, তাদের ভেতরও ভালোমন্দ রয়েছে। সামন্তবাদী সংস্কৃতির বিশেষ বৈশিষ্ট্য হচ্ছে ভক্তি, আনুগত্য ও ঐতিহ্যপ্রীতিÑ এদের তিনি জরুরি বলে মনে করেন।
আরও দু’জন বড় মাপের ঔপন্যাসিক নিয়ে এ-বইতে আলোচনা আছে। এদের একজন হলেন বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, অন্যজন মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়। উভয়েরই বিশেষ আগ্রহ গ্রামের জীবনে। বিভূতিভূষণ পশ্চিমবঙ্গের গ্রামকে দেখেছেন, মানিক দেখেছেন পূর্ববঙ্গের গ্রামকে। বিভূতিভূষণের ভেতর একজন কবি আছেন, যে-কবিকে ভাবালু বলতে আগ্রহ জন্মে, কিন্তু যিনি আবার অত্যন্ত বাস্তববাদী, অর্থনীতির প্রকৃত শক্তিটাকে তিনি জানেন এবং চেনেন, দুঃখকে দুঃখ হিসেবেই তিনি উপস্থিত করেন। তার আগ্রহের একটি বিশেষ এলাকা কিশোর-কিশোরীরা। সামান্য বস্তু অসামান্য হয়ে ওঠে তার বাক্যশক্তির স্পর্শ পেয়ে। বিভূতিভূষণের চরিত্ররা দরিদ্র, কিন্তু তারা আবার ব্রাহ্মণ, যে জন্য বিচ্ছিন্ন এবং আÍমর্যাদাজ্ঞানসম্পন্ন। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাসে গরিব মানুষেরা সত্যি সত্যি গরিব, তাদের দুঃখটা অনেকাংশেই ব্যক্তিগত; পদ্মাপাড়ের জেলেদের তিনি যে-ভাবে সাহিত্যে নিয়ে এসেছেন তেমনভাবে তার আগে কেউ আনেননি। তার বাস্তববাদিতা নির্মোহ, ভাবালুতাবিহীন এবং বিশেষভাবে সে-কারণেই অসামান্য।
পূর্ববঙ্গের পল্লীর কথা জসীমউদ্দীনের কবিতাতেও রয়েছে। তিনি বাস্তববাদী। কিন্তু তার জগৎটা স্থির, যে জন্য দেখি তিনি যে নতুন নতুন বিষয়বস্তু খুঁজে নেবেন তেমনটা ঘটছে না। বর্তমানকে তিনি ইতিহাসের পরিপ্রেক্ষিতে স্থাপন করেন না। তার বর্তমানে রাষ্ট্র প্রায় অনুপস্থিত। জসীমউদ্দীনের আবেগটা পদ্মাপাড়ের মানুষের আবেগের মতোই প্রবল, ভাষা একাধারে কবিত্বময় ও ওজস্বী; ওই ওজস্বিতাটাও পূর্ববঙ্গীয়। জসীমউদ্দীনের প্রায় সমসাময়িক হয়েও কাজী নজরুল ইসলাম ও জীবনানন্দ দাশ তার থেকে অনেক দূরে। জীবনানন্দের কবিতাতেও পূর্ববঙ্গ আছে, কিন্তু সে-পূর্ববঙ্গে স্থির হয়েও স্থির নয়, শান্ত নদীটির মতো চলমান। সেখানে আকাশে ছায়া পড়ে, যে-আকাশ খবর রাখে আধুনিককালের। তিনি সমুদ্রের কথা ভাবেন, দ্বীপ তাকে ডাকে, তিনি নাবিককে ভোলেন না। জীবনানন্দের ভেতরও বিষণœতাটা এসেছে, সেটি কেবল যে ব্যক্তিগত তা নয়, সমসাময়িক ইতিহাসেরও। প্রকৃতিপ্রেমিক হয়েও জীবনানন্দ আধুনিক, কেননা তার আছে ইতিহাস-চেতনা ও সংশয়। তার কবিতায় চিত্রকল্পের যে প্রাচুর্য ও গৌরব তেমনটি অন্য কোনো বাঙালি কবির লেখায় আমরা পাই না। নজরুলের কবিতাতেও অবশ্য চিত্রকল্পের কোনো অভাব নেই। তিন উচ্চকণ্ঠ, তার সময়ের কবিদের মতো মধ্যবিত্তসুলভ মৃদুভাষণ তার জীবনে ছিল না, তার সাহিত্যেও নেই। নজরুল প্রকৃতিকে নিয়ে লিখেছেন, কিন্তু তিনি প্রকৃতির কবি নন। চলমান বিশ্বের খবর তার লেখায় রয়েছে, কিন্তু তিনি আবার সংশয়হীনভাবে তার দেশের। শ্রেণীচ্যুতির অসাধারণ ক্ষমতা নজরুলের ছিল। কৌতুকবোধও তার অসামান্য। সর্বোপরি সাহিত্যে তিনি হিন্দু-মুসলিম পুরাণকে একত্র করে দিয়েছিলেন, অন্য কারো পক্ষেই যা করা সম্ভব হয়নি। বাংলা কাব্যে রবীন্দ্রনাথের পরেই তার স্থান; রবীন্দ্রনাথের গানের মতো তার লেখা গানও স্বতন্ত্র, এবং বৈচিত্র্যেও অতুলনীয়।
নজরুল ও জীবনানন্দের জন্ম একই বছরে, দু’জনেই রোমান্টিক। বিশ্বযুদ্ধের পর পুঁজিবাদের পক্ষে আর সম্ভ্রম বা ভদ্রতা কোনোটা রক্ষা করাই সম্ভব হয়নি, সে বেশ উন্মোচিত হয়ে পড়েছে। পুঁজিবাদ রূপ নিয়েছে ফ্যাসিবাদের। নজরুল ও জীবনানন্দের কবিতায় ফ্যাসিবাদের প্রতি ধিক্কার রয়েছে, যে-ধিক্কারটা বৃদ্ধদেব বসুর কবিতায় আমরা পাই না। তাই বলে বুদ্ধদেব যে পুরোপুরি রাজনীতিমুক্ত তা নয়, রাজনীতির ছাপ তার গদ্য রচনায় পাওয়া যাবে বৈকি এবং সে-রাজনীতি অবশ্যই বাম ধারার নয়। তিনি পুরোপুরি শিক্ষিত মধ্যবিত্তের প্রতিনিধি। সাহিত্য-সমালোচনায় তিনি সৃষ্টিশীলতা এনেছেন, এবং সাহিত্যরুচির পরিবর্ধনে তার অবদান সামান্য নয়। বুদ্ধদেবও রোমান্টিক, কিন্তু সে-রোমান্টিকতায় জীবনানন্দের সংশয়, কিংবা নজরুলের উচ্চকণ্ঠ নেই।
মোটকথা মধ্যবিত্তই এ সাহিত্য সৃষ্টি করেছে তার নিজের প্রয়োজনে; এ সাহিত্যের মধ্যে ওই শ্রেণীর অভিজ্ঞতা, আকাক্সক্ষা, পক্ষপাত, প্রবণতা, চিন্তা সবকিছুই স্বাভাবিক ও সুন্দরভাবে প্রতিফলিত হয়েছে এবং বড় একটা সত্য এই যে ওই সাহিত্য দ্বারা, সে নিজেও প্রভাবিত হয়েছে বৈকি।
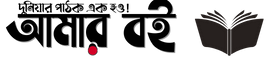

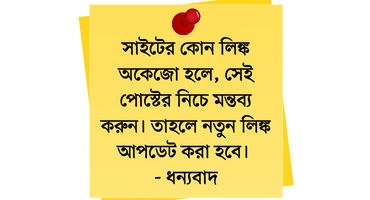







![[ছোট্টগল্প] সেক্সবয় - তসলিমা নাসরিন](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEizCNalHzbcL_TRO47frupqVrYhkJmfl_OaBixQzVrIC9gZtXtGiggWI52u_yo8X-cwdAfVwBlwyTJSaFM9F2lp5Qn4Kq0vWMi5DWKhVvP7UN-MkOFsO-kl7tIV3Xu874EhlsSm4r8fbNgR/w72-h72-p-k-no-nu/sboyt.png)








