
দেবী দর্শন
অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়
আজকাল টের পাচ্ছি, জীবনের সব বিস্ময় কেমন ক্রমে হারিয়ে যাচ্ছে। কিছুই আর অসম্ভব মনে হয় না। অথবা মনে হয় না, এরপর আর কিছু থাকতে পারে না। অহরহ পৃথিবীটা বদলাচ্ছে। আজ যেখানে দাঁড়িয়ে আছি, কাল সেখানে নেই। এক জীবনে মানুষ সব পায়, আর এক জীবনে সে সব হারাতে থাকে। টের পাই আমার হারাবার পালা বুঝি শুরু হয়েছে। ভয় লাগে। নিজের মধ্যেই কে যেন কথা কয়ে ওঠে, জীবন, জীবন রে!
তখন হাহাকার বাজে ভিতরে। শরতের নীল আকাশ, কাশফুলের ওড়াউড়ি, হেমন্তের মাঠ সব যেন বড়ো অর্থহীন। নিজের জানালায় বসে থাকলে আর একটা পৃথিবীর কথা মনে হয়। বড়ো আগেকার ছবি, যেন গত জন্মের ছবি। দূরে দেখতে পাই, কেউ সাইকেল চালিয়ে যাচ্ছে। পেছনে আমরা।
এ সব সেকালের গ্রামবাংলার কথা। আমাদের স্মৃতির কথা। শৈশবের কথা। আমাদের বড়ো হওয়ার কথা।
বাড়ি থেকে নামলেই ছিল গোপাট, দু-পাশে হিজলের গাছ। গ্রীষ্মের দুপুরে হিজলের নিবিড় ছায়ায় ঘাসের উপর কতদিন ঘুমিয়ে পড়েছি। কখনো দূর থেকে আসত গোপাল ডাক্তার। তার সাইকেলের ক্রিং ক্রিং ঘন্টিবাজনা শুনলে আমরা যে যেখানে থাকতাম জেগে যেতাম। হ্যামলিনের বাঁশিওয়ালার মতো মনে হত তাকে। সাইকেলের ঘন্টির শব্দ আমাদের চঞ্চল করে তুলত। যতদূর সাইকেল যায় ততদূর আমরা ছুটি। গোপাল ডাক্তার আর তার সাইকেল গোপাট পার হয়ে নদীর পাড়ে হারিয়ে যেত।
যতক্ষণ দেখা যায় দেখেছি। ধীরে ধীরে অনেক দূরের আকাশের নীচে সাইকেলটা এবং গোপাল ডাক্তার। সাইকেল, গোপাল ডাক্তার ক্রমে ছোটো হতে হতে বিন্দুবৎ হয়ে যেত। চোখের উপর তখন নাচত সেই বিন্দু। আমরা বলতাম, এখনো দেখা যাচ্ছে। কেউ বলত, না, আর দেখা যাচ্ছে না। মিছে কথা। আমি বলতাম, হ্যাঁ দেখা যাচ্ছে। এই নিয়ে তারপর আমাদের মধ্যে মারামারি পর্যন্ত শুরু হয়ে যেত। ফেরার সময় মনে হত গোপাল ডাক্তার আমাদের সব নিয়ে চলে গেল। আমরা ভারি মনমরা হয়ে যেতাম।
আর আসত হরিপদ কবিরাজ। ঘোড়ার পিঠে চড়ে আসত। মাথায় সোলার হ্যাট। ধুতির নীচে শার্ট গোঁজা। ঘোড়ার দুপাশে দুটো পাসিংশো টিনের সুটকেস। তাতে সব ছোটো ছোটো শিশি। হলুদ লাল নীল সব বড়ি। তার আসার খবর পেলে দল বেঁধে পুকুরপাড়ে গিয়ে দাঁড়াতাম। উঁচু ঢিবির মতো জায়গায় উঠে কিংবা গাছের ডালে চড়ে চিৎকার—ওই আসছে।
বাড়ির সামনে যতদূর চোখ যায় ফসলের জমি গ্রীষ্মের উরাট হয়ে আছে। ওর ঘোড়া আসত উরাট জমিনের ধুলো উড়িয়ে। বল্লভদির মাঠে প্রথমে বিন্দুর মতো কাঁপত। তারপর দিগন্তে লাফাত একবার উপরে, একবার নীচে। পর্দায় যেন একটা কালো বিন্দু নাচানাচি করছে। তারপর বিন্দুটা ক্রমশ বড়ো হতে থাকত। যত কাছে এগিয়ে আসত, তত বিন্দুটা একসময় বড়ো হতে হতে হরিপদ ডাক্তার আর তার ঘোড়া হয়ে যেত। আমাদের এমন আবিষ্কারের কথা কোনো বইয়ে লেখা আছে কিনা আজও জানা নেই।
হরিপদ কবিরাজ আমার মামার বাড়ির লোক। সে গ্রীষ্মে বসন্তে তার ঘোড়া নিয়ে বের হত। দূর দূর গাঁয়ে চলে যেত। দশ ক্রোশ বিশ ক্রোশের মহল্লায় সে আর তার ঘোড়া। ঘোড়ার পিঠে বোঁচকাবুঁচকি। রুগীবাড়িতে স্নানাহার। গাঁয়ের কার কী অসুখ সবকিছু খবর নিয়ে ওষুধ দিয়ে স্নানাহার। কখনো রাত হলে নিশিযাপন। সকাল হলে সে আর তার ঘোড়া আবার বের হয়ে পড়ত।
হরিপদ কবিরাজ আমাদের গাঁয়ে বছরে, দুবার আসত। গ্রীষ্মে ঘোড়ায় চড়ে, বর্ষায় নৌকো করে। নৌকোয় দুজন মাঝি। কাঠের পাটাতনের উপর ছোটো জানালা দেওয়া কাঠের ঘর। জানালাটি আরও ছোটো। ভিতরে ইজিচেয়ার, তাতে তার কাজের শেষে বিশ্রাম। একপাশে আলমারি। তাতে কাচের সব বোয়েম। চ্যবনপ্রাশ থেকে ভাস্কর লবণ সব সাজানো। ঝড়জলে কবিরাজের ছোট্ট ময়ূরপঙ্খী নৌকো নদীর জলে ভেসে যাচ্ছে। ঘাটে ঘাটে নৌকো ভিড়িয়ে ওষুধ ও রুগীর খোঁজখবর, পথ্য সব ফিরি করে আবার যাত্রা। নৌকোতেই খাওয়াদাওয়া, ঘুম। মাস দু-মাসের জন্য কখনো পুরো বর্ষাকালটাই বাড়ির বাইরে। সারা পরগনা জুড়ে তার এই ওষুধ ফিরি।
ঘাটে নৌকো বাঁধলেই খবর হয়ে যায়, এসেছে। আমাদের কাজ ছিল তখন বাড়ি বাড়ি খবর পেঁÌছে দেওয়া। ছোটোকাকা কবিরাজমামাকে বৈঠকখানায় নিয়ে বসাতেন। সাদা ফরাসে তিনি পদ্মাসনে বসে কার কী অসুখ, কী পথ্য হবে, ওষুধের বড়ির সঙ্গে কী অনুপান হবে, সব বলে দিতেন। নাড়ি দেখতেন চোখ বুজে। একটা লোক এলে গাঁয়ের সব রোগ-শোক-জরা কেমন নিমেষে উধাও হয়ে যেত। যারা মরে যাবে কথা ছিল, তারাও হরিপদ কবিরাজের নাম শুনে বিছানায় উঠে বসত। সাক্ষাৎ ধন্বন্তরি। আমাদের নিজের চোখে দেখা, হরিগোপালের বাবাকে তুলসীতলায় রাখা হয়েছে। হেঁচকি উঠছে। ওটা শেষ হলেই ব্রহ্মপুত্রের পাড়ে নিয়ে যাওয়া হবে। কানে কানে কে বলল, হরিপদ কবিরাজ এয়েছেন। সঙ্গে সঙ্গে কাজ। হেঁচকি বন্ধ হয়ে গেল।
এমন ধন্বন্তরি আমরাই দেখেছি। নৌকোটি চলে যাবার সময় শেষবারের মতো ধন্বন্তরির পরামর্শ। ঘাটে ভিড়। হরিপদ কবিরাজ কী গাছের কোনো মূলে সঞ্জীবনী সুধা আছে, তার খবর দিয়ে যেতেন। বলতেন, ঈশ্বর অসুখবিসুখ দিয়েছে, তার নিরাময়ের ব্যবস্থায় রেখেছেন সব তরুলতা, লতাগুল্ম। যা শুধু মাটিতেই জন্মায়। মধু খেতে বলতেন বয়স্কদের। মধু নাকি রক্ত উষ্ণ রাখতে ভারি সক্ষম। স্বর্ণসিন্দুর পুড়িয়া করে দিতেন বুড়োদের। দীর্ঘ জীবনলাভের এটা নাকি একটা মোক্ষম উপায়। দল বেঁধে দাঁড়িয়ে থাকত সবাই। কিংবা আমাদের বৈঠকখানায় যে ক-দিন থাকতেন, প্রায় মেলা বসে যেত যেন। মানুষজন নৌকোয় আসছে। ঘাটে শুধু তখন নৌকো আর নৌকো। আর সেসব যে কত রকমের নৌকো। আমরা নৌকোয় উঠে লাফাতাম। একটা থেকে আর একটায় লাফিয়ে যেতাম। কবিরাজমামা বাড়িতে, জলে ডুবে গেলে ভয় নেই, আগুনে পুড়ে গেলে ভয় নেই। অসুখবিসুখ আমাদের বাড়িতে ঢুকতেই সাহস পাবে না। ফলে হরিপদ কবিরাজের মতো বিস্ময়কর মানুষ আর দুটো আছে পৃথিবীতে তখন আমাদের জানা ছিল না।
সেই কবিরাজমামার বাড়ি দেখার জন্য একবার বায়না ধরেছিলাম। পুজোর ছুটিতে মামাবাড়ি গেছি। ছোটোমামাকে বললাম, আমাকে কবিরাজমামার কাছে নিয়ে চলো। ছোটোমামা বললেন, বাড়ি নেই। ওষুধ ফিরি করতে বের হয়েছে শ্রাবণ মাসে। এখনো ফেরেননি। মহালয়ায় ফিরবেন। আমার ত বাড়িটা দেখার ইচ্ছে। মানুষটাকে ত দেখাই আছে। বললাম, চলো না মামা। দেখব। কেমন বাড়িতে থাকেন। এমন সুন্দর মানুষ আমার কবিরাজমামা, এমন বিস্ময়কর মানুষ আমার মামা, তার বাড়িটা না জানি কী! দাদু বললেন, যাবে তো, কিন্তু গিয়ে আবার আটকে না যাও। যা একখানা বাড়ি। হরিপদর নানারকমের গাছপালার বাই। ওটা ত বাড়ি না একখানা জঙ্গল। জঙ্গলে হারিয়ে গেলে খুঁজে পাওয়া যাবে না। দাদুর কথা শুনে আমার আরও কৌতূহল বেড়ে গেল। জঙ্গলে হারিয়ে যাবার ভয়েই হয়ত এতবার মামাবাড়ি এসেছি একবারও ছোটোমামা কবিরাজবাড়ির দিকে নিয়ে যায়নি। ছোটোমামাকে চেপে ধরলাম, চলো না মামা।
ছোটোমামা বললেন, মুশকিল। কামড়ে না দেয়!
কামড়ে দেবে কেন! বাঘ আছে জঙ্গলে।
বাঘই বলতে পারিস। দুটো ডালকুত্তা আছে। সারা বনটায় দাপাদাপি করে বেড়ায়। চোরের উৎপাত খুব। গাছপালা সব কে চুরি করে নিয়ে যায়। কত কষ্ট করে সব সংগ্রহ করা। কেউ গাছের ছাল তুলে নিয়ে যায়। ছাল দিয়ে সালসা বানালে পরমায়ু বাড়ে। পরমায়ু কার না বাড়াবার ইচ্ছে।
আমরা মামাবাড়ি এসেছি মহালয়ার আগে। মণ্ডপে দুর্গাঠাকুর বানাচ্ছে নবীন আচার্য আর তার ছেলে। খড়বিচলির কাজ কবেই শেষ। এক মেটের কাজও শেষ। দোমেটের কাজ চলছে। আসলে স্কুল ছুটি না হতেই মার সঙ্গে মামাবাড়ি আসার একটাই কারণ। মণ্ডপে ঠাকুর বানানো দেখার বড়ো কৌতূহল। আমরা সেজন্যে এবারে আগেই চলে এসেছিলাম। কত রকমের লোকজন আসছে। দিবাকরমামা দাদুর তালুকের আদায়পত্র করে। তাঁর সারাদিন ছোটাছুটি। আমরা ভাইবোনেরা দঙ্গল বেঁধে বসে থাকি মণ্ডপে। সাদা রং দেবার সময় হলেই নাওয়া-খাওয়ার কথা ভুলে যাই। একটা ঝুড়িতে ঠাকুরের মুণ্ডু সব আলগা করা। মুণ্ডু বসিয়ে দেবার দিন কাকভোরে উঠে পড়তাম। কী জানি যদি মুণ্ডু বসানো দেখা শেষ পর্যন্ত ভাগ্যে না জোটে।
বড়ো উঠোনের একপাশে দোতলা বাড়ি। উঠোনের পুবে আটচালা মণ্ডপ। পশ্চিমে চক-মেলানো টিনের চালাঘর। অতিথি অভ্যাগতরা এলে থাকে। দক্ষিণে একতলা বিশাল একখানা দালান। ওটার একটায় সাদা ফরাস পাতা। মাথায় ঝাড়লণ্ঠন। তাকিয়ায় হেলান দিয়ে দাদু বসে থাকেন। পাশের ঘরটা বৈঠকখানা। নানারকম টেবিল চেয়ার বাতিদান। সব মিলে এক আশ্চর্য আতরের গন্ধ। এত সব বিস্ময়ের মধ্যেই কেন যে কবিরাজমামার বাড়িটা দেখার শখ হল বুঝি না।
ছোটোমামা বললেন, বিকেলে নিয়ে যাব। রেডি থাকিস।
আর তখনই রাঙামাসি বলল, ঠাকুরের শাড়ি পরানো হবে, দেখবি না।
বড়ো দোটানায় পড়া গেল। রং তুলি সব এনে সকাল থেকেই জড় করেছে নবীন আচার্য। যে ক-দিন ঠাকুর বানায়, নবীন আচার্য কারো হাতে খায় না। মণ্ডপের এক পাশে পেতলের হাঁড়িতে আতপ চালের ভাত, ঘি আর সেদ্ধ। নবীন আচার্যের ছেলেই ফুটিয়ে দেয়। বাপ-বেটায় খায়। আজ নাকি তাও হবে না। উপবাস। তিনটে দিন প্রতিমা তৈরিতে বড়ো সতর্ক থাকতে হয়। এক শাড়ি পরানোর দিন, দুই, চক্ষুদানের দিন এবং তিন, গর্জন লেপার সময়। নিয়ম অনিয়ম বলে কথা। কোথায় কখন খাঁড়া আটকে যাবে অনিয়মে সেই ভয়ে তটস্থ সবাই।
ছোটোমামাকে বললাম, শাড়ি পরানো হবে, দেখব না?
তবে তাই দেখ। আমি কিন্তু আর নিয়ে যেতে পারব না। সময় হবে না।
অগত্যা আর কী করা! বিকালেই ছোটোমামার সঙ্গে কবিরাজমামার বাড়ির দিকে হাঁটা দিলাম। মামা বললেন, ঘাবড়ে যাস না। শহরে থাকলে এমনই হয়।
এসব কথা কেন! শহরে থাকলে কী হয়? প্রশ্ন করলাম। আর কারা শহরে থাকে তাও জানতে চাইলাম।
মামা বললেন, কবিরাজদার দুই মেয়ে রাণী ভবানী। শহরে মামাবাড়িতে মানুষ। বাড়িতে জুতো পরে থাকে। ফ্রক গায়ে দেয়। সাদা ফ্রক। আমার দাদুর কথা তুলে বললেন, জানিস ত বাবা আমার সেকেলে। এসব পছন্দ করেন না। ফ্রক পরা দেখে কবিরাজদাকে ডেকে পাঠিয়েছিলেন। এটা ঠিক না হরিপদ। তোর মেয়েরা বড়ো হয়েছে। ফ্রক পরা ঠিক না।
দাদু আমার বড়ো রক্ষণশীল মানুষ জানি। কত বড়ো হলে ফ্রক পরতে হয় না এটি আমার তখনো ভালো জানা নেই। এসব নিয়েই বোধ হয় রেষারেষি আছে দুই পরিবারের মধ্যে। কিংবা হরিপদ কবিরাজ দাদুর চেয়েও প্রভাবশালী হয়ে যাচ্ছেন বলে বোধ হয় ভেতরে টান ধরেছে। সে যাহোক,—যেতে যেতে আবার মামা বললেন, জানিস ত মেয়ে দুটো বেড-টি খায়।
বেড-টি? সে আবার কী?
আরে সকালে উঠেই চা খায়।
চা খায়! বল কী মামা! বিস্ময়ে হতভম্ব! দাদুর এত পয়সা, কই চা হয় না তো! সকালে কলা মুড়ি দুধ, ছোটোরা ঘি ভাত আর কৈ মাছ ভাজা আলুসেদ্ধ না হয় পটল ঝিঙে সেদ্ধ। নরম সুগন্ধ আতপ চালের ভাত আর ঘি সে বড়ো সুস্বাদু আহার। এ-সব ফেলে চা খায়! তাও ওরা ছেলে নয়। ছেলে হলে অনেক কিছু মানিয়ে যায়। মেয়ে হয়ে এত বড়ো নেশা করে।
বললাম, কবিরাজমামা কিছু বলে না?
জানিস না কবিরাজদাও চা খায়! দুপতারার বাজারের কৈলাস মুদি নারায়ণগঞ্জ থেকে ব্রুকবন্ডের প্যাকেট আনিয়ে দেয়।
সত্যি দেখছি, আমার কবিরাজমামার বিস্ময়ের অন্ত নেই। আর তখনই মামা বললেন, এসে গেছি। বনটার শুরু।
সত্যি বন বলা যায়। বড়ো বড়ো অর্জুন গাছ, চন্দন গোটার গাছ, হাতির শুঁড়ের গাছ, জায়ফল দারচিনি কি গাছ নেই। বনটার ভিতর দিয়ে যেতে যেতে মামা আমাকে গাছ চেনাচ্ছিলেন। একবার শুধু বললেন, ডালকুত্তা ঘুরছে না কেন! বনটার ভিতর দিয়ে যেতে গা আমার ছমছম করছিল—বাসক গাছের ঝোপ—আট দশটা বড়ো বড়ো শিউলি ফুলের গাছ, পাশে বিঘেখানেক জমি জুড়ে বাসক গাছের জঙ্গল, জায়ফল হরিতকীর গাছ সব প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড। আর সব কাঠবেড়ালি এ-গাছ ও-গাছে। পাখপাখালি কত—কেমন এক তপোবনের মতো জঙ্গলের মধ্যে বাড়িটা উদ্ভাসিত হয়ে উঠলে আমার মুখে রা সরছিল না।
তারপরের দৃশ্যটা দেখে আরও মুহ্যমান অবস্থা। একটা লাল রঙের ঘোড়া, সবুজ লন, দুটো মেয়ে সাটিনের ফ্রক গায়ে দিয়ে ঘোড়া চড়া শিখছে। আমি আর হাঁটছি না। মামা ডাকলেন, এই আয়। দাঁড়িয়ে থাকলি কেন! আমি যে কেন দাঁড়িয়ে আছি মামা বুঝছে না। মেয়ে দুটো নীল রঙের চটি পরে আছে। কী লম্বা মেয়ে দুটো! টকটকে ফর্সা রং। ফ্রক গায়ে দিয়ে আছে যে বোঝাই যায় না। গায়ের রঙের সঙ্গে সাটিনের ফ্রক একেবারে মিশে গেছে। যেন ডানা লাগিয়ে দিলেই এক জোড়া পরি। পরিরা এমনই হয় বোধ হয়। নাকি দাদুর কথাই ঠিক। হরিপদ কবিরাজের বনটায় পরি ঘুরে বেড়ায়। সেখানে ছেলে ছোকরাদের ঘোরাঘুরি ঠিক নয়।
মামাকে দেখেই ওরা দৌড়ে এল। কীরে বোধাদিত্য, তুই!
মামা বললেন, আমার সেজ ভাগ্নে। তোদের বাড়িটা দেখতে এয়েছে।
তাই নাকি আয় আয় বলে আমাকে জড়িয়ে ধরল। কী সুন্দর গন্ধ শরীরে। আমার বড়ো লজ্জা লাগছিল। নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে ছুটতে চাইলাম। কিন্তু ছোটোটা আমার হাত খপ করে ধরে ফেলল। বলল, তোকে আর ছাড়ছি না। কি মিষ্টি দেখতে রে তুই! বুধ ভিতরে যাবি না? বসবি না? এত বড়ো মেয়েরা মামার সঙ্গে এভাবে কথা বলতে পারে আমার মাথায় আসে না। ছোটোমামা বলল, কুকুর দুটো দেখছি না।
ওদের এখন মেটিংয়ের সময়। আকবর ঘরে আটকে রেখেছে।
আমি বললাম, মামা মেটিং কী?
আমার কথা শুনে রাণী ভবানী খিলখিল করে হাসতে থাকল।
মামা মেটিং বিষয়টা আমাকে না বুঝিয়ে অন্য কথায় এলেন। চল দেখবি ভিতরে একটা প্রকাণ্ড শিংয়ালা রামছাগল আছে।
রাণী বলল, সজারু দেখবি?
এত কিছু আছে বাড়িটাতে জানিই না। সজারু দিয়ে কী হয়! বড়ো শিংয়ালা রামছাগল দিয়ে কী হয় কিছুই জানা নেই।
বললাম, তোমরা ওগুলো রাখ কেন!
বারে, বাবার ওষুধে লাগে। কবিরাজি তেলে ওদের চর্বি দরকার হয়।
বাড়িটা সত্যি ছবির মতো। লাল ইঁটের দালান। সামনে বড়ো লন। দাগ কাটা চুন দেওয়া। ব্যাডমিন্টন খেলার জায়গা। পাশে ডিসপেন্সারি। বারান্দায় অতিকায় সব উদূখল। বড়ো বড়ো শীতলপাটিতে গাছের শেকড় ছাল সব শুকানো হচ্ছে। একজন লোক উবু হয়ে হামানদিস্তায় ছাল শেকড়বাকড় গুঁড়ো করছে।
ছোটোমামার কত ছোটো আমার রাঙা মাসি। শাড়ি পরে। মেয়েরা বড়ো হলে ফ্রক পরে না। বড়োরা খারাপ পায় এতে। এত সুন্দরের মধ্যে ওটুকু খুঁত থাকবে কেন ভাবতেই কেন যেন বলে ফেললাম, তোমরা ফ্রক পর কেন? শাড়ি পরতে পার না!
রাণী আমাকে আবার জাপ্টে ধরতে এল। চুকচুক করল ঠোঁটে। বলল, হ্যাঁ পরি। রাতে পরি।
ভারি তাজ্জব কথা। রাতে শাড়ি পরে দিনে পরে না। ভ্যাবলুর মতো তাকিয়ে বললাম, রাতে শাড়ি পর কেন!
আবার খিলখিল হাসি দু-বোনের। ছোটোমামা পাশে হাঁটছে। রাণী ভবানী এমনই মামা যেন জানে। রাণী বলল, আয় পরিজ খাবি। বলে ভিতরে নিয়ে গেলে আরও বিস্ময়। ঘরের টেবিলে ফুলদানি। তাতে রজনীগন্ধা গুচ্ছ। জানালায় ভেলভেটের পর্দা। যেদিকে তাকাই সর্বত্র ছবির মতো এক সৌন্দর্য খেলা করে বেড়াচ্ছে। পরিজ কি জানি না। এত খাবার খেয়েছি পরিজ খাইনি কেন—এসব মনে হচ্ছিল। আর সেই বনটার ভিতর এই দুই মেয়ে ঘুরে বেড়ালে পৃথিবীর কোনো গোপন রহস্য ধরা পড়ে যায় এমন মনে হবার সময় দেখলাম, ভবানী তার মাকে ডেকে নিয়ে আসছে। চা-পরিজ কেক। একেবারে ভিনদেশি খাবার। লজ্জায় খেতে পারছিলাম না। আমার পায়ে জুতো নেই। শুধু হাফশার্ট-হ্যাফপ্যান্ট পরনে। কেমন এক অপরিচিত পৃথিবীতে ঢুকে কেবল বিস্ময়ের পর বিস্ময়ের সম্মুখীন হচ্ছি। হঠাৎ আমার কী হল জানি না, সহসা দৌড়ে ছুটে পালালাম। রাণী চিৎকার করে বলল, কী রে কী হল! কোথায় যাচ্ছিস! আমি বললাম, বাড়ি। আবার শুনতে পেলাম, যাস না বনটার মধ্যে দেখবি কে দাঁড়িয়ে আছে।
আমি বললাম, দুর্গাঠাকুরকে শাড়ি পরানো হবে দেখতে যাচ্ছি।
যাস না। বনটার মধ্যে তোকে দুর্গাঠাকুর দেখাব। তারপর বললে, খেতে দিলে না খেয়ে যেতে নেই।
তোমাদের বনটায় দুর্গাঠাকুর আছে!
থাকবে না। এমন সুন্দর বনে ঠাকুর-দেবতারাই তো থাকে।
বনের মধ্যে ঢুকে আমারও একথা মনে হয়েছিল। শিউলি ফুলের গন্ধে চারপাশ ম ম করছে। সকালবেলায় শিউলি ফুল সাদা হয়ে শতরঞ্চের মতো সেজে থাকে। ভাবলাম মহালয়ার দিন এখান থেকেই ফুল চুরি করে নিয়ে যাব।
আর মহালয়ার দিন রাত থাকতে আমরা ক-ভাই বোন মিলে গেছিলাম সেই শিউলি গাছগুলোর নীচে ফুল তুলতে। আশ্চর্য আবছা অন্ধকারে দেখলাম বিরাট এক জন্তুর পিঠে পা দিয়ে এক দেবী শিউলি গাছে পিঠ দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। অস্পষ্ট আঁধারে মোমের মতো যেন জ্বলছিল দেবী। আমরা কাছে যেতে সাহস পাইনি। ফুল না নিয়েই দৌড়ে পালিয়েছিলাম। সেই আমার প্রথম ও শেষ সাক্ষাৎ দেবী দর্শন। তারপর সারাজীবন মণ্ডপে মণ্ডপে ঘুরেও আর তার দেখা পাইনি।
অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়
আজকাল টের পাচ্ছি, জীবনের সব বিস্ময় কেমন ক্রমে হারিয়ে যাচ্ছে। কিছুই আর অসম্ভব মনে হয় না। অথবা মনে হয় না, এরপর আর কিছু থাকতে পারে না। অহরহ পৃথিবীটা বদলাচ্ছে। আজ যেখানে দাঁড়িয়ে আছি, কাল সেখানে নেই। এক জীবনে মানুষ সব পায়, আর এক জীবনে সে সব হারাতে থাকে। টের পাই আমার হারাবার পালা বুঝি শুরু হয়েছে। ভয় লাগে। নিজের মধ্যেই কে যেন কথা কয়ে ওঠে, জীবন, জীবন রে!
তখন হাহাকার বাজে ভিতরে। শরতের নীল আকাশ, কাশফুলের ওড়াউড়ি, হেমন্তের মাঠ সব যেন বড়ো অর্থহীন। নিজের জানালায় বসে থাকলে আর একটা পৃথিবীর কথা মনে হয়। বড়ো আগেকার ছবি, যেন গত জন্মের ছবি। দূরে দেখতে পাই, কেউ সাইকেল চালিয়ে যাচ্ছে। পেছনে আমরা।
এ সব সেকালের গ্রামবাংলার কথা। আমাদের স্মৃতির কথা। শৈশবের কথা। আমাদের বড়ো হওয়ার কথা।
বাড়ি থেকে নামলেই ছিল গোপাট, দু-পাশে হিজলের গাছ। গ্রীষ্মের দুপুরে হিজলের নিবিড় ছায়ায় ঘাসের উপর কতদিন ঘুমিয়ে পড়েছি। কখনো দূর থেকে আসত গোপাল ডাক্তার। তার সাইকেলের ক্রিং ক্রিং ঘন্টিবাজনা শুনলে আমরা যে যেখানে থাকতাম জেগে যেতাম। হ্যামলিনের বাঁশিওয়ালার মতো মনে হত তাকে। সাইকেলের ঘন্টির শব্দ আমাদের চঞ্চল করে তুলত। যতদূর সাইকেল যায় ততদূর আমরা ছুটি। গোপাল ডাক্তার আর তার সাইকেল গোপাট পার হয়ে নদীর পাড়ে হারিয়ে যেত।
যতক্ষণ দেখা যায় দেখেছি। ধীরে ধীরে অনেক দূরের আকাশের নীচে সাইকেলটা এবং গোপাল ডাক্তার। সাইকেল, গোপাল ডাক্তার ক্রমে ছোটো হতে হতে বিন্দুবৎ হয়ে যেত। চোখের উপর তখন নাচত সেই বিন্দু। আমরা বলতাম, এখনো দেখা যাচ্ছে। কেউ বলত, না, আর দেখা যাচ্ছে না। মিছে কথা। আমি বলতাম, হ্যাঁ দেখা যাচ্ছে। এই নিয়ে তারপর আমাদের মধ্যে মারামারি পর্যন্ত শুরু হয়ে যেত। ফেরার সময় মনে হত গোপাল ডাক্তার আমাদের সব নিয়ে চলে গেল। আমরা ভারি মনমরা হয়ে যেতাম।
আর আসত হরিপদ কবিরাজ। ঘোড়ার পিঠে চড়ে আসত। মাথায় সোলার হ্যাট। ধুতির নীচে শার্ট গোঁজা। ঘোড়ার দুপাশে দুটো পাসিংশো টিনের সুটকেস। তাতে সব ছোটো ছোটো শিশি। হলুদ লাল নীল সব বড়ি। তার আসার খবর পেলে দল বেঁধে পুকুরপাড়ে গিয়ে দাঁড়াতাম। উঁচু ঢিবির মতো জায়গায় উঠে কিংবা গাছের ডালে চড়ে চিৎকার—ওই আসছে।
বাড়ির সামনে যতদূর চোখ যায় ফসলের জমি গ্রীষ্মের উরাট হয়ে আছে। ওর ঘোড়া আসত উরাট জমিনের ধুলো উড়িয়ে। বল্লভদির মাঠে প্রথমে বিন্দুর মতো কাঁপত। তারপর দিগন্তে লাফাত একবার উপরে, একবার নীচে। পর্দায় যেন একটা কালো বিন্দু নাচানাচি করছে। তারপর বিন্দুটা ক্রমশ বড়ো হতে থাকত। যত কাছে এগিয়ে আসত, তত বিন্দুটা একসময় বড়ো হতে হতে হরিপদ ডাক্তার আর তার ঘোড়া হয়ে যেত। আমাদের এমন আবিষ্কারের কথা কোনো বইয়ে লেখা আছে কিনা আজও জানা নেই।
হরিপদ কবিরাজ আমার মামার বাড়ির লোক। সে গ্রীষ্মে বসন্তে তার ঘোড়া নিয়ে বের হত। দূর দূর গাঁয়ে চলে যেত। দশ ক্রোশ বিশ ক্রোশের মহল্লায় সে আর তার ঘোড়া। ঘোড়ার পিঠে বোঁচকাবুঁচকি। রুগীবাড়িতে স্নানাহার। গাঁয়ের কার কী অসুখ সবকিছু খবর নিয়ে ওষুধ দিয়ে স্নানাহার। কখনো রাত হলে নিশিযাপন। সকাল হলে সে আর তার ঘোড়া আবার বের হয়ে পড়ত।
হরিপদ কবিরাজ আমাদের গাঁয়ে বছরে, দুবার আসত। গ্রীষ্মে ঘোড়ায় চড়ে, বর্ষায় নৌকো করে। নৌকোয় দুজন মাঝি। কাঠের পাটাতনের উপর ছোটো জানালা দেওয়া কাঠের ঘর। জানালাটি আরও ছোটো। ভিতরে ইজিচেয়ার, তাতে তার কাজের শেষে বিশ্রাম। একপাশে আলমারি। তাতে কাচের সব বোয়েম। চ্যবনপ্রাশ থেকে ভাস্কর লবণ সব সাজানো। ঝড়জলে কবিরাজের ছোট্ট ময়ূরপঙ্খী নৌকো নদীর জলে ভেসে যাচ্ছে। ঘাটে ঘাটে নৌকো ভিড়িয়ে ওষুধ ও রুগীর খোঁজখবর, পথ্য সব ফিরি করে আবার যাত্রা। নৌকোতেই খাওয়াদাওয়া, ঘুম। মাস দু-মাসের জন্য কখনো পুরো বর্ষাকালটাই বাড়ির বাইরে। সারা পরগনা জুড়ে তার এই ওষুধ ফিরি।
ঘাটে নৌকো বাঁধলেই খবর হয়ে যায়, এসেছে। আমাদের কাজ ছিল তখন বাড়ি বাড়ি খবর পেঁÌছে দেওয়া। ছোটোকাকা কবিরাজমামাকে বৈঠকখানায় নিয়ে বসাতেন। সাদা ফরাসে তিনি পদ্মাসনে বসে কার কী অসুখ, কী পথ্য হবে, ওষুধের বড়ির সঙ্গে কী অনুপান হবে, সব বলে দিতেন। নাড়ি দেখতেন চোখ বুজে। একটা লোক এলে গাঁয়ের সব রোগ-শোক-জরা কেমন নিমেষে উধাও হয়ে যেত। যারা মরে যাবে কথা ছিল, তারাও হরিপদ কবিরাজের নাম শুনে বিছানায় উঠে বসত। সাক্ষাৎ ধন্বন্তরি। আমাদের নিজের চোখে দেখা, হরিগোপালের বাবাকে তুলসীতলায় রাখা হয়েছে। হেঁচকি উঠছে। ওটা শেষ হলেই ব্রহ্মপুত্রের পাড়ে নিয়ে যাওয়া হবে। কানে কানে কে বলল, হরিপদ কবিরাজ এয়েছেন। সঙ্গে সঙ্গে কাজ। হেঁচকি বন্ধ হয়ে গেল।
এমন ধন্বন্তরি আমরাই দেখেছি। নৌকোটি চলে যাবার সময় শেষবারের মতো ধন্বন্তরির পরামর্শ। ঘাটে ভিড়। হরিপদ কবিরাজ কী গাছের কোনো মূলে সঞ্জীবনী সুধা আছে, তার খবর দিয়ে যেতেন। বলতেন, ঈশ্বর অসুখবিসুখ দিয়েছে, তার নিরাময়ের ব্যবস্থায় রেখেছেন সব তরুলতা, লতাগুল্ম। যা শুধু মাটিতেই জন্মায়। মধু খেতে বলতেন বয়স্কদের। মধু নাকি রক্ত উষ্ণ রাখতে ভারি সক্ষম। স্বর্ণসিন্দুর পুড়িয়া করে দিতেন বুড়োদের। দীর্ঘ জীবনলাভের এটা নাকি একটা মোক্ষম উপায়। দল বেঁধে দাঁড়িয়ে থাকত সবাই। কিংবা আমাদের বৈঠকখানায় যে ক-দিন থাকতেন, প্রায় মেলা বসে যেত যেন। মানুষজন নৌকোয় আসছে। ঘাটে শুধু তখন নৌকো আর নৌকো। আর সেসব যে কত রকমের নৌকো। আমরা নৌকোয় উঠে লাফাতাম। একটা থেকে আর একটায় লাফিয়ে যেতাম। কবিরাজমামা বাড়িতে, জলে ডুবে গেলে ভয় নেই, আগুনে পুড়ে গেলে ভয় নেই। অসুখবিসুখ আমাদের বাড়িতে ঢুকতেই সাহস পাবে না। ফলে হরিপদ কবিরাজের মতো বিস্ময়কর মানুষ আর দুটো আছে পৃথিবীতে তখন আমাদের জানা ছিল না।
সেই কবিরাজমামার বাড়ি দেখার জন্য একবার বায়না ধরেছিলাম। পুজোর ছুটিতে মামাবাড়ি গেছি। ছোটোমামাকে বললাম, আমাকে কবিরাজমামার কাছে নিয়ে চলো। ছোটোমামা বললেন, বাড়ি নেই। ওষুধ ফিরি করতে বের হয়েছে শ্রাবণ মাসে। এখনো ফেরেননি। মহালয়ায় ফিরবেন। আমার ত বাড়িটা দেখার ইচ্ছে। মানুষটাকে ত দেখাই আছে। বললাম, চলো না মামা। দেখব। কেমন বাড়িতে থাকেন। এমন সুন্দর মানুষ আমার কবিরাজমামা, এমন বিস্ময়কর মানুষ আমার মামা, তার বাড়িটা না জানি কী! দাদু বললেন, যাবে তো, কিন্তু গিয়ে আবার আটকে না যাও। যা একখানা বাড়ি। হরিপদর নানারকমের গাছপালার বাই। ওটা ত বাড়ি না একখানা জঙ্গল। জঙ্গলে হারিয়ে গেলে খুঁজে পাওয়া যাবে না। দাদুর কথা শুনে আমার আরও কৌতূহল বেড়ে গেল। জঙ্গলে হারিয়ে যাবার ভয়েই হয়ত এতবার মামাবাড়ি এসেছি একবারও ছোটোমামা কবিরাজবাড়ির দিকে নিয়ে যায়নি। ছোটোমামাকে চেপে ধরলাম, চলো না মামা।
ছোটোমামা বললেন, মুশকিল। কামড়ে না দেয়!
কামড়ে দেবে কেন! বাঘ আছে জঙ্গলে।
বাঘই বলতে পারিস। দুটো ডালকুত্তা আছে। সারা বনটায় দাপাদাপি করে বেড়ায়। চোরের উৎপাত খুব। গাছপালা সব কে চুরি করে নিয়ে যায়। কত কষ্ট করে সব সংগ্রহ করা। কেউ গাছের ছাল তুলে নিয়ে যায়। ছাল দিয়ে সালসা বানালে পরমায়ু বাড়ে। পরমায়ু কার না বাড়াবার ইচ্ছে।
আমরা মামাবাড়ি এসেছি মহালয়ার আগে। মণ্ডপে দুর্গাঠাকুর বানাচ্ছে নবীন আচার্য আর তার ছেলে। খড়বিচলির কাজ কবেই শেষ। এক মেটের কাজও শেষ। দোমেটের কাজ চলছে। আসলে স্কুল ছুটি না হতেই মার সঙ্গে মামাবাড়ি আসার একটাই কারণ। মণ্ডপে ঠাকুর বানানো দেখার বড়ো কৌতূহল। আমরা সেজন্যে এবারে আগেই চলে এসেছিলাম। কত রকমের লোকজন আসছে। দিবাকরমামা দাদুর তালুকের আদায়পত্র করে। তাঁর সারাদিন ছোটাছুটি। আমরা ভাইবোনেরা দঙ্গল বেঁধে বসে থাকি মণ্ডপে। সাদা রং দেবার সময় হলেই নাওয়া-খাওয়ার কথা ভুলে যাই। একটা ঝুড়িতে ঠাকুরের মুণ্ডু সব আলগা করা। মুণ্ডু বসিয়ে দেবার দিন কাকভোরে উঠে পড়তাম। কী জানি যদি মুণ্ডু বসানো দেখা শেষ পর্যন্ত ভাগ্যে না জোটে।
বড়ো উঠোনের একপাশে দোতলা বাড়ি। উঠোনের পুবে আটচালা মণ্ডপ। পশ্চিমে চক-মেলানো টিনের চালাঘর। অতিথি অভ্যাগতরা এলে থাকে। দক্ষিণে একতলা বিশাল একখানা দালান। ওটার একটায় সাদা ফরাস পাতা। মাথায় ঝাড়লণ্ঠন। তাকিয়ায় হেলান দিয়ে দাদু বসে থাকেন। পাশের ঘরটা বৈঠকখানা। নানারকম টেবিল চেয়ার বাতিদান। সব মিলে এক আশ্চর্য আতরের গন্ধ। এত সব বিস্ময়ের মধ্যেই কেন যে কবিরাজমামার বাড়িটা দেখার শখ হল বুঝি না।
ছোটোমামা বললেন, বিকেলে নিয়ে যাব। রেডি থাকিস।
আর তখনই রাঙামাসি বলল, ঠাকুরের শাড়ি পরানো হবে, দেখবি না।
বড়ো দোটানায় পড়া গেল। রং তুলি সব এনে সকাল থেকেই জড় করেছে নবীন আচার্য। যে ক-দিন ঠাকুর বানায়, নবীন আচার্য কারো হাতে খায় না। মণ্ডপের এক পাশে পেতলের হাঁড়িতে আতপ চালের ভাত, ঘি আর সেদ্ধ। নবীন আচার্যের ছেলেই ফুটিয়ে দেয়। বাপ-বেটায় খায়। আজ নাকি তাও হবে না। উপবাস। তিনটে দিন প্রতিমা তৈরিতে বড়ো সতর্ক থাকতে হয়। এক শাড়ি পরানোর দিন, দুই, চক্ষুদানের দিন এবং তিন, গর্জন লেপার সময়। নিয়ম অনিয়ম বলে কথা। কোথায় কখন খাঁড়া আটকে যাবে অনিয়মে সেই ভয়ে তটস্থ সবাই।
ছোটোমামাকে বললাম, শাড়ি পরানো হবে, দেখব না?
তবে তাই দেখ। আমি কিন্তু আর নিয়ে যেতে পারব না। সময় হবে না।
অগত্যা আর কী করা! বিকালেই ছোটোমামার সঙ্গে কবিরাজমামার বাড়ির দিকে হাঁটা দিলাম। মামা বললেন, ঘাবড়ে যাস না। শহরে থাকলে এমনই হয়।
এসব কথা কেন! শহরে থাকলে কী হয়? প্রশ্ন করলাম। আর কারা শহরে থাকে তাও জানতে চাইলাম।
মামা বললেন, কবিরাজদার দুই মেয়ে রাণী ভবানী। শহরে মামাবাড়িতে মানুষ। বাড়িতে জুতো পরে থাকে। ফ্রক গায়ে দেয়। সাদা ফ্রক। আমার দাদুর কথা তুলে বললেন, জানিস ত বাবা আমার সেকেলে। এসব পছন্দ করেন না। ফ্রক পরা দেখে কবিরাজদাকে ডেকে পাঠিয়েছিলেন। এটা ঠিক না হরিপদ। তোর মেয়েরা বড়ো হয়েছে। ফ্রক পরা ঠিক না।
দাদু আমার বড়ো রক্ষণশীল মানুষ জানি। কত বড়ো হলে ফ্রক পরতে হয় না এটি আমার তখনো ভালো জানা নেই। এসব নিয়েই বোধ হয় রেষারেষি আছে দুই পরিবারের মধ্যে। কিংবা হরিপদ কবিরাজ দাদুর চেয়েও প্রভাবশালী হয়ে যাচ্ছেন বলে বোধ হয় ভেতরে টান ধরেছে। সে যাহোক,—যেতে যেতে আবার মামা বললেন, জানিস ত মেয়ে দুটো বেড-টি খায়।
বেড-টি? সে আবার কী?
আরে সকালে উঠেই চা খায়।
চা খায়! বল কী মামা! বিস্ময়ে হতভম্ব! দাদুর এত পয়সা, কই চা হয় না তো! সকালে কলা মুড়ি দুধ, ছোটোরা ঘি ভাত আর কৈ মাছ ভাজা আলুসেদ্ধ না হয় পটল ঝিঙে সেদ্ধ। নরম সুগন্ধ আতপ চালের ভাত আর ঘি সে বড়ো সুস্বাদু আহার। এ-সব ফেলে চা খায়! তাও ওরা ছেলে নয়। ছেলে হলে অনেক কিছু মানিয়ে যায়। মেয়ে হয়ে এত বড়ো নেশা করে।
বললাম, কবিরাজমামা কিছু বলে না?
জানিস না কবিরাজদাও চা খায়! দুপতারার বাজারের কৈলাস মুদি নারায়ণগঞ্জ থেকে ব্রুকবন্ডের প্যাকেট আনিয়ে দেয়।
সত্যি দেখছি, আমার কবিরাজমামার বিস্ময়ের অন্ত নেই। আর তখনই মামা বললেন, এসে গেছি। বনটার শুরু।
সত্যি বন বলা যায়। বড়ো বড়ো অর্জুন গাছ, চন্দন গোটার গাছ, হাতির শুঁড়ের গাছ, জায়ফল দারচিনি কি গাছ নেই। বনটার ভিতর দিয়ে যেতে যেতে মামা আমাকে গাছ চেনাচ্ছিলেন। একবার শুধু বললেন, ডালকুত্তা ঘুরছে না কেন! বনটার ভিতর দিয়ে যেতে গা আমার ছমছম করছিল—বাসক গাছের ঝোপ—আট দশটা বড়ো বড়ো শিউলি ফুলের গাছ, পাশে বিঘেখানেক জমি জুড়ে বাসক গাছের জঙ্গল, জায়ফল হরিতকীর গাছ সব প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড। আর সব কাঠবেড়ালি এ-গাছ ও-গাছে। পাখপাখালি কত—কেমন এক তপোবনের মতো জঙ্গলের মধ্যে বাড়িটা উদ্ভাসিত হয়ে উঠলে আমার মুখে রা সরছিল না।
তারপরের দৃশ্যটা দেখে আরও মুহ্যমান অবস্থা। একটা লাল রঙের ঘোড়া, সবুজ লন, দুটো মেয়ে সাটিনের ফ্রক গায়ে দিয়ে ঘোড়া চড়া শিখছে। আমি আর হাঁটছি না। মামা ডাকলেন, এই আয়। দাঁড়িয়ে থাকলি কেন! আমি যে কেন দাঁড়িয়ে আছি মামা বুঝছে না। মেয়ে দুটো নীল রঙের চটি পরে আছে। কী লম্বা মেয়ে দুটো! টকটকে ফর্সা রং। ফ্রক গায়ে দিয়ে আছে যে বোঝাই যায় না। গায়ের রঙের সঙ্গে সাটিনের ফ্রক একেবারে মিশে গেছে। যেন ডানা লাগিয়ে দিলেই এক জোড়া পরি। পরিরা এমনই হয় বোধ হয়। নাকি দাদুর কথাই ঠিক। হরিপদ কবিরাজের বনটায় পরি ঘুরে বেড়ায়। সেখানে ছেলে ছোকরাদের ঘোরাঘুরি ঠিক নয়।
মামাকে দেখেই ওরা দৌড়ে এল। কীরে বোধাদিত্য, তুই!
মামা বললেন, আমার সেজ ভাগ্নে। তোদের বাড়িটা দেখতে এয়েছে।
তাই নাকি আয় আয় বলে আমাকে জড়িয়ে ধরল। কী সুন্দর গন্ধ শরীরে। আমার বড়ো লজ্জা লাগছিল। নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে ছুটতে চাইলাম। কিন্তু ছোটোটা আমার হাত খপ করে ধরে ফেলল। বলল, তোকে আর ছাড়ছি না। কি মিষ্টি দেখতে রে তুই! বুধ ভিতরে যাবি না? বসবি না? এত বড়ো মেয়েরা মামার সঙ্গে এভাবে কথা বলতে পারে আমার মাথায় আসে না। ছোটোমামা বলল, কুকুর দুটো দেখছি না।
ওদের এখন মেটিংয়ের সময়। আকবর ঘরে আটকে রেখেছে।
আমি বললাম, মামা মেটিং কী?
আমার কথা শুনে রাণী ভবানী খিলখিল করে হাসতে থাকল।
মামা মেটিং বিষয়টা আমাকে না বুঝিয়ে অন্য কথায় এলেন। চল দেখবি ভিতরে একটা প্রকাণ্ড শিংয়ালা রামছাগল আছে।
রাণী বলল, সজারু দেখবি?
এত কিছু আছে বাড়িটাতে জানিই না। সজারু দিয়ে কী হয়! বড়ো শিংয়ালা রামছাগল দিয়ে কী হয় কিছুই জানা নেই।
বললাম, তোমরা ওগুলো রাখ কেন!
বারে, বাবার ওষুধে লাগে। কবিরাজি তেলে ওদের চর্বি দরকার হয়।
বাড়িটা সত্যি ছবির মতো। লাল ইঁটের দালান। সামনে বড়ো লন। দাগ কাটা চুন দেওয়া। ব্যাডমিন্টন খেলার জায়গা। পাশে ডিসপেন্সারি। বারান্দায় অতিকায় সব উদূখল। বড়ো বড়ো শীতলপাটিতে গাছের শেকড় ছাল সব শুকানো হচ্ছে। একজন লোক উবু হয়ে হামানদিস্তায় ছাল শেকড়বাকড় গুঁড়ো করছে।
ছোটোমামার কত ছোটো আমার রাঙা মাসি। শাড়ি পরে। মেয়েরা বড়ো হলে ফ্রক পরে না। বড়োরা খারাপ পায় এতে। এত সুন্দরের মধ্যে ওটুকু খুঁত থাকবে কেন ভাবতেই কেন যেন বলে ফেললাম, তোমরা ফ্রক পর কেন? শাড়ি পরতে পার না!
রাণী আমাকে আবার জাপ্টে ধরতে এল। চুকচুক করল ঠোঁটে। বলল, হ্যাঁ পরি। রাতে পরি।
ভারি তাজ্জব কথা। রাতে শাড়ি পরে দিনে পরে না। ভ্যাবলুর মতো তাকিয়ে বললাম, রাতে শাড়ি পর কেন!
আবার খিলখিল হাসি দু-বোনের। ছোটোমামা পাশে হাঁটছে। রাণী ভবানী এমনই মামা যেন জানে। রাণী বলল, আয় পরিজ খাবি। বলে ভিতরে নিয়ে গেলে আরও বিস্ময়। ঘরের টেবিলে ফুলদানি। তাতে রজনীগন্ধা গুচ্ছ। জানালায় ভেলভেটের পর্দা। যেদিকে তাকাই সর্বত্র ছবির মতো এক সৌন্দর্য খেলা করে বেড়াচ্ছে। পরিজ কি জানি না। এত খাবার খেয়েছি পরিজ খাইনি কেন—এসব মনে হচ্ছিল। আর সেই বনটার ভিতর এই দুই মেয়ে ঘুরে বেড়ালে পৃথিবীর কোনো গোপন রহস্য ধরা পড়ে যায় এমন মনে হবার সময় দেখলাম, ভবানী তার মাকে ডেকে নিয়ে আসছে। চা-পরিজ কেক। একেবারে ভিনদেশি খাবার। লজ্জায় খেতে পারছিলাম না। আমার পায়ে জুতো নেই। শুধু হাফশার্ট-হ্যাফপ্যান্ট পরনে। কেমন এক অপরিচিত পৃথিবীতে ঢুকে কেবল বিস্ময়ের পর বিস্ময়ের সম্মুখীন হচ্ছি। হঠাৎ আমার কী হল জানি না, সহসা দৌড়ে ছুটে পালালাম। রাণী চিৎকার করে বলল, কী রে কী হল! কোথায় যাচ্ছিস! আমি বললাম, বাড়ি। আবার শুনতে পেলাম, যাস না বনটার মধ্যে দেখবি কে দাঁড়িয়ে আছে।
আমি বললাম, দুর্গাঠাকুরকে শাড়ি পরানো হবে দেখতে যাচ্ছি।
যাস না। বনটার মধ্যে তোকে দুর্গাঠাকুর দেখাব। তারপর বললে, খেতে দিলে না খেয়ে যেতে নেই।
তোমাদের বনটায় দুর্গাঠাকুর আছে!
থাকবে না। এমন সুন্দর বনে ঠাকুর-দেবতারাই তো থাকে।
বনের মধ্যে ঢুকে আমারও একথা মনে হয়েছিল। শিউলি ফুলের গন্ধে চারপাশ ম ম করছে। সকালবেলায় শিউলি ফুল সাদা হয়ে শতরঞ্চের মতো সেজে থাকে। ভাবলাম মহালয়ার দিন এখান থেকেই ফুল চুরি করে নিয়ে যাব।
আর মহালয়ার দিন রাত থাকতে আমরা ক-ভাই বোন মিলে গেছিলাম সেই শিউলি গাছগুলোর নীচে ফুল তুলতে। আশ্চর্য আবছা অন্ধকারে দেখলাম বিরাট এক জন্তুর পিঠে পা দিয়ে এক দেবী শিউলি গাছে পিঠ দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। অস্পষ্ট আঁধারে মোমের মতো যেন জ্বলছিল দেবী। আমরা কাছে যেতে সাহস পাইনি। ফুল না নিয়েই দৌড়ে পালিয়েছিলাম। সেই আমার প্রথম ও শেষ সাক্ষাৎ দেবী দর্শন। তারপর সারাজীবন মণ্ডপে মণ্ডপে ঘুরেও আর তার দেখা পাইনি।
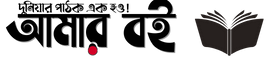

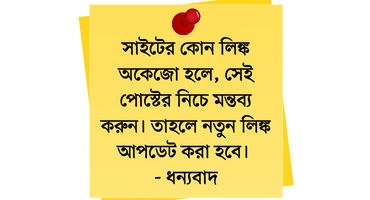







![[ছোট্টগল্প] সেক্সবয় - তসলিমা নাসরিন](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEizCNalHzbcL_TRO47frupqVrYhkJmfl_OaBixQzVrIC9gZtXtGiggWI52u_yo8X-cwdAfVwBlwyTJSaFM9F2lp5Qn4Kq0vWMi5DWKhVvP7UN-MkOFsO-kl7tIV3Xu874EhlsSm4r8fbNgR/w72-h72-p-k-no-nu/sboyt.png)








