চিন্ময় গুহ
অগ্রন্থিত প্রবন্ধ
নীরদচন্দ্র চৌধুরী
সম্পাদনা: শ্রুত্যানন্দ ডাকুয়া। সূত্রধর
নীরদচন্দ্র চৌধুরী সর্বদিক থেকে একক ও স্বতন্ত্র। তিনি সেই বিরলতম সাহিত্যবোদ্ধা ইতিহাসপাঠক, যাঁর আগ্রহ অকল্পনীয় রকম সর্বত্রগামী।
যখন বাঙালি-জীবন থেকে জ্ঞানচর্চার প্রতি শ্রদ্ধা প্রায় সম্পূর্ণ নির্মূল হতে বসেছে, তখন শ্রুত্যানন্দ ডাকুয়া নামে এক বুদ্ধিদীপ্ত তরুণ গবেষক নীরদ চৌধুরীর (১৮৯৭-১৯৯৯) মতো মনীষাকে নতুন করে আমাদের জীবনের সঙ্গে যুক্ত করতে চাইছেন। তাঁর পুনরাবিষ্কৃত নীরদবাবুর তরুণ বয়স থেকে পরিণত বয়সের উনিশটি অগ্রন্থিত প্রবন্ধের এই সংকলনটি, যার রচনাকাল ১৯২৭-১৯৯৭, গত শতকের এক অনন্য দ্বিভাষিক বাঙালি ভাবুকের বহুমাত্রিক ভাবনায় এক নতুন মাত্রা যোগ করল। তাঁর চেয়ে দীর্ঘতর সময় ধরে— ১৯২৫ থেকে ১৯৯৭, প্রায় বাহাত্তর বছর— মননচর্চা সম্ভবত এদেশে আর কেউ করেননি।
এখন প্রশ্ন হল, আমরা কীভাবে পাঠ করব তাঁর চিন্তাজীবনকে? ১৯৮৮ সালে ‘নিউ ইয়র্ক টাইমস’ কাগজে নীরদ সি চৌধুরীর আত্মজীবনীর দ্বিতীয় পর্ব ‘দাই হ্যান্ড গ্রেট অ্যানার্ক’-এর সমালোচনা করতে গিয়ে ডেভিড লেলিভেল্ড লিখেছিলেন, ‘Nirad Chaudhuri is a fiction created by the Indian writer of the same name— a bizarre, outrageous and magical transformation of that stock character of imperialist literature, the Bengali Babu.’ এই ঔপনিবেশিক ব্যাখ্যা মানি বা না মানি, স্বীকার করতেই হবে যে, নীরদচন্দ্র নিজেকে তিলে তিলে তৈরি করে এমন এক ঈর্ষণীয় স্তরে উন্নীত করেছিলেন, যা তাঁকে এক চির-ব্যতিক্রমী সাংস্কৃতিক মিনারে পরিণত করেছে। আমাদের অ্যাকাডেমিক জগতের অনেক পণ্ডিতই জ্ঞানের এই ঘূর্ণিঝড়ের সামনে খড়কুটোর মতো উড়ে যাবেন।
নীরদচন্দ্রকে যদি একটি বিশেষ ঔপনিবেশিকতার উত্তর-ঔপনিবেশিক প্রতিনিধি ভাবি, যিনি সর্বদিক থেকে একক ও স্বতন্ত্র, তিনি সেই বিরলতম সাহিত্যবোদ্ধা ইতিহাসপাঠক, যাঁর আগ্রহ অকল্পনীয় রকম সর্বত্রগামী। জ্ঞানের অহংকার তাঁর ইংরেজি ও বাংলা শৈলীকে আগাগোড়া নিয়ন্ত্রণ করেছে। প্রশ্ন উঠবে, তবে তাঁকে আমরা কীভাবে বিচার করব, কোথায় তাঁর ঐতিহাসিক স্থানাঙ্ক? নিরপেক্ষ বিচার করতে গেলে দেখব, তিনি উনিশ শতকের চিন্তকদের চেয়ে আলাদা। তিনি বঙ্কিমচন্দ্র, হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় বা হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর সগোত্র নন। যাঁকে তিনি এত শ্রদ্ধা করেছেন সেই বিদ্যাসাগরের মতো তো ননই। আবার পরবর্তী কালের অন্নদাশংকর রায়, শিবনারায়ণ রায়, অম্লান দত্ত, অমর্ত্য সেনদের সঙ্গে তাঁর একেবারেই কোনও মিল নেই। তাঁর জ্ঞানচর্চার ধরন আঠারো শতকের ইউরোপীয় দার্শনিকদের মতো এনসাইক্লোপিডিক, যাঁর মূলধন প্রবল যুক্তি, নিজস্ব ভাবনা ও অন্তর্দৃষ্টি। হঠাৎ মনে হবে যেন আঠারো শতক থেকে সমালোচকদের কুলপতি ড. জনসন এসে উপস্থিত হয়েছেন, তাঁর সীমাহীন পড়াশোনা ও ব্যক্তিত্ব নিয়ে। সেই সঙ্গে যুক্ত হয়েছে বাঙালিসুলভ আবেগ, একগুঁয়েমি ও পাণ্ডিত্যশ্লাঘা, যা তাঁকে সম্পূর্ণ পৃথক এক আইডেনটিটি দিয়েছে। বিদ্যা যে বিনয় দেয়, তা তাঁর নিশ্চয়ই ছিল, তাঁর কাছের মানুষেরা তার সন্ধান পেয়েছেন, যেমন তাঁর শিক্ষক মোহিতলালের পুত্র অগ্রগণ্য নীরদচর্চাবিদ মনসিজ মজুমদার, কিন্তু নানা কারণে ক্ষুব্ধ ও তিক্ত মানুষটি সেটিকে সর্বদা নিয়ন্ত্রণ করতে পারেননি।এদিক থেকে সতীর্থ রবীন্দ্রকুমার দাশগুপ্তর সঙ্গে তাঁর প্রধান অমিল।
আসল কথা হল, নিজের মতো করে কথা বলতে এবং প্রয়োজনে চূড়ান্ত বিতর্কিত ও আক্রমণাত্মক হতে তিনি প্রথম থেকেই এক মুহূর্তের জন্যও দ্বিধা করেননি। তা তাঁর স্বাতন্ত্র্য বৃদ্ধি করেছে, বিতর্ক তাঁর রচনার প্রাণ। বর্তমান রচনাগুলি, যেগুলির কয়েকটি তিরিশ বছর বয়সে লেখা, আবার তা প্রমাণ করল।
নীরদচন্দ্র যেন পথভোলা এক দার্শনিক। সক্রেটিসের মতো জ্ঞানের এক অন্তহীন বিতর্কের অগ্নিবলয়ে সতীর্থদের চোখ খুলে দেওয়াই যেন তাঁর লক্ষ্য, জ্ঞানবস্তুকে পৃথিবীর ইতিহাসে প্রোথিত করে। এ এক নতুন নিকোমেকিয়ান এথিকস, বিদ্যাচর্চার অপার আনন্দই যাঁর প্রধান উপজীব্য।আজ থেকে এক শতক আগে স্যাডওয়েল কমিশন বাঙালির নিরাসক্ত সীমাহীন জ্ঞানচর্চা সম্পর্কে যে অপার বিস্ময় প্রকাশ করে, নীরদবাবু সেই ঘরানার অন্যতম শেষ উদাহরণ। ‘বাঙালী জীবনে রমণী’ প্রসঙ্গে তপন রায়চৌধুরী লিখেছেন, “তার বিচিত্র বক্তব্য কাটা হীরের ধারগুলির মতো নানা দিক থেকে আলোক বিচ্ছুরণ করে।...নির্জলা তথ্যভিত্তিক সত্য ইতিহাসের খোঁজে বইটা পড়বেন না, বইটির মূল্য সে হিসেবে নয়।ইতিহাসের সত্য সন্ধান শুধু তথ্য আর যুক্তি ভিত্তিক নয়, কল্পনা এবং intuition-এর উপর প্রতিষ্ঠিত। এখানে ইতিহাস সাহিত্যের সমধর্মী।‘বাঙালী জীবনে রমণী’-তে তথ্য বা যুক্তির অভাব নেই। কিন্তু তার ভিত অনুভূতিময় কল্পনা।” (ভূমিকায় সম্পাদকের উদ্ধৃতি, পৃ. ১৩) এই ‘অনুভূতিময় কল্পনা’ নীরদবাবুকে দিয়েছিল এক অফুরন্ত শক্তি।
আমার সন্দেহ, তাঁর প্রতি সন্দিগ্ধ সম্ভ্রমের সঙ্গে সর্বদা মিশে থেকেছে ভয়। সেই ভয়ও অবশ্য অনেকাংশে নীরদবাবুর নিজের সৃষ্টি। বিশ্বকোষের ওজন কি কম ভীতিপ্রদ? অধিকাংশ সাধারণ বাঙালি পাঠক তাঁর ইংরেজি রচনাগুলি— বিশেষ করে আত্মজীবনী দু’টি এবং ‘দ্য কনটিনেন্ট অফ সারসি’, ‘আ প্যাসেজ টু ইংল্যান্ড’, ‘দ্য স্কলার এক্সট্রাঅরডিনারি’— মন দিয়ে পড়েননি। এবং কোনও কোনও বিষয়ে (যেমন তাঁর অন্ধ ইংরেজপ্রীতি, যাকে বাঙালি কখনও ভাল চোখে দেখেনি) সম্পর্কে দ্রুত উপসংহারে পৌঁছেছেন, যদিও ক্ষেত্রবিশেষে নীরদবাবু যে ভিন্ন মতও অবলম্বন করতে দ্বিধা করেননি তা অনেকেই খেয়াল করেননি। যেমন ‘A Bengali on the Pont des Arts’ (১৯৫৬, From the Archives of a Centenarian), যেখানে ফরাসিদের যে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা আছে— ‘discretion was the keynote’ ইত্যাদি— তা ইংরেজপ্রীতির পাঠক্রমের বাইরে।
নীরদবাবু সম্পর্কে বাঙালি পাঠকের অস্বস্তির আর-একটি কারণ সম্ভবত তাঁর বাংলা লেখা। এক অমসৃণ সাধুভাষায় প্রবল প্রজ্ঞা ও ভীতিজনক পাণ্ডিত্যের পাশে অন্যের প্রতি তাচ্ছিল্য ও অবজ্ঞা দেখে পাঠক সবসময়ই নিজেকে ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র ভেবেছেন, যা বঙ্কিমচন্দ্র, হরপ্রসাদ থেকে রবীন্দ্রকুমার দাশগুপ্ত, অন্নদাশংকর, অম্লান দত্তের ক্ষেত্রে কখনও হয়নি। রবীন্দ্রনাথের সহজ, সাবলীল আন্তর্জাতিকতার সঙ্গে নীরদচন্দ্রের আন্তর্জাতিকতার তুলনা করলে ব্যাপারটা পরিষ্কার হয়। গ্রিক ‘পারেজিয়াস্তের’ (নির্ভীক সত্যবাদী) মতো স্পষ্টভাষিতায় বাঙালির মুখোশ খুলে দিতে তাঁর দ্বিধা ছিল না। তাঁর বাংলা ও ইংরেজি গদ্যের মূলগত পার্থক্য পাঠকমনে নানা সমস্যার সৃষ্টি করেছে। ইংরেজি রচনার অসামান্য প্রসাদগুণের একটি হল তিক্ততাকে খানিকটা আড়াল করে রাখতে পারা। দু’টি ভাষার তরঙ্গদ্রাঘিমা তো আলাদা।
শ্রুত্যানন্দ ডাকুয়া তাঁর ভূমিকায় দু’টি ভাষায় লেখা প্রসঙ্গে নীরদ চৌধুরীর উদ্ধৃতি দিয়েছেন— ‘ভাষা শুধু ভাষা নয়, মানুষের মনের প্রকাশ। দুই ভাষাভাষীর মনের অনৈক্য হয়। উহার ফলে অর্থও ঠিক বোঝা যায় না, ব্যঞ্জনার উপলব্ধি তো হয়ই না। ...আমি ইংরাজীতে লিখি পাশ্চাত্য মনের জন্য; বাঙালীর, এমন কি সমগ্র ভারতীয়ের মনের জন্যও নয়। বাঙালী মন ও পাশ্চাত্য মন এত বিভিন্ন যে, আমি ইংরাজীতে লিখিয়া দেশে আমাকে ভুল বুঝিবার অবকাশ দিয়াছি।’
তাঁর সম্পর্কে শিক্ষিত বাঙালির একটি বড় অংশের প্রবল অনীহার সম্ভবত অন্য একটি কারণ, তিনি ‘আমাদের লোক’ নন, কলকাতা ছেড়ে দীর্ঘদিন দিল্লি ও পরে ইংল্যান্ডবাসী। রবীন্দ্রকুমার দাশগুপ্তের ভাষায়, ‘বিদ্যার বহর দেখাইতে তাঁহার বড় আনন্দ।’ (ভূমিকায় শ্রুত্যানন্দের উদ্ধৃতি, পৃ. ১২) উপরন্তু তিনি বাঙালিকে ‘আত্মঘাতী’ মনে করেন, পূর্বতন ঔপনিবেশিক প্রভুর দেশে বসে তিনি বাঙালিকে ভর্ৎসনা করেন।মনোজ্ঞ সংলাপ তাঁর ধাতে নেই। ১৯৭৩ সালে ‘ইলাসট্রেটেড উইকলি’-তে তাঁর একটি প্রবন্ধের নাম ছিল ‘Envy as Part of our National Character’। তাঁর ভাষায়, ‘আমার সহিত মতের মিল নাই, এই কথা আমি বাঙালি-অবাঙালির মুখে শুনিতে শুনিতে ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছি। তখনই আমি বলি, একমত হইবেন কেন? আমি তো তাহা প্রত্যাশা করি না। আমার কথাটা যদি পড়িয়া আপাতত একটু প্রণিধান করেন তাহা হইলেই যথেষ্ট।’ (শারদীয় বসুমতী, ১৩৭৪; ‘নির্বাচিত প্রবন্ধ’, আনন্দ পাবলিশার্স, ১৯৯৭)।
কিন্তু ‘প্রণিধানযোগ্য’ হওয়ার প্রয়াস সবসময় ছিল কি? বইয়ের প্রথম প্রবন্ধে (সম্পাদক জানাচ্ছেন, ‘প্রবাসী’-তে প্রকাশিত এটি তাঁর প্রথম বাংলা লেখা ‘সর্ব্বহারা’, ১৯২৭; দু’বছর আগে ‘মডার্ন রিভিউ’-তে ভারতচন্দ্র সম্পর্কে তাঁর প্রথম ইংরেজি রচনা প্রকাশিত হয়) ‘অসম্বন্ধ প্রলাপভাষী’ কাজি নজরুলকে তিরিশ বছর বয়সি নীরদচন্দ্র কশাঘাত করেন। তরুণদের প্রতি লাগামছাড়া আক্রমণের এমন উদাহরণ পাওয়া যাচ্ছে প্রথম দিকের সব রচনাতেই। ‘বাংলা সাহিত্য আন্ডারগ্রাজুয়েটদের হাতে পড়িয়াছে।...দুর্ব্বল, ভিত্তিহীন, যুক্তিহীন, অনিয়ন্ত্রিত ভাবাবেগ ছাড়া আর কিছুই পাই নাই।...তরুণ-সঙ্ঘ কাঁদিতে থাকুন। বালানাম্ রোদনম্ বলং।’ বঙ্কিম থেকে রবীন্দ্রনাথ কেউই কোনওদিন এমন ভালবাসাহীন ভাবে (‘স্কুলবয় সাহিত্যিক’, ‘তরুণ সাহিত্যিকদের হাহাকারময় বাণী’) তরুণদের আক্রমণ করেননি। ১৯৬৫ সালে লেখা ‘দ্য কন্টিনেন্ট অফ সার্সি’-তে লিখেছেন, ‘I do not take youthful rebelliousness very seriously…It has no revolutionary significance.’ এ এক অদ্ভুত অযৌক্তিক অশুভ সাহিত্য-পাঠ। বিশ্বসাহিত্যের ইতিহাসে প্রায় প্রতিটি বিপ্লবই তো তরুণদের। ভের্লেনকে লেখা র্যাঁবোর বিখ্যাত উক্তির কথা মনে পড়ে: ‘আমি তরুণ, আমার দিকে বাড়িয়ে দাও হাত’! তরুণ প্রজন্মের সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিকোণের সঙ্গে (ধরা যাক, ‘শেষের কবিতা’-র) নীরদবাবুর নিষ্করুণ মনোভাবের তুলনা করুন।
অর্থাৎ নীরদবাবু যে ‘জীবনব্যাপী দুঃখকষ্টের’ কারণে তিক্ত হয়েছেন, সেই যুক্তি হয়তো সত্যি নয়। এই বই আর-একবার প্রমাণ করল যে, সীমাহীন তিক্ততা প্রথম থেকেই ছিল। ‘শনিবারের চিঠি’-তে প্রকাশিত দ্বিতীয় লেখাটিই (প্রসঙ্গ-কথা ১) বিবেচনা করা যাক। ‘ভাবিয়াছিলাম এবারে বাঙালী Mallarme, Verlain-র [রোমান হরফে বিদেশি নাম লেখা থেকে মনে হয়, তিনি উচ্চারণ নিয়ে সুনিশ্চিত ছিলেন না; ফরাসি ব্যাকরণ ও বানানও সঠিক নয়, হবে pourvu que, Mallarmé, Verlaine] লেখার সহিতও পরিচয় হইবে। হায় আশা!’ বোঝা গেল না, রনে দুমিক (?), রেমি দ্য গুরমঁ, মালার্মে, ভের্লেন না পড়লে হঠাৎ আকাশ ভেঙে পড়বে কেন। মালার্মের তাত্ত্বিক মূল্য কি তিনি অনুধাবন করেছেন? বোদল্যেরের কাব্যগ্রন্থের নাম Fleurs du Mal নয়, Les Fleurs du mal। স্নবারি, ভারসাম্যহীন ক্রোধ ও বিদ্রূপের (‘বাঙালী লেখকদের ইন্দ্রিয়পরতন্ত্রতা furtive, sheepish জাতীয়’) সঙ্গে যুক্ত হয়েছে এমন সুসভ্য উক্তি: ‘আমরা এযুগে মেয়েদের “কম্বিনেশন” অথবা ইজারের এককোণ দেখিয়াই জ্বলিয়া পুড়িয়া মরিতেছি।’
পাঠকের অপরিচিত সাহিত্য থেকে যত্রতত্র নামোল্লেখ যুক্তির সীমা অতিক্রম করে যায়। তাঁর পড়াশোনার পক্ষপাত উনিশ শতকের দিকে, তাতে আপত্তি নেই। কিন্তু বিশ শতকের তৃতীয় দশকের পরিপ্রেক্ষিতে বারবার আনাতোল ফ্রাঁসের উল্লেখ কৌতুকের উদ্রেক করে, কারণ বিশ শতকে কোনও পশ্চিমি বোদ্ধা সেই নাম করবেন না। আমরা লক্ষ করব, নীরদবাবু জিদ, প্রুস্ত, জয়েস, সেলিন, কাম্যু-কাফকাকে চেনেন না, তাঁর সাহিত্যপাঠ বিশ শতকে প্রবেশ করেনি। তাঁর হাতে বুদ্ধদেব বসুর জাদু-লন্ঠন নেই। তিনি শুধু হঠাৎ হঠাৎ পুরনো সিন্দুক থেকে সেকেলে জামার ধুলো ঝাড়েন। স্কুলছাত্রের মতো নাম দিয়ে চমক লাগানোর করুণ উদাহরণ কম নেই। ‘এম এ পড়িবার সময়ে পাঠ্য বিষয়গুলির যত বই আমার ছিল আমার অনেক অধ্যাপকেরও তত বই ছিল না।’ (পৃ. ১৫৭) ‘গ্যাল্স্ওয়ার্দি’ ও হাডসনের উদ্ধৃতি দেন। ‘Johan Bojer, Knut Hamsun, Gorky অথবা Boccaccioর Decameroneর [হবে Decameron] un-expurgated edition কিনিবার জন্য দুই একটা টাকা চাই।’ ফরাসি ক্লাসিক থেকে চয়ন করেন, যা অনেক সময়েই অতি সুপ্রযুক্ত, কিন্তু কোনও রহস্যময় কারণে সেগুলির মানে বলেন না। পূর্ব-নির্ধারিত নিন্দা-প্রশংসা, সীমাহীন বিষোদ্গার ও এইসব অমল হীরকখণ্ড একসঙ্গে মিশে থাকে।
‘শনিবারের চিঠি’-ই কি তবে তাঁর মানসিক গঠনকে তৈরি করে দিয়েছিল? এর উত্তর হল, হ্যাঁ। ‘আমি তো হীন সাহিত্যিক গ্ল্যাডিয়েটর মাত্র।’ (পৃ. ৪৮) ‘মান্দ্রাজী বা মেড়ুয়াবাদী’ বলতে তাঁর বাধে না। ‘শনিবারের চিঠি’-তে যোগদান ও সঙ্গ ত্যাগ নিয়ে তাঁর ‘অক্ষমের ক্ষমতা’ (‘আমার দেবোত্তর সম্পত্তি’) ও ‘দাই হ্যান্ড, গ্রেট অ্যানার্ক’-এর ‘আ লিটরারি ক্যাম্পেন’-এর কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন সম্পাদক। অর্থাৎ রচনার ধমনির মধ্যে একটি সংকট
তৈরি হচ্ছে।
বইয়ের পাতা ওলটাতে ওলটাতে আমরা হঠাৎ দেখি মধ্য-তিরিশের নীরদচন্দ্র এক বিস্তৃত আকাশপথে হাঁটতে শুরু করেছেন। ‘প্রবাসী’ (১৩৩৭ চৈত্র, ১৯৩১ মার্চ)-র ‘বাংলাদেশ ও ভারতবর্ষ’ নিবন্ধে হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর ‘আত্মবিস্মৃত জাতি’ কথাটির সূত্র ধরে ‘আত্মঘাতী বাঙালী’-র বিতর্কের প্রাথমিক ঐতিহাসিক ও সমাজতাত্ত্বিক কাঠামোটি রচিত হয়। (পৃ. ৪৯-৬৪) এটি বাঙালির জাতিভেদ ও জাতীয়তাবোধ সম্পর্কে তাঁর মতামতকে বোঝার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ‘বাঙালীত্বের স্বরূপ’ (পৃ. ৮০-৯০) আরও একধাপ এগিয়ে এক গভীর আত্মবীক্ষার সামনে আমাদের দাঁড় করায়। আমরা অনুভব করি, এইবার তিনি গাণ্ডিব তুলে নিতে চলেছেন। এর কিছু পরেই আসবে ১৯৩১-এর জুলাই মাসে ‘প্রবাসী’-তে প্রকাশিত তাঁর অন্যতম শ্রেষ্ঠ রচনা দশম শতাব্দ পর্যন্ত মুসলমান চিত্রকলার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস ‘ইস্লামের প্রথম যুগের চিত্রকলা’ (পৃ. ৬৭-৭৯), যা আগে কেন গ্রন্থিত হয়নি বোঝা শক্ত। শুধু এই একটি প্রবন্ধের জন্য বইটি স্বর্ণোজ্জ্বল হয়ে থাকবে।
ক্রমশ আসে ‘বাংলা সামাজিক উপন্যাসের উপক্রমণিকা—নক্সা ও ব্যঙ্গচিত্র’ (পৃ. ৯১-১০৫), ‘যুদ্ধের “নূতন” টেকনিক’ (পৃ. ১১৩-১২১), ‘বর্তমান যুদ্ধে নৌবল’ (পৃ. ১৩৩-১৪৬)-এর মতো স্বতন্ত্র চিন্তার প্রবন্ধ। এখানে অহমিকা নেই, আছে অন্ধকার ভেদ করে এক নিবিষ্ট অভিযাত্রা, যা আবার তিনিই পারেন। এই বইয়ে সম্পাদক যুক্ত করেছেন ‘তিনটি নিবন্ধ’ নামে আর-একটি অনুধাবন: ‘ইংরেজীতে সাহিত্য প্রচেষ্টা’ (১৯৭৭), ‘ভারতবাসীর ব্রিটেনে বসতি’ (১৯৭৮) এবং ‘বিলাতের খবরের কাগজ’ (১৯৭৮)।
তাঁর সমস্যাগুলিও যেমন জানব, তেমনই আমরা অবাক হব এই বইয়ের দ্বিতীয়ার্ধের অনেক রচনার বিস্তৃতি, ঘনত্ব ও দার্ঢ্যে, যেন এই ছোট ছোট চুম্বক হিমের রাতে প্রদীপ জ্বালবে বলে আমরা কত যুগ হাপিত্যেশ করে বসে আছি।
সূত্রঃ বইয়ের দেশ, জুলাই - সেপ্টেম্বর ২০১৮
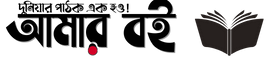


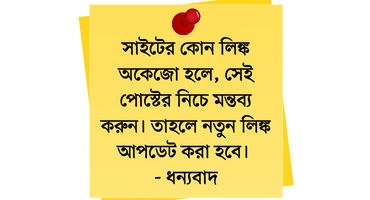







![[ছোট্টগল্প] সেক্সবয় - তসলিমা নাসরিন](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEizCNalHzbcL_TRO47frupqVrYhkJmfl_OaBixQzVrIC9gZtXtGiggWI52u_yo8X-cwdAfVwBlwyTJSaFM9F2lp5Qn4Kq0vWMi5DWKhVvP7UN-MkOFsO-kl7tIV3Xu874EhlsSm4r8fbNgR/w72-h72-p-k-no-nu/sboyt.png)








