 |
| বঙ্গবন্ধুর পরিবার |
আব্বার বাড়ি বঙ্গবন্ধুর বন্দিজীবন
সেমন্তী ঘোষ
“৮ই ফেব্রুয়ারি, দুই বৎসরের ছেলেটা এসে বলে ‘আব্বা বালি চলো।' কি উত্তর ওকে আমি দিব। ওকে ভোলাতে চেষ্টা করলাম, ও তো বোঝে না আমি কারাবন্দি। ওকে বললাম, ‘তোমার বাড়ি তুমি যাও। আমি আমার বাড়ি থাকি। আবার আমাকে দেখতে এসো।” ও কি বুঝতে চায়। কি করে নিয়ে যাবে এই ছোট্ট ছেলেটা, ওর দুর্বল হাত দিয়ে মুক্ত করে এই পাষাণ প্রাচীর থেকে!
দুঃখ আমার লেগেছে। শত হলেও আমি তো মানুষ, আর ওর জন্মদাতা। অন্য ছেলেমেয়েরা বুঝতে শিখেছে। কিন্তু রাসেল এখনও বুঝতে শিখে নাই। তাই মাঝে মাঝে আমাকে নিয়ে যেতে চায় বাড়িতে।”
শিশুপুত্রের অবুঝ আবদার ‘বাড়ি চলো” শুনে জেলের মধ্যে বাবার প্রাণ কেঁদে উঠেছিল যে আট ফেব্রুয়ারি, সে ছিল ১৯৬৬ সালের কথা। সেই বছর শেখ মুজিবুর রহমান আরও এক বার— আবারও এক বার— বন্দি হয়েছিলেন তাঁর দেশের পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকদের হাতে। সে বার তিনি কারাগারে থাকবেন টানা তিন বছর— ১৯৬৬-র ফেব্রুয়ারি থেকে ১৯৬৯-এর এপ্রিল মাস পর্যন্ত, ‘আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা' নামে খ্যাত সেই ঘটনা।
এর আগেও অনেক বার জেলে থেকেছেন রাসেলের বাবা, অনেক বার। ১৯৪৮ সালে। ১৯৫২, ১৯৫৪, ১৯৫৮, ১৯৬২, ১৯৬৪, ১৯৬৫ সালে। ১৯৬৬ সালের গোড়ায় পাকিস্তানি শাসকদের ভয়-পাইয়ে- দেওয়া তাঁর ‘ছয় দফা দাবি' পেশের পর তিনি পর পর আট বার গ্রেফতার হতে থাকেন চট্টগ্রাম, যশোহর, ময়মনসিংহ, সিলেট, খুলনা, পাবনা ও অবশ্যই ঢাকা-সহ বিভিন্ন শহরে। যখনই তিনি জনসভায় বক্তৃতা করতে ওঠেন, তখনই তাঁকে বন্দি করে জেলে পোরে পাকিস্তান সরকার। অবশেষে '৬৬ থেকে ’৬৯, টানা তিন বছরের সেই কারাবাস। তত দিনে অন্য ছেলেমেয়েরা মেনে নিতে শিখেছে কঠোর বাস্তব। মা রেণুর সঙ্গে আব্বাকে দেখতে আসে তারা শুকনো বিষণ্ন মুখে, কামাল- হাসিনা-জামাল-রেহানা। কেবল শিশুপুত্র রাসেলই তখনও শুধু বার বার তাঁকে বাড়ি নিয়ে যেতে চায়। তাও প্রথম দিকে। তার পর আস্তে আস্তে সে-ও মেনে নেয় যে তার আব্বা জেলেই থাকেন, জেলকে সে নাম দিয়ে দেয় ‘আব্বার বাড়ি'। বাবা মুজিব লক্ষ করেন শৈশবের সেই আহত বোঝাপড়া, আর জেলকুঠুরিতে বসে ডায়েরিতে লেখেন, “রাসেলও বুঝতে আরম্ভ করেছে, এখন আর আমাকে নিয়ে যেতে চায় না।” আরও কিছু দিন কেটে গেলে তিনি ডায়েরিতে লেখেন— তাঁকে জেলে দেখতে এসে রাসেল ওর মাকে গলা জড়িয়ে কেঁদে ‘আব্বা’ বলে ডাকছিল। “আমি জিজ্ঞাসা করলাম, ‘ব্যাপার কি?’ ওর মা বলল, ‘বাড়িতে ‘আব্বা’ ‘আব্বা” করে কাঁদে, তাই আমি বলেছি আমাকেই ‘আব্বা” বলে ডাকতে।”
রাসেল বুঝতে পারেনি, জেলকে সে যে ‘আব্বার বাড়ি’ নাম দিয়েছিল, তার মধ্যে কত বড় একটা ঐতিহাসিক সত্য লুকিয়ে আছে। জেল তো সত্যিই ঘরবাড়ি বাবা শেখ মুজিবের কাছে। তাঁর পঞ্চান্ন বছরের জীবনে তেরো বছরেরও বেশি কেটে গিয়েছে কারাগারে— হিসেব বলছে ৪৬৮২টি দিন। আর যদি আমরা মনে রাখি যে, ১৯৪৭ সালে পাকিস্তানের জন্ম ও আড়াই দশক পরে মুক্তিযুদ্ধ-শেষে ১৯৭২ সালে পূর্ব পাকিস্তানের বাংলাদেশ রাষ্ট্র হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হওয়া, এই সময়েই তো কেটেছে শেখ মুজিবের জীবনের প্রধান রাজনৈতিক পর্ব, এই সময়েই তো তিনি হয়ে উঠেছেন প্রবাদপ্রতিম নেতা! অবাক হয়ে দেখতে হয়, সেই পঁচিশ বছরের অর্ধাংশই কিন্তু মুজিব জেলে ছিলেন। জেল-গরাদের ও দিকে থেকেই পূর্ব পাকিস্তানের প্রথম, প্রধান, প্রবল নেতা হিসেবে বিকশিত ও প্রকাশিত হয়ে উঠেছেন তিনি— অনেক ইতিহাসবিদই যাঁকে পরে বলবেন, সর্বকালের সেরা বাঙালি রাজনৈতিক নেতাদের এক জন।
অথচ দেশভাগের সময়ে অবিভক্ত ভারতের অবিভক্ত বাংলায় মুজিব কিন্তু কোনও বড় মাপের নেতা ছিলেন না। সেই সময়ে তিনি ছিলেন হোসেন শহিদ সুরাবর্দির নেতৃত্বে বাংলার মুসলিম লীগের তরুণ ব্রিগেডের উৎসাহী নেতা, এইটুকুই। ১৯৪৭ সালের পরই তাঁর সত্যিকারের নেতা-জীবনের শুরু। ১৯৪৮ সালের পূর্ব পাকিস্তানে বাংলা ভাষার দাবিতে সরব হয়ে ওঠা। পুব বাংলার নানা জেলায় এখানে ওখানে ছাত্র-বিক্ষোভের পুরোভাগে নেতৃত্ব দিতে দিতে পাকিস্তান সরকারের চক্ষুশূল হয়ে ওঠা। আর তার ফলে— সেই ১৯৪৮ সাল থেকেই বার বার গ্রেফতার এবং কারাবাস— ১৯৭২-এর জানুয়ারি পর্যন্ত। কত বার রাজবন্দি থেকেছেন, সশ্রম কারাদণ্ড পেয়েছেন। বার বার একাকী (‘সলিটারি’) সেলে পোরা হয়েছে তাঁকে, যাতে কোনও মানুষের মুখ না দেখে দেখে মন ভেঙে যায়। এই সব কাহিনি পড়তে পড়তে আর আরও অনেক বিশ্বখ্যাত নেতার কথা মনে পড়ে যায়— মহাত্মা গাঁধী, নেতাজি সুভাষচন্দ্র কিংবা নেলসন ম্যান্ডেলা। বন্দি নেতারা কী ভাবে তাঁদের জাতির ভাগ্যরেখা পাল্টে দিতে পারেন, এঁরাই উদাহরণ।
বাঙালি নেতা শেখ মুজিব এমনই এক অসামান্য চরিত্র। এতগুলো বছর কারাকুঠুরিতে থেকে তিনি জনবিচ্ছিন্ন হয়েও যেতে পারতেন। মনোবল ভেঙে যেতেও পারত। কিন্তু ঘটল অন্য রকম। প্রতিটি জেলবাসের সঙ্গে সঙ্গে তাঁর নেতৃত্বগুণ যেন আরও শাণিত হয়ে উঠল, আরও প্রজ্বলিত হল। মানুষের সঙ্গে তাঁর সংযোগ আরও সজোর হল। বাংলা ও বাঙালি বিষয়ে বোধ ও বিশ্বাস আরও দৃঢ়প্রোথিত হল। কোথায় তিনি যেতে চান, দেশবাসীকে কোন লক্ষ্যে পৌঁছে দিতে চান - দিশাটি স্পষ্ট জ্বলে উঠল। এবং, সবচেয়ে বড় কথা, মহাপ্রতাপশালী পাকিস্তানি শাসকের সঙ্গে টক্কর দিতে হলে কোন পথে কখন কী ভাবে এগোতে হবে, সেই কৌশল-চাতুর্য কলায় কলায় বিকশিত হতে শুরু করল। এই বছর তাঁর জন্মশতবর্ষ পূর্ণ হল। নেতা মুজিবের নেতৃত্বের অনেক আলাপ-আলোচনা, অনেক রকম ঘটনার মধ্যে হারিয়ে গেল না তো এই তথ্যটুকু যে, তিনি পুব বাংলার বাঙালিকে একটি নতুন দেশের জন্য তৈরি করতে যে পঁচিশ বছর সময় পেয়েছিলেন, তার মধ্যে অর্ধেক সময় কিন্তু তিনি আসলে পানই নি, জেলকুঠুরিতে দিবস-রজনী, মাসের পর মাস কাটাচ্ছিলেন?
পাকিস্তানি শাসকরা বোধ হয় নতুন দেশ শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই বিপদ গণেছিলেন তাঁকে দেখে। ১৯৪৮ সালের গোড়াতেই পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র লীগ কর্মীরা যখন জেলায় ও মহকুমায় ‘রাষ্ট্রভাষা বাংলা সংগ্রাম পরিষদ' গঠন করতে শুরু করেছে, ১১ মার্চ বাংলা ভাষা দাবি দিবস ঘোষণা করা হয়েছে— মুজিবের আত্মকথায় পড়ি, “জেলায় জেলায় আমরা বের হয়ে পড়লাম। আমি ফরিদপুর, যশোর হয়ে দৌলতপুর, খুলনা, বরিশালে সভা করে ঢাকা ফিরে এলাম।” সে দিন ভোর থেকেই শুরু হল ছাত্রদের পিকেটিং, হরতাল। পুলিশ লাঠিচার্জ করতে শুরু করল, অনেককে ধরে নিয়ে জিপে তুলল। “আমাদের প্রায় সত্তর-পঁচাত্তর জনকে বেঁধে নিয়ে জেলে পাঠিয়ে দিল সন্ধ্যার সময়। আন্দোলন দানা বেধে উঠল। ঢাকার জনগণের সমর্থনও আমরা পেলাম।” জেলে বসেই শুনলেন মুজিব বাইরে ক্ষুব্ধ মিছিলের উত্তাল স্লোগান— ‘বন্দি ভাইদের মুক্তি চাই’, ‘পুলিশি জুলুম চলবে না’, ‘রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই'। জেলের উঠোন থেকে দেখলেন, পাশের স্কুলবাড়ির ছাদে উঠে ছোট্ট ছোট্ট মেয়েরা ইশকুলের পোশাক পরে স্লোগান দিচ্ছে, একটানা, সকাল দশটা থেকে বিকেল চারটে। গর্বে আর আশায় ভরে উঠত নতুন ছাত্রনেতার বুক— “আমাদের বোনেরা বেরিয়ে এসেছে, আর বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা না করে পারবে না।”
এই এক অস্ত্রের সন্ধান পেলেন পুব বাংলার ভাবী ‘জাতীয় নেতা”। এমন এক অস্ত্র, যাতে রাষ্ট্রীয় প্রতিপক্ষকে ঘায়েল করতে জনতা নিজেই এগিয়ে আসতে পারে, কোনও শক্তপোক্ত নেতার উপস্থিতি ছাড়াই। সময়মতো যদি নেতারা গ্রেফতার হন, জেলে প্রবেশ করেন, তাঁদের বন্দিদশা অনেক সময়ই আন্দোলনকে থামায় না, তার শক্তিক্ষয় করে না, বরং আন্দোলন তার শক্তি অর্জন করে— বুঝে গেলেন মুজিব। এর পর বার বার তিনি এই কৌশল কাজে লাগাবেন। ১৯৪৯ সালের মার্চে আবার— ঢাকার বিক্ষোভকারী ছাত্রদের একেবারে সামনে এসে দাঁড়ালেন তিনি। “আন্দোলন ঝিমিয়ে আসছিল, একে চাঙ্গা করতে হলে আমার গ্রেফতার হওয়া দরকার।” একটু পরেই জেলা ম্যাজিস্ট্রেট এসে তাঁকে গ্রেফতারের হুকুম দিলেন। ফল? পর দিন থেকে পূর্ণ ধর্মঘট, ছাত্ররা দলে দলে গ্রেফতার, দূর পশ্চিমে বসে প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলি খানের ঘুম ছুটে গেল পুব বাংলার কাণ্ড দেখে। দমনপীড়ন দ্রুত বাড়তে লাগল। মুজিবরাও শক্ত হতে লাগলেন। “যে পাকিস্তানের স্বপ্ন দেখেছিলাম, এখন দেখি তার উল্টা হয়েছে। এর একটা পরিবর্তন করা দরকার।”
পরিবর্তনে পৌঁছনো কি সহজ? অনেক বছর পর, এক ভয়ঙ্কর বছরের কালান্তক দিন— ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ, ঠিক এই একই কথা ভাবছিলেন মুজিব। পূর্ববঙ্গের দিকে দিকে তখন মুক্তিযুদ্ধের দামামা, ৭ মার্চ মুজিবের অসামান্য উদ্দীপনাময় ভাষণে তেতে উঠেছে গোটা দেশ, আর নয় আর নয়, এ বার ‘জয় বাংলা’, ‘বাংলার জয়’ চাই-ই চাই। পাকিস্তানি সেনারা মুজিবকে ধরতে আসামাত্র তিনি ধরা দিলেন। বন্দি মুজিবকে চালান করে দেওয়া হল পশ্চিম পাকিস্তানে, সুদূর রাওয়ালপিন্ডির কাছে, সিন্ধু নদের তীরে— মিয়াঁওয়ালি শহরের কারাগারে। গোটা মুক্তিযুদ্ধ পর্বটা তিনি জেলবন্দি। আবার খোলা আকাশ দেখবেন ১৯৭২ সালের জানুয়ারিতে। নতুন দেশের হাল ধরবেন, সমগ্র পৃথিবী তাঁকে জানবে বাংলাদেশের জনক হিসেবে। পরে যখন তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হবে, কেন অত সহজে ধরা দিলেন তিনি, কেন? তিনি উত্তর দেবেন, তিনি সে দিন বুঝেছিলেন উন্মত্ত পাকিস্তানি শাসক তখন রক্তখাদক হয়ে উঠেছে— তাঁকে না ধরতে পারলে আরও অনেক মানুষের প্রাণ যেতে পারে। আর তা ছাড়া— এই তো তাঁর সেই অমোঘ অস্ত্র— “আমার সুদৃঢ় বিশ্বাস আমি পাকিস্তানিদের হাতে বন্দি থাকায় আমার দুঃখী বাঙালিদের মধ্যে দুশ্চিন্তা, উদ্বেগ যেমন বেড়েছে, তেমনি মানুষ আমার অনুপস্থিতিতে আমার একটা বিশাল প্রতীক মনে মনে তৈরি করে নিয়েছে। এটা ছিল মুক্তিযুদ্ধের খুব বড় একটা শক্তি। আমি প্রবাসী সরকারে থাকলে শুধু প্রমাণ সাইজের মুজিবই থাকতাম। ওদের হাতে বন্দি থাকায় আমি এক মহাশক্তিধর, বাংলাদেশের সকল মানুষের প্রাণপ্রিয় নেতার স্থান পাই। মানুষ আমার নাম নিয়ে হেলায় হেসে প্রাণ বিসর্জন দিয়েছে।...ওরা যদি আমাকে মেরে ফেলত, তা হলে আমি আরও বড় অমোঘ প্রতীকে পরিণত হতাম। বাংলার মানুষ আরও লড়াকু হয়ে যুদ্ধ করত।”
সাধারণ মানুষে হেলায় হেসে প্রাণ বিসর্জন না দিলে পূর্ব পাকিস্তান কখনও কোনও মতে পশ্চিম পাকিস্তানের কবল থেকে মুক্ত হয়ে বাংলাদেশ নামে নবজন্ম নিতে পারত না। অনেক সংগ্রাম করে, অনেক বিক্ষোভে সকলের সামনে দাঁড়িয়ে নেতৃত্ব দিতে দিতে মুজিব জেনে গিয়েছিলেন, তাঁর থাকার মতো তাঁর না-থাকাটাও মুক্তিকামী বাঙালির কাছে কত বড় অনুপ্রেরণা হতে পারে। এই স্বচ্ছ দৃষ্টি, জোরালো বিশ্বাস— প্রবাদসম নেতা করে তুলেছিল তাঁকে, ঐতিহাসিক সাফল্য এনে দিয়েছিল।
জেলে বসে নিয়মিত খবর রাখতেন বাইরের রাজনীতির, এমনকী ছোটখাটো ঘটনা বা সংঘর্ষেরও। রাজবন্দিদের মুক্তির দাবিতে কী ভাবে জোরালো হয়ে উঠছে আওয়ামী লীগ কর্মীদের রাজনৈতিক কর্মসূচি, কী ভাবে কোথায় কোথায় কাদের নেতৃত্বে তাঁর ‘ছয় দফা’ দাবির পক্ষে ধর্মঘট পালন করছে তারা, বিক্ষুব্ধ সাধারণ মানুষকে চালনা করছে। এবং চার দিকে কী ভাবে তার জবাবে চলছে ব্যাপক ধরপাকড়, তল্লাশি। যত বেপরোয়া হচ্ছে পাকিস্তানি শাসকরা, ততই আরও বেশি করে ‘নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনে' আস্থা রেখে এগোতে বলছেন বন্দি নেতা, বিবৃতিতে সই করছেন, বার্তা দিচ্ছেন জেল থেকেই। “শত অত্যাচার ও নির্যাতনেও কর্মীরা ভেঙে পড়ে নাই, আন্দোলন চালাইয়া চলেছে। নিশ্চয় আদায় হবে জনগণের দাবি।”
তার সঙ্গে সঙ্গে, বাইরের এই বিস্ফোরণে যোগ দিতে পারছেন না বলে ছটফট করছেন জেলের ভিতরে বসে— “কি হবে? কি হতেছে? দেশকে এরা কোথায় নিয়ে যাবে, নানা ভাবনায় মনটা আমার অস্থির হয়ে রয়েছে। এমনি ভাবে দিন শেষ হয়ে আসছে। আমরা জেলে আছি, তবুও কর্মীরা, ছাত্ররা ও শ্রমিকরা যে আন্দোলন চালাইয়া যাইতেছে, তাদের জন্য ভালবাসা দেওয়া ছাড়া এখন আর কিছুই করার নাই।” না, আরও একটা কাজ তাঁর করার ছিল। এক দিনও বাদ দেননি সেই কাজে। সেটা হল, মানুষের সঙ্গে যোগ রেখে চলা। যারা ভিতরে আসছে, তাদের সঙ্গে তো বটেই। যারা ভিতরেই থাকে, পুরনো বন্দি, কিংবা জেলের রক্ষী, তাদের সঙ্গেও। সাধারণ মানুষের সঙ্গে কথা বলা, তাদের সুখদুঃখের খবর নেওয়া- এ ছিল তাঁর সর্বক্ষণের কাজ, প্রতিদিনের ব্রত। প্রবাদের নেতা তো কেবল রাজনীতির কৌশল দিয়ে তৈরি হন না, হন সম্পর্কের জাদু দিয়ে। পঞ্চাশের দশকে, ষাটের দশকে তাঁর জেল বসবাসের দিনরাত ভরে থাকত সেই জাদুতে।
নতুন বন্দি এসেছে জেলে, একসঙ্গে বিরাশি জন শ্রমিক। তারা “এক কাপড়ে এসেছে”, তাদের “গামছা নাই, কাপড় নাই, কোনও জামা নাই। আমি তাড়াতাড়ি কিছু কাপড়চোপড় পাঠাইয়া দিলাম যাতে আপাতত চলতে পারে।” সঙ্গে চলল মানসিক শুশ্রূষাও, যে নেতা জামিনবিহীন একাকী সেলে আটক আছেন মাসের পর দিন, তিনিই আবার নতুন আসা তরুণ ছেলেদের আশ্বাস দিচ্ছেন— “চিন্তা করিও না, জামিনের চেষ্টা করতে হবে।” ছেলেরাও তাঁকে ভুলতে পারত না। কিছু দিন পর, তিনি দেখেন, “কয়েক জন ছোট ছোট বালক জামিন পেয়ে বাইরে যেতেছে। খুব তাড়াতাড়ি হাঁটছে, যেন যেতে পারলেই বাঁচে। থাকতে আর চায় না, এই পাষাণ-কারার ভিতরে। আমার কাছে এসে সকলে থেমে গেল। বলল— আমরা চললাম স্যার, আপনাকে বাইরে দেওয়ার জন্য আবার আন্দোলন করব।— ওদের দিকে আমি চেয়ে রইলাম। ওদের কথা শুনে আনন্দে আমার বুক ভরে গেল। মনে হল, এটা তো কারাগার নয়, শান্তির নীড়। মনে হল, পারব! বহু দিন জেল খাটতে পারব! এরাও যখন এগিয়ে এসেছে মুক্তির আন্দোলন কে আর রুখতে পারে?”
কারাগারও ‘শান্তির নীড়' হয়ে ওঠে, কেননা মানুষের সঙ্গে তাঁর সংযোগ একই রকম গভীর, হয়তো আরও বেশি গভীর। কত অসামান্য গল্প তাঁর কারাগারের রোজনামচা বইয়ের পাতায় পাতায়, এখানে সে সব বলার অবকাশ কই! '৬৬-’৬৭ সালে জেলে বসে মুজিব যে ডায়েরি লিখতেন, যত্ন করে তা রেখে দিতেন তাঁর স্ত্রী রেণু— হয়তো মনে মনে জানতেন, কত মূল্যবান দলিল তৈরি হয়ে উঠছে লোকচক্ষুর অন্তরালে, একাকী সেলের অন্ধকারে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা, বাবার আদরের হাচিনা বা হাচু, আর তাঁর বোন রেহানার উদ্যোগে সম্প্রতিকালে প্রকাশিত হয়েছে জেলের কিছু ডায়েরি-র সংকলন এই বই। অবশ্য এ ছাড়াও জেলবাসের কিছু স্মৃতি রয়ে গিয়েছে মুজিবের অসমাপ্ত আত্মজীবনী বইয়ে। ১৯৪৮ থেকে ১৯৫২ সালের একাধিক বন্দিত্ব-কালের কথা সেখানে পড়েছি আমরা। কিছু বর্ণনা, কিছু তথ্য আবার পেয়েছি আমরা অন্যদের স্মৃতিচারণ থেকে, যাঁরা মুজিবের সঙ্গে কাজ করেছেন, একসঙ্গে বন্দি থেকেছেন, তাঁদের থেকে।
এই যেমন, মাত্র কয়েক বছর আগে, ২০১৫ সালে, একটি গুরুত্বপূর্ণ দিনের ঘটনা আমরা জানতে পেরেছি এক অবসরপ্রাপ্ত পাকিস্তানি পুলিশ অফিসারের কাছ থেকে। নাম তাঁর রাজা আনার খান। পাকিস্তানি টেলিভিশনে তিনি জানান, ১৯৭১ সালে তাঁর উপর দায়িত্ব ছিল পূর্ব পাকিস্তানের বিপজ্জনক নেতা এবং কল্পিত নতুন দেশ ‘বাংলাদেশ’- এর ঘোষিত প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবুর রহমানের উপর নজরদারি করা। নজরদারি নিপুণ করার জন্য তাঁকেও বন্দি সাজিয়ে মুজিবের পাশের সেল-এ রাখা হয়েছিল! ’৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর যখন খবর এল, পূর্ব বাংলায় পাকিস্তানি সেনা আত্মসমর্পণ করেছে, বাংলাদেশ-এর জন্মকে আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি দিয়েছে ভারত, সেই সময় কী ঘটল তাঁর বন্দির জেলে? ১৬ তারিখ রাতের অন্ধকারে করিডর দিয়ে হেঁটে এলেন পাকিস্তানের সিনিয়র পুলিশ অফিসার খোজা তুফাইল, বঙ্গবন্ধুর সেল-এ গিয়ে তাঁকে বার করে আনলেন। সকলে ধরেই নিল, মুজিবকে ফাঁসি দেওয়ার জন্য নিয়ে যাওয়া হচ্ছে, কেননা সকলেই জানত, মুজিবও— বাইরে খোঁড়া হয়ে গিয়েছে তাঁর কবর! প্রত্যক্ষদর্শী আনার খান মনে করতে পারেন, কত শান্ত গলায় মুজিব জানতে চাইলেন, তাঁকে কি তা হলে ফাঁসির জন্যই নিয়ে যাওয়া হচ্ছে? তুফাইলের ছোট্ট উত্তর— ‘ফলো মি’। না, ফাঁসি নয়, অন্যত্র গৃহবন্দি করা হল তাঁকে। কিছু দিন পরে এল পাকিস্তানের নতুন প্রধানমন্ত্রী জুলফিকার আলি ভুট্টোর নির্দেশ, মুজিবকে বলা হবে না যে বাংলাদেশ জন্ম নিয়েছে ইতিমধ্যেই, তবে তাঁকে পাঠিয়ে দিতে হবে তাঁর নিজের দেশে — ৫ জানুয়ারি, ১৯৭২।
আবেগদীপ্ত মুজিব যে আবেগের বশেই শান্ত হয়ে থাকতে পারতেন কতটা— এই কাহিনি তার প্রমাণ। বাস্তবিক, বলতেই হয়, এই সব আলোচনা, বর্ণনা, ডায়েরি, চিঠি— সব মিলিয়ে যে মানুষটি তৈরি হয়ে ওঠেন, কেবল বাইরের রাজনৈতিক বক্তৃতা আর সরকারি নথিপত্রের দলিলে তাঁকে পুরোটা পাওয়া যায় না। ঠিক যেমন নেলসন ম্যান্ডেলার পুরো পরিচয় পাওয়া যায় না তাঁর জেল থেকে লেখা চিঠিপত্র ও ডায়েরির সংকলন প্রিজন লেটার্স না পড়লে। সত্যিই, ম্যান্ডেলার সঙ্গে মুজিবের অনেক মিল, দু'জনেই ইতিহাসে নাম খোদাই করে যাওয়া অসামান্য জননেতা, দু'জনেই তাঁদের দেশবাসীর কাছে দেশের মূর্ত প্রতীক হয়ে উঠেছেন, দু'জনেই নিজেদের দেশের মুক্তির লড়াইকে আক্ষরিক অর্থে নিজেদের জীবনের মধ্য দিয়ে যাপন করেছেন, ধারণ করেছেন। কিন্তু তাঁদের লেখা— বিশেষত জেলে বসে তাঁদের লেখালেখি পড়তে গেলে একটা বিষয় পরিষ্কার, দু'জনের একটা বিরাট অমিলও রয়েছে। কী সেই অমিল?
নেলসন ম্যান্ডেলা চিরকালের বিশ্ববরেণ্য নেতাদের অন্যতম, কিন্তু তবু তাঁকে খুব বড় বাগ্মী নেতা বলা যায় না। যদিও তাঁর যে কোনও সভায় মানুষে মানুষে তিলধারণের জায়গা থাকত না— প্রত্যক্ষদর্শীদের মতে, মঞ্চে তাঁর আবির্ভাবের সময়ে যে কান-ফাটানো করতালি শোনা যেত, কথা শেষ করে মঞ্চ থেকে বেরিয়ে যাওয়ার সময় করতালি পড়ত তার চেয়ে অনেকটাই কম। তিনি খুব আবেগমথিত কথা বলতে পারতেন না, হয়তো বলতে চাইতেন না, তাঁর কথা ছিল বেশ ‘প্র্যাকটিকাল', সোজাসুজি। নিষ্পেষিত মানুষের কাছে সে কথার দাম আকাশ-ছোঁওয়া হলেও সে সব শুনে যে শ্রোতারা বিহ্বল হয়ে পড়তেন, এমনটা বলা যাবে না। অথচ তিনি যখন লিখতেন কারাগারের নিভৃতিতে বসে, তাঁর হৃদয়ের আগল ভেঙে যেন বেরিয়ে আসত আবেগ, তিনি মানুষটি তাঁর লিখিত লাইনগুলির শব্দে শব্দে অক্ষরে অক্ষরে জড়িয়ে যেতেন। বক্তা ম্যান্ডেলা আর লেখক ম্যান্ডেলা প্রায় দু'জন আলাদা মানুষ আর মুজিব? কথার জাদুকর বাঙালি নেতার কথায় কিংবা লেখায় জাদু যেন একই রকম প্রবল। সাদামাটা ঘরোয়া ভাষায় আন্তরিক সুরে ধ্বনিত হত তাঁর প্রবল আহ্বান, তাঁর গভীর বিশ্বাস। যাঁরা শেখ মুজিবের ভাষণ শুনেছেন স্বকর্ণে, মনে করেছেন অমন করে বাঙালিকে আর কোনও বাংলার নেতা উদ্বুদ্ধ করে তুলতে পারেননি কখনও। তাঁর লেখার মধ্যেও সেই একই সুর। কোনও সাজানো-গোছানো ভাব নেই, কোনও বড় কথা নেই, কোনও ছোট মাপের চিন্তাও নেই। একটি সংবেদনশীল মন, পরতে পরতে বাঙালি, কখনও যেন-বা একটু বেশিই সরল, বেশিই সহজ। কয়েক সহস্র মানুষের সামনে যে উদাত্ত স্বরে তিনি শপথ নেন “আমাদের কেউ দাবায়ে রাখতে পারবে না”, ওই একই স্বর ধাক্কা দিয়ে যায় কারাগারের রোজনামচায়, জেলের “কর্তারা কত কিছুই তো বন্ধ করে দেন যাতে কারাগারের রাজনৈতিক বন্দিরা কষ্ট পায় এবং আদর্শচ্যুত হয়ে যায়। ভুল করেছেন [তাঁরা], এরা ভেঙে যেতে পারে, কিন্তু বাঁকা হবে না। নীতির জন্য, আদর্শের জন্য, দেশের মানুষের জন্য যারা ছেলেমেয়ে সংসার ত্যাগ করে কারাগারে থাকতে পারে, যে কোনও কষ্ট স্বীকার করার জন্য তারা তো প্রস্তুত হয়েই এসেছে।” সোজা তিরের মতো সাধারণ মানুষের মনের মধ্যে ঢুকে যেতে পারত তাঁর কথা— কী মুখের ভাষায়, কী লেখার ভাষায়— কোনও প্যাঁচ বা জট থাকে না তাতে।
সোজা করে ভাবতেন মুজিব, দেশের কথা, দেশবাসীর কথা। হয়তো একটু বেশিই সোজা-সরল করে ভাবতেন— সত্যিই তো রাজনীতি বস্তুটা অত সোজা-সরল কিংবা প্যাঁচবিহীন নয়! কত রকম স্বার্থ সেখানে, কত রকম সংঘাত। জেলের মুজিব কিন্তু বাংলা ও বাঙালিকে স্বপ্ন-বপন করে গিয়েছেন সব সময়, সেই স্বপ্নই তাঁকে চলমান রেখেছে, হাজার বাধাতেও নুয়ে পড়তে দেয়নি। সেটা বুঝেও বলতেই হয়, তাঁর মুখের কথার মতোই লেখার কথার সারল্যও আমাদের মনে একটা অদ্ভুত বিষাদ তৈরি করে। জেলে বসে তিনি ভাবতেন, “বাঙালি জাতটা এত নিরীহ, না খেয়ে মরে যায়, কিন্তু কেড়ে খেতে আজও শিখে নাই। ভবিষ্যতে শিখবে এমন আশা করাও ভুল। চুপ করে শুয়ে ভাবতে লাগলাম গ্রামের কথা, বস্তির কথা। গ্রামে গ্রামে আনন্দ ছিল, গানবাজনা ছিল, জেয়াফত হত, লাঠিখেলা হত, মিলাদ-মাহফিল হত। আজ আর গ্রামের কিছুই নাই।... অনেকক্ষণ শুয়ে শুয়ে ছোটবেলার কত কাহিনীই না মনে পড়ল। আমি তো গ্রামেরই ছেলে। গ্রামকে আমি ভালবাসি।”
এ সব ১৯৬৬ সালের লেখা। দশ বছরও কাটবে না, বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবকে ১৯৭৫ সালের অগস্ট মাসের ১৫ তারিখ তাঁর বাড়িতে চড়াও হয়ে নির্মম ভাবে হত্যা করবে তাঁর সেই পরম বিশ্বাসভাজন দেশবাসীরই কেউ কেউ, ‘নিরীহ বাঙালি জাত'-এর একাংশ। তাঁর সঙ্গে, তাঁর সেই অবুঝ শিশুপুত্র রাসেল, যে তখন এগারো বছরের বালক— তাকেও হত্যা করবে বাঙালিরাই। রাসেলের মা রেণুকেও। রাসেলের দুই দাদা, কামাল ও জামালকেও। তাদের স্ত্রীদেরও। প্রত্যেকের ঘরে হানা দিয়ে রক্তলীলা বইয়ে দেওয়া হবে। এই হত্যাকারীদেরই জন্য স্বাধীন বাংলাদেশের স্বপ্নে, আদর্শে, আবেগে ভর করে এতগুলো বছর পাকিস্তানি নির্যাতন সহ্য করেছিলেন শেখ মুজিব?
একটা কথা ঠিক। বন্দিদশায় যতটা সোজা করে ভাবতে ভালবাসতেন, মানুষকে বিশ্বাস করায় বিশ্বাস রাখতেন, দেশ স্বাধীন হওয়ার পর শীর্ষক্ষমতায় বসেই বুঝতে পেরেছিলেন, সে ভাবনায় গলদ আছে। কাছের লোকদের বলেছিলেন, “...বড় কঠিন জায়গা। মনে হয় যেন বাঘের পিঠে চড়ে বসেছি।” তাও হার মানবার, পিছু হটবার মানুষ তো তিনি নন। “বেশি দিন তো সহ্য করা যাবে না। শক্ত একটা কিছু করতে হবে।”
সময় পাননি ‘শক্ত কিছু করার'। তবু, এই যে তাঁর হাজার বিপদের মধ্যেও, বিস্তর সঙ্কটের মধ্যেও এগিয়ে যাওয়ার জেদ, নিজেকে দেশের কাজে লাগাবার সঙ্কল্পের ক্রমাগত উচ্চারণ, এই সব নিয়েই তো শেখ মুজিব। জেলের ডায়েরিতে একটি রবীন্দ্রসঙ্গীত বার বার বিভিন্ন প্রসঙ্গে তাঁকে লিখে রাখতে দেখি আমরা: “বিপদে মোরে রক্ষা করো, এ নহে মোর প্রার্থনা/ বিপদে আমি না যেন করি ভয়।”
হৃদয়ভরা আবেগ, আশা আর আশ্বাস নিয়েও তিনি হয়তো দেখতে পেতেন সামনে সীমাহীন বিপদ-সমুদ্র। সঙ্কল্প করতেন, ভয় না পেয়ে সেই পারাবারে ঝাঁপ দেওয়ার জন্য। তাই রোজনামচা বলছে— সহধর্মিণী সপ্তাহান্তের ‘ভিজিট’-এর পর ফিরে যান যখন, জেলের একাকী ঘরের সামনে দাঁড়িয়ে বন্দি নেতা তাঁকে বিদায় দেন: “ভাবিও না, আরও অনেক কষ্ট আছে। প্রস্তুত হয়ে থাকিয়ো।”
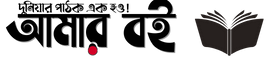

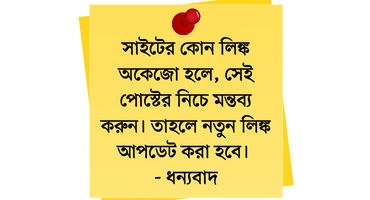







![[ছোট্টগল্প] সেক্সবয় - তসলিমা নাসরিন](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEizCNalHzbcL_TRO47frupqVrYhkJmfl_OaBixQzVrIC9gZtXtGiggWI52u_yo8X-cwdAfVwBlwyTJSaFM9F2lp5Qn4Kq0vWMi5DWKhVvP7UN-MkOFsO-kl7tIV3Xu874EhlsSm4r8fbNgR/w72-h72-p-k-no-nu/sboyt.png)









0 Comments